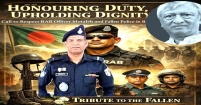প্রকাশ : ০৮ মার্চ ২০২৪, ০০:০০
জাতীয় সংসদে জেন্ডার ভারসাম্য ও জেন্ডার ইস্যু প্রসঙ্গ
সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদ সরকারের হাতিয়ার বৈকি?

“বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।”
জাতীয় কবি যে মহান সৃষ্টির উল্লেখ করেছেন সেই সৃষ্টিতে কোনো ভেদ নেই। কিন্তু মানুষ সেই সৃষ্টিকে নারীত্ব ও পুরুষত্ব নামে যে সামাজিক বৈষম্য করেছে, এই সামাজিক সৃষ্টিই জেন্ডার। জাতীয় ই-তথ্যকোষ জেন্ডারের সংজ্ঞা দিয়েছে, ‘জেন্ডার হলো নারী-পুরুষের ভূমিকার সমতায়ন, সম-অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং কার্যক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক।’ নারীর অধিকারের ব্যাপারে যাঁর প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে তার নাম মেরী ওয়েলস্টোন ক্রাফট। তিনি ‘ভিনডিকেশন অব দি রাইটস অব ওমেন’ (১৭৯২ খ্রিঃ) নামক গ্রন্থে নারী ও পুরুষকে এক মানদণ্ডে বিচারের দাবি জানান। ১৯০৮ সালে ৮ মার্চ নিউইয়র্কের দর্জি শ্রমিকরা নারীর ভোটাধিকার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে এবং ১৯২০ সালে সমগ্র আমেরিকায় স্বীকৃতির পূর্বে ১৯১০ সালে ওয়াশিংটনে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। এর সূত্র ধরে ‘৮ মার্চ সংগ্রামের সূচনা দিবস হওয়ায় ৮ মার্চকেই আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ হিসেবে পালনের জন্যে নির্বাচন করা হয়। এর ৬৫ বছর পর জাতিসংঘ ১৯৭৪ সালের ৮ মার্চ এ দিনটিকে স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘের সহযোগিতায় মেক্সিকো, কোপেনহেগেন, নাইরোবী ও বেইজিং এ চারটি বিশ্ব নারী সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই মাঝে জেন্ডার ইস্যুর সবচেয়ে বড় ঘটনা ১৯৭৯ সালে Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) চুক্তি পাস হয়। এরপর আরও কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাগ্রহণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ-সিডও (ঈঊউঅড)। সিডও সনদের মূল লক্ষ্য হলো, মানুষের মৌলিক অধিকার, মর্যাদা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার নিশ্চয়তা বিধানের আবশ্যকীয়তা এবং নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দান। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর সিডও সনদ অনুমোদন করেছে।
বাংলাদেশে নারীরা সামাজিকভাবে অনগ্রসর ও রাজনীতিতে সবচেয়ে অপ্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠী। নারীরা এ দেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশি (১০৬ : ১০০)। এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর সেবা থেকে সমগ্র বাংলাদেশ বঞ্চিত হলে বিশ্বায়নের এই যুগে বাংলাদেশকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকবে না। সেদিকে লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করা উচিত। এজন্যে নারীদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশ নিয়ে প্রতিটি স্তরে বৈষম্য বিলোপ করতে হবে।
কিন্তু তিন দশকেরও বেশি সময় যাবৎ এ দেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দল তারা নেতৃত্ব দিয়ে আসলেও দেশের জাতীয় সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব মাত্র দু থেকে চার শতাংশ। সংসদে নারী সাংসদ বেশিরভাগ একদিকে যেমন তৃণমূল রাজনীতি থেকে ওঠে আসেননি, তেমনি অপরদিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে চলছে ভয়াবহ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন। চলছে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার এক ভয়াবহ আদর্শহীন প্রতিযোগিতা। এই অশুভ প্রতিযোগিতার সাথে পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় সরলা নারী প্রতিনিধিরা কী করে টিকতে পারেন ?
সংরক্ষিত নারী আসনে যারা মনোনীত হয়ে আসেন তারা অনেকটা চাকুরির ক্ষেত্রে পোষ্য কোটার মতো। মেধা কোটায় যারা চাকুরিতে প্রবেশ করেন তারা পোষ্য কোটার প্রার্থীদের অযোগ্য ও সৌভাগ্যের সন্তান হিসেবে বিবেচনা করেন। ঠিক একই ধরনের মানসিকতা পোষণ করেন মূলধারার প্রতিনিধিরা সংরক্ষিত আসনের প্রতিনিধিদের। ফলস্বরূপ জেন্ডার ইস্যুর জন্ম। অপরদিকে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী নারী প্রতিনিধিদের বেশিরভাগই নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার পরিচয়ে পরিচিত হয়ে সংসদে আসার সুযোগ পান না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক ঐতিহ্য ও পেশাগত দক্ষতার কারণে তারা রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেন। সে কারণে সংসদীয় কর্মকাণ্ডে তারা প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করতে পারেন না, যা পুরুষ সাংসদ সহজেই পারেন। এটি জেন্ডার ইস্যু তৈরির বড় কারণ। বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদেও নারী অধিকারের বিষয় বলা হয়েছে-- ১৯ (৩)-এ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন। ২৮ (২)-এ রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। সেহেতু জাতীয় সংসদে জেন্ডার ভারসাম্য রক্ষা এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, (মূল সংবিধান) ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত আসনে ১৫ জন নারী সাংসদ নির্বাচিত হবেন। সংবিধানের দশম সংশোধনী (১২ জুন ১৯৯২) সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১০ বছরের জন্য ৩০টি এবং পঞ্চদশ সংশোধনী আইন-২০১১ কর্তৃক ৫০টি সংসদীয় আসন সংরক্ষিত করা হয়। যা ৬৫ (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচিত ৩০০ জন সংসদ সদস্য কর্তৃক নারী সাংসদ নির্বাচিত হবেন। এই সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় এবং তারপর ৩৫০ জন সাংসদ নিয়ে ৬৫ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ গঠিত হয়।
বাংলাদেশে নারী সমাজ পশ্চাদপদ, এই যুক্তিতে তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জেন্ডার ভারসাম্য রক্ষার নিমিত্তে সংসদে প্রতিনিধিত্ব রাখা প্রয়োজন। কিন্তু এই যুক্তির বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশ সংবিধানে নারীদের জন্যে সংরক্ষিত আসন রাখা হয়েছে বৈকি? বরং এই ৫০ জন নারী সাংসদ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে শাকসদের বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বললে অত্যুক্তি কিংবা যুক্তির বাইরে হবে না। কারণ সংসদের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ জন সাধারণ সদস্য যখন সংবিধানের ৬৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচিত হন, তখন যদি কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে (যদি ১৫১ টি আসনে জয়ী হয়) তাহলে উক্ত দল তাদের ভোট দিয়ে ৫০টি মহিলা আসনের সব ক’টি জয়ী হতে পারে। সুতরাং দলীয়করণ ব্যতীত কোনো নারীর সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকে না।
আবার, যদি কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাও পায় (৩০০টি আসনের মধ্যে যদি ১৫১টি না পায়) তাহলেও বিভিন্নভাবে ঐ ৫০টি সংরক্ষিত আসনের অধিকাংশ জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথ তৈরি করা হয়। উদাহরণকল্পে প্রমাণিত যে, ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৩০০ জন সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর দেখা যায় যে, কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নাই। বিএনপি ১৪০টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পরবর্তীতে বিএনপি ও জামাতে ইসলামী দলের সমর্থন আদায় করে তারা যৌথভাবে ৩০টি নারী সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী মনোনীত করে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৮টি নারী আসন বিএনপি’র পক্ষে যায় এবং ২টি আসন জামাতে ইসলামী লাভ করে। উল্লেখ্য, অন্য কোনো দল নারী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি এবং এরূপ প্রেক্ষিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং এই নারীদের সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে কোনো দল ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম করতে পারে, ক্ষমতায় টিকে থাকার (যেমন-অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হলে সরকারি দল নারী সাংসদদের ব্যবহার করতে পারে) পথ দৃঢ় করতে পারে এবং বিভিন্ন আইন পাস করিয়ে নিতে পারে অনায়াসে।
এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, উন্নত গণতান্ত্রিক বিশ্বে আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় নারীদের জন্যে আলাদা সংরক্ষিত আসনের ঘটনা সাধারণত নজিরবিহীন। যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক পদ্ধতিতে এ ধরনের কোনো সংরক্ষিত আসন নেই। এমনকি বর্তমান ভারত, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের সংবিধানেও এরূপ কোনো বিধান নেই। [দেখুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান-অনুঃ ১(৩), ভারত সংবিধান- অনুঃ ৮১, সিঙ্গাপুর সংবিধান-অনুঃ ৩৯) তবে কতিপয় দেশের সংবিধানে অনগ্রসর সংখ্যালঘু বা তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্যে আইন পরিষদে সংরক্ষিত আসনের বিধান করা হয়ে থাকে। এরূপ তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্যে সংরক্ষিত আসন রাখার পেছনে যে যুক্তিযুক্ত ও বাস্তব কারণ থাকে তা উল্লেখ করার মতো। এরা শুধু যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তা-ই নয়, উপরন্তু এরা শিক্ষায় অনগ্রসর, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল এবং ইহাদের ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার অন্যান্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, অথবা ইহাদের ভাষা এক হলেও বিশেষ সংস্কৃতি এদেরকে সাধারণ জাতি থেকে পৃথক করেছে এবং সুদীর্ঘকাল ধরে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে অত্যাচারিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে, অথবা এরা এমন পশ্চাদপদ সম্প্রদায় বা উপজাতি যারা বহুদিন থেকে কতিপয় বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছে এবং হঠাৎ এ সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হলে এরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হবে। (যেমন-ভারতের ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়) উল্লেখ্য, ভারতীয় সংবিধানে তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য লোকসভায় সংরক্ষিত আসনের বিধান রাখা হয়েছে। (ভারতীয় সংবিধান-অনুঃ ৩৩০ ও ৩৩২)
সুতরাং যে দেশটির স্বাধীনতা যুদ্ধে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ অংশগ্রহণ করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রটি সৃষ্টি করে; যে দেশটির জন্মের পর থেকে এ পর্যন্ত বেশিরভাগ সময় নারীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে; যে দেশটির সরকার প্রধান, বিরোধী নেতা, সংসদের সভাপতি এরূপ প্রায় সবাই নারী, সেই বাংলাদেশের আইনসভা তথা জাতীয় সংসদে জেন্ডার ভারসাম্য থাকবে না-- তা এই বিশ্বায়নের যুগে বাস্তবতায় বলে না। তাই বলতে হয়, জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের জন্যে এরূপ সংরক্ষিত আসন রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়। নারীরা পুরুষের সাথে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে সংবিধানের ৬৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোনো নির্বাচনী এলাকা থেকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সাংসদ নির্বাচিত হতে পারেন। তবে অনেক সময় অনেকে যুক্তি দেখান যে, নারীরা পুরুষের মত সঠিকভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করতে পারে না এবং সে কারণে তাদের জন্যে সংরক্ষিত আসন রাখা প্রয়োজন। এরূপ যুক্তির বাস্তবতায় নারীদের জন্যে কিছু সাধারণ নির্বাচনী এলাকা সংরক্ষিত রাখার বিধান করা যেতে পারে, যাতে করে নারীরা প্রত্যক্ষভাবে জনগণের ভোটে উক্ত সংরক্ষিত এলাকা থেকে নির্বাচিত হতে পারে। সংবিধানে চলমান সংরক্ষিত আসন সংক্রান্ত বিধান সমর্থনযোগ্য হতে পারে কি? যেহেতু এটা বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক মোঃ হাছান আলী সিকদার, সভাপতি, চাঁদপুর জেলা জাসদ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা; চাঁদপুর জেলা শিক্ষক নেতা; সমাজ ও রাজনীতিবিশ্লেষক।
তথ্য-সহায়ক গ্রন্থ :
১. বাংলাদেশের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, মোঃ রফিকুল ইসলাম (রফি), মোঃ আক্তারুজ্জামান, এন এস পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০১৭
২. সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ-মোঃ আব্দুল হালিম, ঢাকা, ১৯৯৭
৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (সংশোধনীসহ মুদ্রিত)-অক্টোবর, ২০১১
৪. রাজনীতি ও উন্নয়নে নারী-সৈয়দ নুরুল হক, গ্রন্থ কুটির, ঢাকা পুনর্মুদ্রণ-২০১৫
৫. সরকার সংবিধান ও অধিকার-মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সময় প্রকাশন, বইমেলা ’৯৯
৬. বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র, রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স (১৯৯১-২০০৭) : আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ২০০৯