প্রকাশ : ১৮ মার্চ ২০২৪, ০০:০০
অপারেশনকালীন মৃত্যু : রোগী-চিকিৎসক বিপর্যয়
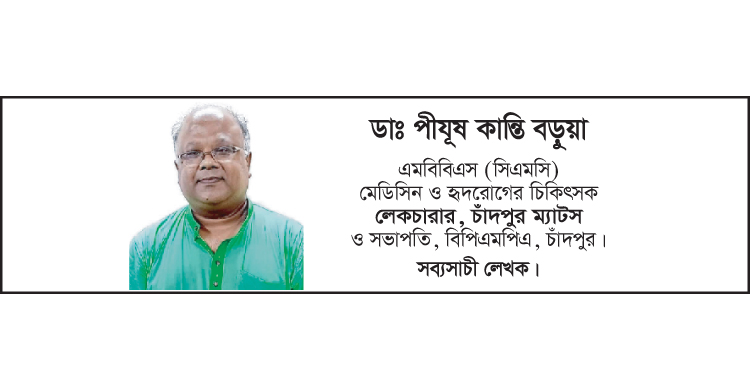
আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা অবিসংবাদিতভাবেই বিজ্ঞানের মহৎ অবদান। আগে রোগ নিরূপণী ব্যবস্থায় দুর্বলতা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার অনুন্নতির কারণে কিছু কিছু রোগ যেমন চিহ্নিত করা যেত না, তেমনি কিছু কিছু চিকিৎসাযোগ্য রোগেরও প্রতিকার সম্ভব হতো না। ফলে মানুষ নিজেদের মনগড়া একটা কারণ ও ব্যাখ্যা তৈরি করে এসব মৃত্যুকে মেনে নিতো বা মেনে নিতে বাধ্য হতো। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার বিকাশ ও বিস্তার লাভের কারণে শৈল্য চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষের রুগ্ন জীবনে যেমন আরাম ও উপশমের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে তেমনি অনির্ণীত রোগে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকেও বর্তমানে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সকল সুখেই দুঃখ ওঁৎ পেতে থাকে কালিমা লেপনের জন্যে। আমরা একারণেই চিকিৎসাকালীন অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর মুখোমুখি হই। মানুষ মরণশীল এবং চিকিৎসকের পক্ষে আয়ুকে জয় করে মুমূর্ষুকে সর্বদা বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। চিকিৎসক রোগীকে দ্রুত আরোগ্য লাভ করাতে পারেন মাত্র। চিকিৎসক যেমন কারও জীবন দিতেও পারেন না তেমনি কারও জীবন নিতেও পারেন না। প্রশ্ন হলো, চিকিৎসা দিতে গিয়ে চিকিৎসকের কোনো অবহেলা ছিলো কি না এবং কোনো প্রকার দক্ষতার ঘাটতি ছিলো কি না। অতি সাম্প্রতিককালে দুজন ছোট শিশুর সুন্নতে খতনা করতে গিয়ে নির্মম ও অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে চিকিৎসক সমাজ আজ অপরাধীর কাঠগড়ায়। তারা যেমন জনতার কাঠগড়ায় তেমনি আইনেরও কাঠগড়ায়। মানুষের আজ তাই অস্ত্রোপচার বা শৈল্য চিকিৎসার বিষয়ে ভীতি ও শঙ্কা তৈরি হয়েছে।
কোনো চিকিৎসকই তার হাতে চিকিৎসাপ্রার্থী কোনো রোগীর মৃত্যু কামনা করে না। কারণ চিকিৎসা দেওয়া তার কেবল পেশাই নয়, ব্রতও বটে। প্রতিজন রোগী চিকিৎসা শাস্ত্রে এক একটা বই যা পাঠে চিকিৎসক তার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে নিতে পারেন এবং জ্ঞানকে শাণিয়ে নিতে পারেন। একজন চিকিৎসকের জন্যে প্রতিটা রোগী এক একজন বিজ্ঞাপনী দূত। রোগী নিজেই তার চিকিৎসকের হাতযশের প্রচার ও বিস্তার ঘটান। কাজেই মানবতার স্বার্থে, মানুষের জীবনের বহমানতার প্রয়োজনে চিকিৎসক-রোগী সম্পর্কটি আন্তরিক ও সহজ হওয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কটি আস্থা-নির্ভর না হলে কেউই সেবা দিয়ে এবং সেবা নিয়ে স্বস্তি পাবেন না।
কোনো রোগীকে অপারেশনের টেবিলে শোয়ানোর আগে তাকে অবেদনযোগ্য করতে তুলতে শারিরীক উপযুক্ততা যাচাই করতে হয়। অর্থাৎ কিছু শারিরীক পরীক্ষা করে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে তাকে পরীক্ষাকারী প্রাথমিক চিকিৎসকের কাজটা গুরুত্বপূর্ণ। তার রোগের ইতিহাস আদ্যোপান্ত জানা দরকার হয়। তার হার্টের অবস্থা, তার শ্বাসতন্ত্রের অবস্থা জানা জরুরি। তার হাঁপানি বা অ্যাজমা থাকলে সেক্ষত্রে অতিরিক্ত সচেতনতা দরকার হয়। রোগীর ওজন একটা বড় নিয়ামক। রোগীর অতি স্থূলতা অবেদনবিদের জন্যে ঝুঁকির কারণ হতে পারে। রোগীর কিডনির কার্যকারিতা, লিভারের সুস্থতা সম্পর্কে জেনে নিতে হয়। রোগীর রক্তের গ্রুপ নিরূপণ এবং হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ জেনে নিতে হয়। পাশাপাশি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করতে হয় অত্যাবশ্যকীয়ভাবে। এসবকিছু করতে হলে একজন জেনারেল ফিজিশিয়ানের উপস্থিতি প্রয়োজন। তিনি দরকার মনে করলে সকল আবশ্যকীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট অবেদনবিদের কাছে পাঠাতে পারেন। অপারেশনের আগে অবেদনবিদ রোগীকে নিজে দেখে যাচাই করে নিবেন, তার রোগী অপারেশন টেবিলে ওঠানো যাবে কি না। সার্জন বা শৈল্যবিদ অবেদনবিদের অনাপত্তি পেলে তবে রোগীকে অপারেশন টেবিলে ওঠাতে বলবেন। রোগীকে অপারেশন টেবিলে ওঠানোর আগে সার্জন বা অবেদনবিদ বা জেনারেল ফিজিশিয়ানের যে কোন একজন অপারেশন পদ্ধতি ও পরিণাম সম্পর্কে রোগী ও রোগীর অভিভাবককে ব্যাখ্যা করবেন এবং এরপরে হাসপাতাল বা ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ একটি সম্মতিপত্রে তাদের স্বাক্ষর নিবেন। এরপর রোগীকে অপারেশন টেবিলে ওঠাতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে যে বাস্তবতা, তাতে আমরা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে অভ্যস্ত। আমরা সরাসরি সার্জনের সাথে যোগাযোগ করি। নিজেরাই নির্ধারণ করি, কোন বিশেষজ্ঞ দেখাবো। যাদের ন্যূনতম ধারণা নেই চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে, তারাই নির্ধারণ করি এবং নির্বাচন করি সরাসরি কোন্ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া যায়। অথচ এটা নির্ধারণ করার কথা হলো একজন প্রাইমারি ফিজিশিয়ানের। তিনিই রোগী দেখে, প্রাথমিক পরীক্ষাদি করে নিরূপণ করবেন, আদৌ রোগীটা কি সার্জনের না মেডিসিনের। ফলে কী হয়? তথ্য ঘাটতি তৈরি হয়। এতে চিকিৎসক ও চিকিৎসার সমন্বয় ভেঙে পড়ে।
অপারেশনের ক্ষেত্রে বড় একটা বিষয় হলো, অপারেশন টেবিলে নেওয়ার আগে অন্ততপক্ষে ছয় ঘণ্টা না খাইয়ে রাখা। কেননা, অবেদন করার ঔষধ প্রয়োগ করলে বমির প্রবণতা তৈরি হয়। এতে অচেতন অবস্থায় রোগীর শ্বাসতন্ত্রে পাকস্থলীর পাচ্য-অপাচ্য-অর্ধ পাচিত আহার অনুপ্রবিষ্ট হয় ও রোগী অপারেশন টেবিলে মারা যায়। আমাদের দেশে একটা রেওয়াজ প্রচলিত আছে, হাসপাতালে আসার আগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপারেশনের রোগীকে পেটভরে খাইয়ে দেওয়া হয়। এই কথাটি আবার গোপন করা হয় হাসপাতালে এসে চিকিৎসকের কাছে। ফলে অপারেশন টেবিলে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে যে শিশু দুটির ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে একজনের চাচা এসে কোলে করে বাইরে নিয়ে অপারেশনের দু'ঘন্টা আগে নাশতা খাইয়ে এনেছে। এই কথাটি গোপন থাকায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেছে বলে শোনা গেছে। এজন্যে অবেদনযোগ্য যে কোন অপারেশনের রোগীকে অন্তত আগের রাতে বা আট-ঘণ্টা আগে হাসপাতালে ভর্তি করা জরুরি। এতে অপারেশনের উপযুক্ত প্রক্রিয়া মেনে চলা যায়। আবার অবেদনবিদ যে ঔষধ প্রয়োগে রোগীকে আবেদনযোগ্য করে তোলেন, সেই ঔষধের গুণগত মান নিয়েও অনেক সন্দেহ থেকে যায়। সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে এটা বুঝা গেছে, যে হ্যালোথেইন অবেদনবিদ ব্যবহার করেন তা বাজারে হ্যালোসিন নামে অপেক্ষাকৃত কম দামে পাওয়া যেতো। কিন্তু এর উৎপাদক এসিআই কোম্পানি গত দুহাজার তেইশ সালের ডিসেম্বরে ঔষধটির সকল ধরনের উৎপাদন ও বিপণন বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হলো, ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় অবেদনের জন্যে যে হ্যালোসিন ব্যবহৃত হলো তা এলো কোথা থেকে? নকল নয়তো? এই প্রশ্ন এখন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, কয়েকজন শিশুর অপারেশন টেবিলে বা অপারেশনজনিত মৃত্যু যাদের হয়েছিলো, তাদের অবেদনের জন্যে এই হ্যালেসিন ব্যবহৃত হয়েছিলো যার উৎপাদন ও বিপণন দুহাজার তেইশের ডিসেম্বর হতে বন্ধ। অবেদন বা অচেতন প্রক্রিয়াজনিত মৃত্যুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, অবেদনের ঔষধ রোগীর শরীরে প্রয়োগ করার পর হতে পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু হলে তাকে অবেদনজনিত মৃত্যু বলা হয়। অবেদনবিদ ও সার্জনের জন্যে অতিরিক্ত বয়োবৃদ্ধ ও অতি ছোটো শিশু খুবই অনিরাপদ। এদের অজ্ঞান করে পুনঃচেতনা ফিরিয়ে আনা কঠিন। যারা অতিবৃদ্ধ রোগী তাদের মৃত্যুহার বিভিন্ন রোগজনিত জটিলতায় অধিক। এদের উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাজমা, হৃদরোগ, কিডনি ফেইলিওর প্রভৃতি রোগ থাকে। ফলে এদের অপারেশনের জন্যে উপযুক্ত করে নিতে অনেক বেগ পেতে হয়। পাশাপাশি সদ্যোজাত বা মাসখানেকের বাচ্চারা অতিবৃদ্ধদের চেয়ে আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। মার্কিন অবেদনবিদ সোসাইটির অবেদনবিদেরা বয়স ও অন্যান্য রোগজনিত নিয়ামক বিবেচনায় অবেদনযোগ্যতার গ্রেডিং করেন। তাদের গ্রেড অনুযায়ী গ্রেড তিনের রোগীদের মৃত্যুহার ১.৮% এবং গ্রেড পাঁচের রোগীদের মৃত্যুহার ৯.৪%।
আবার সার্জনের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে অংশে অস্ত্রোপচার হবে সে অংশের অবস্থান ও গুরুত্বভেদেও অস্ত্রোপচার ঝুঁকিপূর্ণ হয়। যদি অপারেশনটা কোনো মহাধমনী, বক্ষপিঞ্জর বা পেটের ঊর্ধ্বাংশে হয় তবে তা অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ থাকে। এমনকি রোগীর অন্য কোন রোগ না থাকলেও। একইভাবে ইমার্জেন্সি অপারেশন, কার্ডিওলজিক্যাল অপারেশন কিংবা নিউরোসার্জারি বিষয়ও এই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনের আওতায় পড়ে।
অবেদনবিদের ত্রুটির জন্যেও অপারেশন টেবিলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। দেশে অবেদনবিদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে এবং সেই তুলনায় অনেক বেশি অপারেশন হওয়ায় অবেদনবিদেরা সব সময় একটা চাপের মধ্যে থাকেন। তারা উপযুক্ত মানসিক ও পেশাগত প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পান না অনেক ক্ষেত্রেই। এছাড়াও ঔষধের মাত্রা নির্ধারণকৃত পরিমাণের চেয়ে অধিক হওয়া, ঔষধের বোতলের গায়ে এক ঔষধের স্থলে ভুল ঔষধের লেবেল লাগানো থাকা, অভিজ্ঞতার ঘাটতি এবং মুখে টিউব ঢোকানোর সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া প্রভৃতিও মানবসুলভ ভুলের আওতায় পড়ে। রোগীর অবেদনক্রিয়া সূচনাকারী ঔষধ এবং প্রশ্বাসে গ্রহণকৃত ঔষধ-বাষ্পের প্রতি রোগীর অতি সংবেদনশীলতাও রোগীর অপারেশন টেবিলে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। পাশাপাশি পেশি শিথিলতার ঔষধও এসময় কার্ডিয়াক এরেস্ট ঘটায় এবং হৃদযন্ত্রের তাল বেতাল হয়ে যায়। এছাড়াও রোগীর মুখে শ্বাসনালীর টিউব ঢুকাতে গিয়ে দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্বরনালী ও শ্বাসনালীর সংকোচন ঘটে। কখনো কখনো অবেদনবিদের কাজ করার জন্যে অপারেশন থিয়েটারে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সেট আপ থাকে না। ফলে অবেদনবিদের পক্ষে দুর্ঘটনা দেখা দিলে তা মোকাবেলার উপায় থাকে না।
সার্জারিজনিত কারণ
অপারেশনের টেবিলে মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে বলতে হয়, যতো অপারেশন করা হয় ততো অপারেশন সফল হয় না। শতভাগ সাফল্য কোন সার্জনের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ কিছু কিছু সার্জারিতে উচ্চ মাত্রার ঝুঁকি থাকে। অতিমাত্রায় হঠাৎ করে রক্তক্ষরণ, দুর্ঘটনার কারণে অন্ত্র ফুটো হয়ে যাওয়া, প্রধান রক্তনালীর ইনজুরি হওয়া, কোন কিছু বিদ্ধ হওয়াজনিত রক্তক্ষরণের অপারেশনগুলো সব সময় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে।
অভিজ্ঞ ও দক্ষ অবেদনবিদ হলে অপারেশন থিয়েটারে শতকরা নব্বইভাগ কার্ডিয়াক এরেস্টের রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। সময় এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। কার্ডিয়াক এরেস্ট অনুমিত হওয়ার সাথে সাথেই রোগীকে ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম শুরু করে দিতে হবে। অপারেশন থিয়েটারে কী কী পর্যায় অনুসৃত হলো তা সব বিধিসংগতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।
ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড ধারা ঊনচল্লিশ মোতাবেক অপারেশন ও অবেদনকালীন মৃত্যুগুলো অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে পুলিশকে অবহিত করতে হবে।
পক্ষান্তরে, অবেদনকালীন মৃত্যুতে অবেদনবিদের কিছু দায় থেকে যায়। যেমন :
১. রোগী অবেদনের জন্যে উপযুক্ত ছিলো কি না
২. রোগীকে অবেদন প্রক্রিয়ার আগে যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিলো কি না
৩. রোগীকে কোন ধরনের উপায়ে অবেদন করা হবে তা ব্যাখ্যা করে সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছিলো কি না
৪. যথা দক্ষতা ও যত্নে অপারেশন ও অবেদন সম্পন্ন হয়েছিলো কি না
৫. আকস্মিক কোনো অঘটন ঘটলে তা মোকাবেলা করার মতো প্রস্তুতি ছিলো কি না
৬. উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে রোগীকে ফিরিয়ে আনতে প্রযোজ্য পর্যায়গুলো অনুসৃত হয়েছিলো কি না।
৭. আদৌ কোন অবেদন মেশিন ভুলভাবে সেট করা ছিলো কি না
৮. অবেদন করার মেশিনে কোন ত্রুটি ছিলো কি না
৯. অবেদন করার ঔষধগুলো মেয়াদোত্তীর্ণ ছিলো কি না বা যথাযথ উৎপাদনকারী হতে ক্রীত কি না।
চিকিৎসক ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি রোগীকে চিকিৎসা দিয়ে শতভাগ আরোগ্য করতে না পারলেও শতভাগ আস্থা অর্জন করতে পারা উচিত। আস্থার সংকট হলে রোগী বাঁচিয়ে দিয়েও কোনো সুনাম অর্জিত হয় না। আজকাল বাংলাদেশে চিকিৎসক ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোর জন্যে এক ক্রান্তিকাল যাচ্ছে। এই ক্রান্তিকাল কাটিয়ে উঠতে চিকিৎসকদের আরও অধিক যত্নবান ও সাবধানী হওয়া উচিত। রোগী হাসপাতালে কিংবা ডাক্তারের হাতেই মারা যাবেন। এটাই এ পেশার সত্যি এবং নিয়তি। কিন্তু তাই বলে চিকিৎসকের অবহেলায় কিংবা অদক্ষতায় যাতে কোনো রোগীর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু না ঘটে। কারণ যতই হোক রুগ্ন হলে রোগী চিকিৎসকেরই শরণাপন্ন হন।








