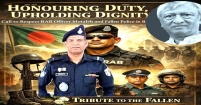প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ০০:০০
মানুষের ভাষা ভাষার মানুষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
ভাষা সম্পর্কে আকরগ্রন্থ ‘ইথনোলগ'র দুহাজার বাইশ সালের পরিসংখ্যান মোতাবেক পৃথিবীতে বর্তমানে জীবিত ভাষার সংখ্যা সাতহাজার নিরানব্বইটি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাষা চালু আছে পাপুয়া নিউগিনিতে, যার সংখ্যা আটশো পঞ্চাশটিরও অধিক। এর পরেই আছে ইন্দোনেশিয়া, যেখানে প্রায় ছয়শ সত্তরটি ভাষা মানুষের মুখে মুখে বেঁচে আছে আজও। যদিও ভাষা সংক্রান্ত সমীক্ষায় বলছে প্রতি পনের দিনের ব্যবধানে একটি করে ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে। যদিও কয়েকটি ভাষা আবারও সরকারি তৎপরতায় ফিরেও এসেছে। যেমন : ওয়েলস, মাওরির ইত্যাদি ভাষাগুলো। লেখার সাংকেতিক চিহ্ন ছাড়া কেবল মুখের চর্চায় ভাষা বেঁচে থাকতে পারে না। যাদের নিজেদের বর্ণমালা আছে, সেই ভাষাগুলোই টিকে আছে দীর্ঘ সময় ধরে এবং ভবিষ্যতেও তা টিকে থাকবে। ভাষা লেখার সংকেতগুলোই হলো বর্ণ। পৃথিবীতে বর্ণের সংখ্যায় সবচেয়ে ছোট বর্ণমালা হলো ‘রোটোকাস’। এই ভাষাটি পাপুয়া নিউগিনিতে চালু আছে, যার বর্ণমালায় বর্ণের সংখ্যা মাত্র এগারটি। সবচেয়ে দীর্ঘ বর্ণমালা হলো কম্বোডিয়ানদের। এতে চুয়াত্তরটি বর্ণ আছে। মহাশূন্যে প্রথম যে ভাষাভাষী মানুষকে পাঠানো হলো তিনি ছিলেন রুশভাষী নারী নভোচারী ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা। তার ভাষার কারণেই বলা যায়, মহাশূন্যে সর্বপ্রথম রুশভাষা উচ্চারিত হয়। যে ভাষায় প্রথম বই ছাপা হয়েছিলো, তা হলো জার্মান।
কিছু কিছু ভাষা বর্তমানে অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে আছে। যেমন : ‘বাদেশি’ নামে একটি ভাষা আছে যার ভাষাভাষীর সংখ্যা মাত্র তিনজন। এদের একজন হলেন সাইদ গুল। এটি উত্তর পাকিস্তানের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের একটি ভাষা ছিলো। শুরুর দিকে এ ভাষায় দশটি পরিবার কথা বলতো। আফ্রিকার আরেকটি ভাষার নাম ‘এনজেরেপ’, যে ভাষায় কথা বলেন বর্তমানে মাত্র চারজন। সবচেয়ে কনিষ্ঠ জনের বয়স হলো ষাট, যিনি নাইজেরিয়ার নাগরিক। ইন্দোনেশিয়ার পাপুয়া অঞ্চলের একটি বিপন্ন ভাষা ‘লিকি’, যার ভাষাভাষীর সংখ্যা বর্তমানে দশজন। এটা ছিলো এককালে গির্জার পাদ্রীদের ভাষা। বাইশজন কথা বলে এরকম একটি বিপন্ন ভাষা হলো ‘পাকান্তি'। এটি অস্ট্রেলিয়ার মারে ডার্লিং নদীর তীরবর্তী একটি ভাষা, যা আদিবাসীরা চর্চা করে থাকে। সরকারি চেষ্টায় কিছু কিছু মানুষকে এ ভাষায় কথা বলতে শেখানো হচ্ছে বর্তমানে। ‘রেংমিটচ্য’ ভাষায় কথা বলে মাত্র ছয়জন, যারা আমাদের বান্দরবানের মানুষ। একজন নারী এবং পাঁচজন পুরুষ এ ভাষায় কথা বলে। এদের চারজনের বয়সই ষাটের ওপরে। এরা হলেন কুনরাও (৬৯ বছর), মাংপুন (৭৫ বছর), সিংরা (৪৫ বছর), থোয়াইংলক (৫৮ বছর), রেংপুন (৭২ বছর) এবং মাংওয়াই (৬০ বছর)। এরা সবাই ম্রো সম্প্রদায়ের লোক। দুর্গম পার্বত্য এলাকায় আলাদা আলাদা থাকার কারণে এ ভাষার চর্চাও তারা করতে পারেন না।
মাতৃভাষার অধিকার নিয়ে বাঙালিই লড়াই করেছে প্রথম। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ভাষা বা লিংগুয়া ফ্রাংকা কী হবে তা নিয়ে তৈরি হয় অস্বচ্ছতা। ছাপান্ন শতাংশ বাংলা ভাষাভাষীর দেশে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পাঁয়তারা চলে। এটা আঁচ করতে পেরে ঊনিশশো আটচল্লিশ সালের পঁচিশে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে বাঙালি জনপ্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন। ঊনিশশো আটচল্লিশ সালের একুশে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের নাগরিক সংবর্ধনা সভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। আবার চব্বিশে মার্চ কার্জন হলে বিশেষ সমাবর্তনের ছাত্রসভায়ও তিনি বেশ জোরালো ভাষায় বলেন, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। যারা এর বিরোধিতা করে, তারা পাকিস্তানের দুশমন। তাদের কঠোর হাতে দমন করা হবে। এরই বিরোধিতায় উপস্থিত ছাত্ররা ‘নো নো’ বলে চিৎকার করে উঠে। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ঊনিশশো বায়ান্ন সালের একুশ ফেব্রুয়ারি তারিখে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার একশ’ চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র-জনতা মিছিল নিয়ে যায় বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে। পুলিশের গুলিতে সেদিন শহিদ হয় বাঙালি ছাত্র-জনতার কয়েকজন। ঠিক কতজন ভাষা আন্দোলনে শহিদ হয় তা নিয়ে বেশ মতানৈক্য রয়েছে। যদিও একুশের প্রথম কবিতা ‘কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’ কবিতায় কবি মাহবুব আলম চৌধুরী চল্লিশ জনের শহিদ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তবে আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং ভাষা আন্দোলনকালীন গুরুত্বপূর্ণ নেতা তাজউদ্দীন আহমদের লেখা ডায়েরি হতে জানতে পারি, সেদিন বেসরকারি তথ্যমতে মৃতের সংখ্যা ছিলো বারো জন এবং আহতের সংখ্যা বহু। এই বার জনের সবার নাম জানা না গেলেও কয়েকজনের নাম জানা গেছে। তারা হলেন : ২১ শে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদ আব্দুল জব্বার, রফিক উদ্দিন আহমদ, আবুল বরকত ও আব্দুস সালাম। ২২ শে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদ শফিউর রহমান, আব্দুল আউয়াল, মোঃ অহিউল্লাহ এবং এক অজ্ঞাত বালক। এছাড়াও সালাউদ্দিন নামে একজনকেও শহিদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে কারো কারো লেখায়।
ভাষা আন্দোলনের শহিদদের সম্মান জানিয়ে ঊনিশশো ছিয়াত্তর সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘একুশে পদক’ চালু করা হয়। এটি প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির কুড়ি তারিখ ঘোষণা করা হয়। প্রথমে তিনটি বিষয়ে একুশে পদক চালু করা হলেও পরে আরও ছয়টি বিষয় যোগ করা হয়। যারা বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তাদেরকে ভাষাবীর বা ভাষা সংগ্রামী নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে যদিও এটা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নয়। রাষ্ট্র এই ভাষা শহিদদের দুহাজার সালে একুশে পদকে ভূষিত করেছে। পাশাপাশি জীবিত ভাষা সংগ্রামীদের অনেকেই ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখায় একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন। দুহাজার সালে ভাষা শহিদ বরকত, জব্বার, সালাম, রফিক, শফিউর এবং জীবিত ভাষা সৈনিক গাজীউল হককে ‘ভাষা আন্দোলনে একুশে পদক’ প্রদান করা হয়। ‘মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড’ নামে একটি সংগঠন কানাডার ভ্যাঙ্কুবার থেকে জাতিসংঘের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনানকে চিঠি দেয় একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার। কানাডা নিবাসী বাঙালি রফিক, সালাম; ইউনেস্কো, জাতিসংঘ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অবশেষে দুহাজার দশ সালের সতেরো নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়, যা প্রথমবারের মতো দুহাজার দশ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। বিশ্বব্যাপী বিকাশমান ভাষা ও বিপন্ন ভাষাকে রক্ষার জন্যে দুহাজার এক সালের পনের মার্চে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই ইন্সটিটিউট দুহাজার দশ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে শুভযাত্রা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সরাসরি ভাষা আন্দোলনে যেমন অংশ নিয়েছিলেন তেমনি ঊনিশশো বায়ান্ন সালে সেপ্টেম্বরের শেষে তিনি নয়া চীনে গিয়ে অক্টোবরের শান্তি সম্মেলনে পরিকল্পিতভাবে বাংলায় ভাষণ দেন। ঊনিশশো বাহাত্তরে সংবিধান প্রণয়নকালে তিনি বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেন। ঊনিশশো চুয়াত্তরের পঁচিশে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তিনি বাংলায় ভাষণ দিয়ে বিশ্বকে জানান দেন বাংলার গুরুত্ব সম্পর্কে।
বাংলা ভাষার প্রতি ঊনিশশো আটচল্লিশের এই নির্যাতন আসলে শুরু হয়েছিলো সেই মধ্যযুগ থেকে। তখন বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানী ভাষা আখ্যা দিয়ে অবজ্ঞা করার চেষ্টা করা হলে মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিম, কবি আব্দুল মুত্তালিবসহ আরো অনেক মুসলিম কবি কবিতার মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ জানান। কবি আব্দুল হাকিম বলে ওঠেন, ‘যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী /সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।’ তার পাশাপাশি কবি আব্দুল মুত্তালিব লেখেন,
‘আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ।
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ ॥
মুসলমানি শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলুঁ।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ ॥ ’
মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি ভাষায় কাব্য চর্চায় সুখ্যাতি অর্জনে ব্যর্থ হয়ে বাংলা ভাষায় ফিরে আসেন এবং ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় নিজেই বলেন,
‘পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি পূর্ণ মায়াজালে।’
কবি রামনিধি গুপ্তের কবিতায় আমরা পাই,
‘নানান দেশের নানা ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা
মেটে কি আশা, পুরে কি তৃষা?’
ভাষার ব্যাপারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, পরে চাই ইংরেজি শেখার পত্তন।’ এ কথাকেই যেন সমর্থন দিয়েছেন অকুণ্ঠভাবে পঞ্চকবির অন্যতম অতুল প্রসাদ সেন। তাঁর হাতে আমরা পাই অমোঘ বাণী, ‘মোদের গরব মোদের আশা /আ-মরি বাংলা ভাষা।’
মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় আইনস্টাইনের সমীহ ও সঙ্গ লাভকারী পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন সেন গুরুত্ব আরোপ করে গিয়েছেন। সেই আন্দোলনকে সামনে টেনে নিয়ে গেছেন বিজ্ঞানী কুদরত-ই খুদা এবং পরবর্তীকালে ড. আব্দুল্লাহ্ আল-মুতী শরফুদ্দিন ও ড. আলী আসগর প্রমুখ বিজ্ঞানীরা।
বাঙালির পাশাপাশি অসমীয়ারাও মায়ের ভাষা তথা বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে আন্দোলন করে। এর ফলস্বরূপ ঊনিশশো একষট্টি সালের ঊনিশে মে তারিখে আসামের শিলচরে পুলিশের গুলিতে এগারজন শহিদ হন। এদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের প্রথম নারী শহিদ ষোল বছর বয়সী কমলা ভট্টাচার্যও ছিলেন। অন্য দশজন যথাক্রমে শচীন্দ্র পাল, কানাই নিয়োগী, সুনীল সরকার, সুকোমল পুরকায়স্থ, কুমুদ দাস, চন্ডীচরণ সূত্রধর, তরণী দেবনাথ, হীতেশ বিশ্বাস, বীরেন্দ্র সূত্রধর ও সত্যেন্দ্র দেব।
নিহত সবারই বয়স ছিলো পঁচিশ বছরের নিচে। এই ভাষা শহিদদের স্মরণে দুহাজার পাঁচসালে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনটিকে নামকরণ করা হয় ‘ভাষা শহিদ স্টেশন’ রূপে। বাঙালিদের পাশাপাশি মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদায়ও তাদের মাতৃভাষার সম্মান রক্ষায় লড়াই করে। বরাক উপত্যকাতেই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার স্বীকৃতির আন্দোলনে ঊনিশশো ছিয়ানব্বই সালের ষোলো মার্চ শহিদ হন বিশ্বের দ্বিতীয় নারী ভাষা-শহিদ সুদেষ্ণা সিংহ। ঐদিন পুলিশের গুলিতে আহত হন আরো সহস্রাধিক বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাযোদ্ধা। শহিদ সুদেষ্ণার স্মরণে ভারত ও বাংলাদেশের মণিপুরীরা ষোলো মার্চ ভাষাদিবস পালন করে থাকে।
‘আমার পরিচয়’-এর কবি সৈয়দ শামসুল হক ভাষাবীর শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনাকে ‘ভাষাকন্যা’ উপাধি দিয়েছেন। কারণ ‘মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড’-এর আবেদনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেতে তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কোকে পত্র প্রেরণসহ সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অত্যন্ত দ্রুততায় সম্পন্ন করেন। কবি সৈয়দ হক কানাডায় ভ্রমণকালে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে বাংলা কী প্যাড ও ভাষা অন্তর্ভুক্তির জন্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোকে আবেদন জানান। আজকের স্মার্ট ফোনে বাংলা কী বোর্ড ও ভাষা সেট আপ করার পেছনে তাঁর এই আবেদনের অবদান কিছুটা হলেও থেকে থাকতে পারে।
ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার উত্তর প্রজন্ম ইন্দো-আর্য ভাষা হতে উদ্ভূত বাংলা ভাষার আদি রূপ পাওয়া যায় হাজার বছর আগে ‘চর্যাপদ’ নামক সহজিয়া বৌদ্ধ গুরুদের রচিত গ্রন্থে। চর্যাপদের ভাষাকে হেঁয়ালির কারণে হোক কিংবা বোধগম্যতার কাঠিন্যে হোক সন্ধ্যা ভাষা নাম দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা যেমন একদিকে রহস্য তৈরি করে আর অন্যদিকে দিন ও রাতের সংযোগ আনে, তেমনি চর্যাপদের ভাষার ভূমিকাও অনেকটা তাই। চর্যাপদের পদকর্তা লুই পা’-এর লেখা থেকে একটা উদাহরণ দিলেই চর্যাপদের ভাষার হেঁয়ালি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। লুই পা’ লিখেছেন, ‘কাআ তরুবর পঞ্চ বী ডাল / চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।’ অর্থাৎ মানবদেহ হলো পাঁচ শাখার তরুর মতো। চিত্ত চঞ্চল হলেই তাতে প্রমাদ কালরূপে অনুপ্রবেশ করে। এই পাঁচ শাখা বলতে রাগ, দ্বেষ, মোহ, কাম ও মাৎসর্যকে বুঝানো হয়েছে। চর্যাপদের ভাষা থেকে বাংলা ভাষা উত্তরণ ঘটিয়ে উত্তরাধুনিক পর্যায়ে পৌঁছেছে বেশ আগেই। কিন্তু’ রেডিও ডিজে, আর জে, টুইটার-ফেসবুকের কারণে আজ যে পর্যায়ে এসেছে তাতে এই অতি প্রাযুক্তিক যুগে আমরা শংকিত। কারণ আজকের ভাষা ক্ষেত্রবিশেষে খিচুড়ি ভাষা হয়ে যাচ্ছে আবার ক্ষেত্রবিশেষে হয়ে যাচ্ছে টেলিগ্রাফিক সংকেতের মতো। রোমান হরফে কেউ কেউ বাংলা লিখে রীতিমতো অসুস্থ’ করে তুলছে সাধারণ মানুষকে। কখনো কখনো পুরো বাক্যে ক্রিয়াপদ ও বিভক্তির ভালো ব্যবহার না থাকায় তা হয়ে যাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভাষার মতো। গুগল ট্রান্সলেটর থেকে পাওয়া অনুবাদ নিয়ে ভাষার দফারফা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নব্বইয়ের দশকে স্বৈরাচারের দিনগুলোতে আমরা একটা জাতীয় দৈনিকের ক্রীড়া পাতার শিরোনামের কথা উল্লেখ করতে পারি। অন্তর্জালে পাওয়া মূল শিরোনাম ছিলো ‘সেরেনা উইলিয়ামস্ উইল প্লে ইন দ্য গেম অব সেক্সেস।’ এটাকে বাংলা করে শিরোনাম করা হয়েছিলো ‘সেরেনা উইলিয়ামস্ যৌনতার খেলা খেলবেন।’ কিন্তু এটা যে নারী বনাম পুরুষের টেনিস খেলা ছিলো তা ঐ প্রতিবেদক বুঝে উঠতে পারেননি। খুদে বার্তার মতোই হয়ে গেছে মানুষের আন্তঃযোগাযোগের ভাষা। সামনাসামনি কথা বলার চেয়ে মানুষ আজকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা ফেসবুকে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বেশি। ফলে ভাষা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ সাংকেতিক ও সংক্ষিপ্ত। তবে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগেও রোগীরা চিকিৎসকের কাছে তাদের রোগ সম্পর্কে অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে উপমা কিংবা উদাহরণ প্রয়োগের দ্বারস্থ হচ্ছে। এতে ভাষা কিছুটা প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। কোনো কোনো রোগীকে এসে বলতে শোনা যায়, স্যার আমার পিঠে কেউ মনে হয় এসি ফিট করে দিয়েছে। অর্থাৎ পিঠের কোনো একটা স্থানে অতি শীতলতা বুঝাতে রোগী এসির ঠান্ডার সাথে তাকে তুলনা করেছেন। আবার এক নারী রোগী এসে রোগের বিরুদ্ধে শুনানি করে গেলো, ডাক্তার সা’ব, আমার পেটে দুপুরে গাঙ ডাকে। এ কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাই। কী সুন্দর উপমা। অর্থাৎ তার পেটে কল কল করে। একজন মধ্য বয়স্ক রোগী সেদিন বললেন, স্যার, আমার মাথার মজলিশ নষ্ট হয়ে গেছে। চিকিৎসক হিসেবে আমাকে আর বুঝে নিতে কষ্ট হলো না, আক্রান্ত ব্যক্তির মাথায় কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে। রোগীদের এই কথোপকথন আমাকে আশাবাদী করে তুলেছে, আসলে ভাষাশৈলীর নান্দনিকতা এখনও সাধারণ মানুষের মনে সৌন্দর্যবোধকে জাগিয়ে রেখেছে।
মানবজাতির ইতিহাসে ভাষার আবিষ্কার হলো সর্বসেরা আবিষ্কার। ভাষা যদি আবিষ্কৃত না হতো তবে মানুষ এতো সহজে পৃথিবী জয় করতে পারতো না। এমনিতেই পরিবেশ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মানুষই এই গ্রহে এলিয়েন। যে কারণে পৃথিবীর পরিবেশের সাথে মানুষ খাপ খাওয়াতে পারেনি বলেই শীতে কম্বল লাগে আর গরমে লাগে পাখা। অথচ অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে এগুলোর কিছুই লাগে না। তারা প্রাকৃতিকভাবেই সবকিছুর সাথে অভিযোজিত হয়ে যেতে পারে। অন্যান্য প্রাণী খাবারকে প্রক্রিয়াজাত করতে হয় না। তারা পরিবেশ থেকে তৈরি খাবার গ্রহণ করে। শুধু মানুষই ভিন্ন, যাকে প্রকৃতি হতে খাবার সংগ্রহ করে তাকে তৈরি করতে হয়। এ গ্রহে মানুষই একমাত্র প্রাণী যাদের নিজস্ব ভাষা আছে। এই ভাষাই আসলে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের পূর্ব পুরুষদের তৈরি করা ধ্বনি বা কথাবার্তা সবই ইথারে ভাসমান। যদি ভবিষ্যতে কোনো প্রযুক্তি সেইসব ধ্বনিমালাকে ধরতে পারে তবে মানব সভ্যতার সূচনার ইতিহাস নিয়ে অনেক ধোঁয়াশা কেটে যাবে। তাই বলতে হয়, পৃথিবীর কোনো ভাষা যাতে মরে না যায়। সকল ভাষাকে রক্ষার উদ্যোগ এখনই নিতে হবে। কেননা ভাষাই আমাদের সভ্যতার প্রবাহকে ভবিষ্যতে বহন করার অন্যতম বাহন।
তথ্য সহায়িকা :
1. Hwo Language Begun, Daniel Everett, 2017
2. Gray's Anatomy, Henry Gray, 42nd edition, October 2020
3. Syntatic Structures, Noam Chomsï, 1957
4. Plato's Cratylus, D Sedly, Nov. 2003
৫. চর্যাগীতিকা, মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা
৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম
৭. অন্তর্জাল