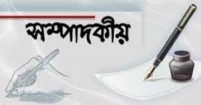প্রকাশ : ২২ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯:২১
দেশের অর্থনীতিতে নীতিগত কোনো পরিবর্তন আসবে?

বাংলাদেশ একটি পুঁজিবাদী নির্ভরশীল অর্থনৈতিক রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা। তার ওপর বিগত পতিত সরকারের সময়ে দেশের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যে নৈরাজ্য ও লুটতরাজ সৃষ্টি হয়েছে, জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর সে সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের প্রত্যাশা করেছিল মানুষ এবং এ ঘটনায় দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাগুলো আরো তীব্র হয়ে উঠে। একই সঙ্গে তৈরি হয়েছিল জনকল্যাণমুখী নীতি বাস্তবায়ন আকাঙ্ক্ষা। যদিও বাস্তবতা হচ্ছে পাঁচ মাসের অধিক অতিক্রান্ত হচ্ছে, পতিত সরকারের মতোই আইএমএফের নির্দেশ-দর্শনেই চলেছে দেশের অর্থনীতি। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরেও দেশের অর্থনীতিতে নীতিগত তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি।
বিশেষজ্ঞরা বলতে চেয়েছেন, নব্বইয়ের দশকে পুঁজিবাদী আলোকে বেসরকারি খাতের উত্থানের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতিতে অনেকটা নতুন যুগের সূচনা হয়। স্থানীয় উৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি রফতানিতেও বেশ কিছুটা সাফল্য আসে। এর প্রভাবে অর্থনীতিও বিকশিত হতে থাকে। তবে বিগত পতিত সরকারের সময়ে দেশের অর্থনীতিতে কিছু পরিবর্তন হলেও রাজনীতির পাশাপাশি অর্থনীতিতে আবির্ভাব হয় অলিগার্ক বা গোষ্ঠীতন্ত্রের। উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির অন্তরালে অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিজস্ব ঘরানার ব্যক্তিদের কাছে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় নীতিও এ শ্রেণিকে সুবিধা দেয়ার জন্যে তৈরি হতো। এমনকি নিজেদের স্বার্থে প্রয়োজনে নীতির পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতাও ছিল অলিগার্কদের হাতে। পতিত সরকারের শেষ বছরগুলোয় অর্থনীতিতে অনেকটা বিপর্যয়ের মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে আইএমএফ-এর দ্বারস্থ হয় সরকার। সে সময় সংস্থাটির পক্ষ থেকে বেশ কিছু সংস্কারের শর্ত বেঁধে দেয়া হয় এবং অনেকগুলো খাতে ভর্তুকি কমিয়ে আনতে চাপ প্রয়োগ করে। এসব শর্তই অর্থনীতিতে শেষ পর্যন্ত পতিত সরকারের দর্শন হয়ে দাঁড়ায়। এ দর্শন থেকে বেরিয়ে আসেনি বর্তমান অন্তর্র্বতী সরকারও। তবে আদৌ এ সরকার উক্ত নির্দেশ-দর্শন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে কি?
আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশনে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানো বা এতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনার প্রয়াস কখনো সফল হতে দেখা যায়নি। যদিও বাংলাদেশ এখনো অর্থনীতির মূল দর্শনকে এ প্রেসক্রিপশনের বাইরে আনতে পারেনি। এতে বৈষম্য বাড়ছে। যদিও দেশে সংঘটিত ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মূল দর্শনই ছিল বৈষম্য দূর করা। তাই বললে বলতে হয়, বর্তমান অন্তর্র্বতীকালীন সরকার এই নীতিতে থেকে আদৌ বৈষম্য দূর করতে পারবে? বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমরা যদি অতীতের দিকে তাকাই, তাহলে দেখবো যে আশির দশকে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্যে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলাম। শুধু আমরা নই, অন্য অনেক দেশও নিয়েছিলো। এ ধরনের ঋণ কিন্তু ভালো কিছু বয়ে নিয়ে আসেনি। অতীত অভিজ্ঞতা কিন্তু দেখায়, এ ধরনের সহায়তা প্রকল্প সমস্যা সমাধানে বিশেষ করে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানো বা কাঠামোগত পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে হোক, অতীতে কখনো সফল হয়নি। এবারও যে জুলাই-আগস্টের চেতনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কোনো পরিবর্তন আসবে সেটা আমার কাছে মনে হয় না।’
আমাদের দেশে বিগত বছরগুলোতে অর্থনীতির কাঠামোগত যে বিবর্তন হয়েছে, সেটির কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসমতা বেড়ে গেছে, যেটিকে আমরা বৈষম্য বলি। এই বৈষম্য কমিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন আনার ক্ষেত্রে আইএমএফ কিংবা বিশ্বব্যাংকের নীতিগুলো ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে হয় না, যা অনেক বিশেষজ্ঞদের ধারণা। অথচ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মূল কথা ছিলো বৈষম্য দূর করে এমন একটি সমাজ গঠন করা, যেখানে সবার কল্যাণ নিশ্চিত হবে। আমরা সে পথে না হেঁটে অন্য পথে হাঁটছি না তো? আর যদি অন্য পথে হাঁটি তবে সে পথ আমাদের বৈষম্যবিরোধী চেতনার সঙ্গে কিংবা '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।
রাষ্ট্রের নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সুরক্ষা, মৌলিক-সেবার নিশ্চয়তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি বৈষম্য প্রশমনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রণীত বাজেটগুলো জনকল্যাণমুখী বাজেট হিসেবে পরিচিত।
বাংলাদেশের মানুষ জনকল্যাণমুখী বাজেট থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে বহু বছর ধরে। এখানে বাজেট মানেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নামে জনগণের অর্থের যথেচ্ছ তছরুপ। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাজেটটিও এর ব্যতিক্রম নয়।
জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ফলে গণবিরোধী এ বাজেট কাঠামো পরিবর্তনের সুযোগ ছিলো। যদিও এখন পর্যন্ত আগের সরকারের প্রণীত বাজেটই বলবৎ রয়ে গেছে। আবার একইভাবে বহাল রয়েছে বিগত সরকারের গৃহীত রাজস্ব ও মুদ্রানীতিও।
বর্তমানে আমরা উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে আছি। মূল্যস্ফীতি হচ্ছে সরবরাহজনিত কারণে, চাহিদাজনিত কারণে নয়। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ক্ষেত্রে সুদহার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি কমবে না। সরকারের জন্যে অলিগার্কদের ম্যানেজ করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। একটা শ্রেণি আছে যারা ট্রেডার। তারা এখান থেকে শোষণ করে অর্থ বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। আরেকটা শ্রেণি আছে যারা এখানে বিনিয়োগ করেছে এবং শিল্পায়নের জন্যে তাকে প্রয়োজন, কিন্তু সে নিজে বড়ো হয়ে যাচ্ছে। এই যে অলিগার্ক ব্যবস্থাপনা, এটি তো আর আইএমএফ কিংবা বিশ্বব্যাংকের নোটবুকে নেই। সরকারের পক্ষ থেকে সংশোধন করে একটি বাজেট তৈরি করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেটিও তো করা হয়নি।
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে প্রায় দুই-তিন বছর ধরে মূল্যস্ফীতির চাপে দিশেহারা দেশের সাধারণ মানুষ। মূল্যস্ফীতি কমাতে সুদহার বাড়ানোর নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল গত ২০২৩-এর জুনে। আওয়ামী সরকার পলায়নপর হলেও একই নীতি অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের নীতিকথা বলে সুদহার উন্নীত করা হয়েছে ১০ শতাংশে। যদিও মূল্যস্ফীতি না কমে উল্টো ডিসেম্বরে এসে ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশ ছুঁয়েছে। আর খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি উঠেছে প্রায় ১৪ শতাংশে। অপরদিকে অতিসংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রভাবে বেসরকারি খাত বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তীব্র তারল্য সংকটে পড়েছে। শ্রমিক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা চলছে দেশের তৈরি পোশাক খাতসহ সব শিল্পে।
বস্তুত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এ সরকার নতুন কিছু করতে পারেনি। প্রচলিত পথেই হেঁটেছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আইএমএফের পরামর্শে কঠোর মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হলেও এর ফলাফল এখনো দেখতে পাইনি। সুতরাং এক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি যথাযথ নজরদারি কাঠামো ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতো, সেটি আমরা দেখতে পাইনি। মানুষ নিরাপত্তার ইস্যুতে, মূল্যস্ফীতির বিষয়ে স্বস্তি চায়।
লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক হাছান আলী সিকদার, সভাপতি, চাঁদপুর জেলা জাসদ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা; চাঁদপুর জেলা শিক্ষক নেতা; সমাজ ও রাজনীতিবিশ্লেষক। রচনাকাল : ১৩/০১/২০২৫।