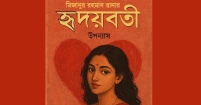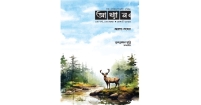প্রকাশ : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৫০
খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ড জীবন

(উনচল্লিশতম পর্ব)
আমার শিক্ষকতা জীবন
শিক্ষা নিয়ে আমাদের এক ধরনের দ্বিচারিতা আছে বাংলাদেশে। আমাদের দেশে শিক্ষা বলতে জ্ঞানের উন্মেষকে বুঝায় না। শিক্ষা এদেশে মানবাত্মার তৃতীয় চক্ষুতে জ্ঞানের সম্মিলন নয়। আমরা এখানে শিক্ষা বলতে বুঝি পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া, সনদ বাগানো এবং সেই সনদের বদৌলতে ভালো একটা চাকরি বাগিয়ে নেওয়া। শিক্ষা এখানে কর্মকে তুচ্ছ করার বোধ নির্মাণ করে এবং কথায় কথায় আমজনতার সাথে নিজের গর্বকে প্রকট করে তোলে। অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিলো আত্ম অবক্ষয় নিরোধ ও মানবিক উন্নত সংস্কৃতির নির্মাণ। আমি হয়তো নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষক ছিলাম না। কিন্তু শিক্ষকতা করার সুযোগ আমারও হয়েছিলো। ঊনিশশো তিরানব্বই সালের শুরু থেকে চট্টগ্রামে ক্ল্যাসিক কোচিং সেন্টারে ক্লাস নিয়েছি টানা ছয় বছর। এ ছয় বছরে অনেক ছাত্রছাত্রীর সাথে আমার সংযোগ ছিলো। মেডিকেল ভর্তি কোচিং, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং এবং কলেজ ভর্তি কোচিংয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিয়েছি কতো তার কোনো হিসেব নেই। কোনো ক্লাসে ইংরেজি, কোনো ক্লাসে বাংলা, কোনো ক্লাসে রসায়ন পড়িয়েছি, যখন যা তাদের দরকার হয়েছে। কোচিং সেন্টারগুলোতে দুঘন্টা করে প্রতিটা ক্লাস। প্রথম আধঘন্টা ছিলো আগের ক্লাসের ওপর ম্ল্যূায়ন অভীক্ষা। পরের দেড়ঘন্টা ক্লাস। প্রতিক্লাসে প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর জন শিক্ষার্থী। ক্লাসে তখন হোয়াইট বোর্ড-মার্কার ছিলো না। চক-ডাস্টারই ভরসা। গলা বাড়িয়ে ক্লাস নিতে নিতে ঘেমে যেতাম যদিও মাথার ওপরে পাখা চলতো। বরং পাখা তখন প্রশান্তির পরিবর্তে বোর্ডে লেখা চকের গুঁড়োকে ছড়িয়ে দিতো আমার নাকেমুখে-মাথায়। দিনশেষে চুলগুলো চকের চুনে মাখামাখি হয়ে অকালে ঝরে গেছে। একটা ক্লাস কেবল পাঠ্যসূচির পাঠদানে সম্পন্ন হয় না। তাতে থাকতে হয় জীবনের গল্প, অনুপ্রেরণার বাণী, শিক্ষার্থীদের অমনোযোগিতার সমাধান, দুষ্ট শিক্ষার্থীর প্রশ্নের তাৎক্ষণিক বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তর ইত্যাদি। এভাবে ক্লাস নিতে নিতে দেখা গেলো অন্য গ্রুপের ছাত্রছাত্রীও আমার ক্লাসে এসে বসে যেতো। পরে বাধ্য হয়ে একই লেকচারের দায়িত্ব সবগ্রুপে আমাকেই দিয়ে দেওয়া হলো। তাতেই রক্ষা। নাহলে মাইক ছাড়া এতো শিক্ষার্থীর কানে পৌঁছাতে আমার কণ্ঠনালীর দফরফা হয়ে যেতো। মেডিকেল ভর্তি কোচিংয়ের ক্লাসগুলো নিতে গেলে প্রচুর কথা বলতে হতো। কারণ উত্তরের চারটা অপশনের মধ্যে কোনটা কেন নয় তা বলতে গেলে প্রচুর ব্যাখ্যা দিতে হতো। ফলে প্রশ্ন তিরিশটা হলে কী হবে আসলে একশো কুড়িটার সমাধান দিতে হতো। তাতে আবার দ্বিমত-ত্রিমতের সমাধান করতে হতো। ফলে ক্লাস নিয়ে যা পেতাম তার দুই-তৃতীয়াংশ খরচ হয়ে যেত ক্লাস শেষে ঠাণ্ডা কোমল পানীয় আর কেক-বিস্কুট খেতে। শিক্ষার্থীদের সুবিধা ছিলো, তারা তাদের লেকচারের বিষয়গুলো আগে জানতো, রুটিনের বদৌলতে। ফলে ক্লাসের দিন জটিল ও বিব্রতকর প্রশ্নের জোয়ার ছুটে আসতো আমার কাছে। তখন দক্ষ মাঝির মতো বৈঠা বেয়ে সে জোয়ারে টিকে থাকতে হতো। ইংরেজি ক্লাস নিতে নিতে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিংয়ের শিক্ষার্থীরা আমাকে একটা নামের খেতাবও দিয়েছিলো আমার অলক্ষ্যে। তারা বলতো আজকে ইংরেজের ক্লাস। বলতো না, আজকে ইংরেজি ক্লাস। তাদের অত্যাচারে মাঝে মাঝে চাপার জোর দেখাতে হতো। বিতার্কিক ছিলাম বলে বেশ কয়েকবার চাপার জোরেই উৎরে গেছি কৃতিত্বের সাথে। শিক্ষার্থীদের সমীহের বাইরে কিছু কিছু উপহারও পেতাম। কেউ একজন বলেছিলো, ভাইয়া, আপনার কখনও যদি রক্ত লাগে তবে আমাকে বলবেন, আমি দেবো। কেউ একজন একটা দামি সিগারেট-লাইটার এনে আমাকে দিতে চেয়েছিলো। আমি অধূমপায়ী বলে তা নিতে পারিনি, ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। একজন শিক্ষার্থী জানতো, আমাদের আন্তঃবর্ষ টেবিল টেনিস খেলায় মিশ্র দ্বৈত জুটি হতো। সে আমাকে আগাম বুকিং দিলো, চান্স পেলে মেডিকেল কলেজে সে আমার মিশ্র দ্বৈতের জুটি হবে। সে বোধ হয় ভালো টেবিল টেনিস খেলতে পারতো। একবার এলাকার চাঁদাবাজ এসে আমাদের কাছে চাঁদা চায়। এটা নিয়ে ঝামেলা হওয়ায় তারা আমাকে টেনে নিয়ে যাবে নিচে মেরামত করার জন্যে। কিন্তু আমার স্টুডেন্টরা আমার সাথে ছিলো বিধায় চাঁদাবাজরা সুবিধা করতে পারেনি কোনো। একবার দরকারি কাজে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে দেখলাম কোথা থেকে আমার সেসব শিক্ষার্থী বের হয়ে আসছে। ওরা বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন বর্ষে পড়ে। এ যেন এক মিলন মেলা হয়ে গেলো। আমাকে ক্লাস নিতে হতো তিন শাখায়। কাতালগঞ্জ, নাসিরাবাদ আর আগ্রাবাদ শাখায়। কাতালগঞ্জ ছিলো প্রধান শাখা। একশাখা থেকে আরেক শাখার যাওয়ার বিরতিটাই ছিলো আমার বিরাম। ক্ল্যাসিকে আমার বন্ধু ছিলো রাজু। বড়ো মজার মানুষ। সুদর্শন এবং সুরসিক। তার ক্লাস ছিলো বাংলা আর কখনও কখনও সাধারণ জ্ঞান। রাজুর বাবা ছিলেন এক সময় বান্দরবানের সিভিল সার্জন। আরেকজন ছিলেন। বুয়েটের সালাউদ্দিন ভাই। তিনি অনেক অনেক ডার্টি জোকস বলতেন। শিক্ষার্থীদের সাথে তখন বেশ মজার এবং সহজ দিন কাটতো।
মেডিকেল ভর্তি কোচিংয়ের মাস্টারি শেষে বিরতি পড়ে প্রায় পনের বছর। তারপর আবার শুরু হয় বিতর্কের শিক্ষকতা। চাঁদপুর রোটারী ভবন, যা এখন ডা. নূরুর রহমান কনফারেন্স হল, তাতে একটা কর্মশালায় ক্লাস নিই। এ কর্মশালায় ডা. আব্দুন নূর তুষারও ক্লাস নিয়েছেন। এটা ছিলো প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের বিতর্ক কর্মশালা। উদ্দেশ্য ছিলো তাদের প্রশিক্ষণ দিলে তারা গিয়ে স্ব স্ব স্কুলে শিক্ষার্থীদের মেন্টর হিসেবে কাজ করতে পারবেন। এ ক্লাসটা বেশ জনপ্রিয়তা পায়। সবার মধ্যে একটা অনুপ্রেরণা তৈরি হয়। এটার গুরুত্ব অনুধাবন করে সাব্বির ও শাহাদাত ভাই একটা পুস্তিকা প্রকাশ করলেন, ‘বিতর্ক বিধান’ নামে। সম্পাদক সাব্বির এবং প্রকাশক টিআইবি। বড়োদের ক্লাস নেওয়া একটু সংকোচের বিষয় হলেও তাদের সহযেগিতার কারণে ক্লাসটা প্রাঞ্জল হয়ে যায়। এ কর্মসূচির সাফল্যের পর বিতার্কিকদের কর্মশালা শুরু হয় বছর কয়েক পরে। তবে শিক্ষার্থী অতিরিক্ত হওয়ায় কখনও কখনও ক্লাসগুলো দীর্ঘায়িত করতে হয়েছে। ফলে কেউ উপভোগ করলে কেউ বিরতি চেয়েছে। কেউ বিরতি শেষে ফিরে আসলে কেউ আবার ওয়াশরুমে যেতে চেয়েছে এমন। কিন্তু দিনশেষে বুঝা গেছে, অখণ্ড মনেযোগ সবারই ছিলো। তবে শূন্য থেকে শুরু করা হবু বিতার্কিকদের জন্যে একটু কঠিন হয়েছিলো বলে মনে হয়। কারণ বিতার্কিক পরিভাষার সাথে তারা পরিচিত ছিলো না। এরপর দুহাজার ঊনিশ সাল থেকে তো শুরু হয়ে গেল বিতর্ক একাডেমির কার্যক্রম। অধ্যক্ষ হিসেবে ক্লাস যেমন নিয়েছি, তেমনি পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করার কঠিন কাজও করেছি। বিতর্ক একাডেমিতে অন্য প্রতিষ্ঠানের কিছু বিতর্ক-শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়েছিলো। তারা মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম কিছু দাবি তুলতো। বুঝতাম, এগুলো আসলে প্রেরিত। তবে বিতর্ক একাডেমিতেও এমন এমন শিক্ষার্থী এসেছে যারা তখনও ভালোভাবে কথা বলতে পারতো না। নিজের সম্পর্কে বলতে দিলে এক মিনিট বলাটাই কষ্ট হতো। এরা আসলে বিতর্ক ক্লাসের চেয়ে বক্তৃতা ও উপস্থাপনার ক্লাসে যোগ দিলে ভালো হতো। এতে পরবর্তীকালে বিতর্ক শেখাটা সহজ হয়ে যেতো। কিন্তু অভিভাবকের আবেগের পারদকে সামাল দিতে গিয়ে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে। এদেরকে বিতর্কের চলক এবং চাতাল বুঝিয়ে আনতে যেমন বেগ পেতে হয়েছে, তেমনি পাঠ্য বইয়ের বাইরে সৃজনশীল ও মননশীল অন্য কোনো বই পড়ার অভ্যাস না থাকায় যুক্তি নির্মাণের রসদ সরবরাহে গন্ধমাদন পর্বত বহনের মতো কষ্ট হতো। বিতর্কের প্রপঞ্চ ও প্রত্যয় নিয়ে বলতে গেলে খুদে এ শিক্ষার্থীরা মুখের দিকে অবাকপানে চেয়ে থাকতো। যদিও বিতর্ক প্রশিক্ষণ মানে কোনো শিশুকে তার যুক্তিসম্মত মতামত তুলে ধরতে সাহায্য করা, তবু বলতে হয়, নির্ভয়ে বলতে না শেখার আগে বিতর্ক শিখতে আসা মানেই ঝিনুকে সাগর সেঁচার শামিল। বিতর্ক শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের কাছে ‘সিসি’ ক্যামেরা তকমা পেয়ে আমার একটু হাসিই পেতো। এটা কি সু অর্থে না বকা অর্থে তা বুঝে উঠতে পারিনি। তবে মনে হয়েছে, চোখ বন্ধ করে থাকলেও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুনে যেতাম যা বুঝা যেত বিচারকার্যের মূল্যায়ন সম্পর্কে বলতে গেলে। আর তাতেই তাদের মনে হতো, আমার স্মৃতিতে বিতার্কিকদের সকল ত্রুটি মজুদ আছে।
বয়সে ও ব্যক্তিসত্তায় পরিণত হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষকতায়ও আসলো পরিবর্তন। এবার যুক্ত হলাম ম্যাটস-এর শিক্ষক হিসেবে। ম্যাটস হলো মেডিকেল স্টুডেন্টস্ ট্রেনিং স্কুল। এতে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করা শিক্ষার্থীরা আসতো ডাক্তারের সহকারী হওয়ার শিক্ষা ও সনদ পেতে। তিন বছরের শিক্ষাক্রম। আমি তিন ইয়ারেই ক্লাস নিতাম। প্রথম বর্ষে কমিউনিটি মেডিসিন ও পরে অ্যানাটমি-ফিজিওলজি। দ্বিতীয় বর্ষে প্যাথলজি এবং তৃতীয় বর্ষে মেডিসিন বিষয়ের ক্লাস। প্রতিটা ক্লাস একঘন্টা করে। শিক্ষার্থীরা একটু বড়ো ও বুঝদার হওয়ায় ক্লাস নিতে ভালোই লাগতো। তবে তাদের ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতার কারণে মাঝে মাঝে পড়াগুলো বাংলায় অনুবাদ করে বুঝাতে হতো। কারণ মেডিকেল সংক্রান্ত অধিকাংশ শিক্ষাসূচিতে পাঠদানের ভাষা হলো ইংরেজি। ম্যাটস-এর স্টুডেন্টরা সবাই এসএসসি-এইচএসসির দ্বিতীয় সারির মেধা সম্পন্ন। কাজেই এদেরকেও লাইনে আনতে বেগ পেতে হতো। পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখতে দিলে বাক্যগুলো হয়তো ভুল হতো, বানানগুলো বেঠিক হতো, কিন্তু প্রশ্নে চাওয়া উত্তর ঠিক হতো। এদের আরও একটা বেকায়দা ছিলো। তাদের অনেকেই পাশাপাশি কলেজে বা অনার্সে ভর্তি ছিলো এবং ওখানেও ক্লাস করতো। একে তো অত শার্প মেধাবী ছিলো না, তার ওপর আবার অতিরিক্ত পড়ার চাপ। এদুটো তাদের চিড়ে চ্যাপ্টা বানিয়ে দিতো। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হতো ইন্টার্নাল হিসেবে পরীক্ষার সময় ভাইবা নিতে। ওদের ক্লাসে যা পড়িয়েছি তা-ই জিজ্ঞেস করলেও তাদের উত্তর দিতে কষ্ট হতো। তারা এমন ভুলো মন ছিলো ( কিংবা উদাসীন), ভাইবা পরীক্ষার সময় হোয়াইট কোট আনতো না। ফলে অনেক সময় মেয়েদেরটা হলেও ধার করে পরতো। অনেকের হোয়াইট কোট বুঝা যেতে না কোন ইঁদুরের গর্ত থেকে বের করে এনেছে। দুমড়ানো, কোঁচকানো। রংজ্বলা, হলদে, মলিন। তবুও ভাইবা নিতাম। একবার না পারলে বলতাম, সবার পরে আবার আসো। তাতেও কাঙ্ক্ষিত ফল আসতো না। ভাইবা নিতে গেলে একটা কমন প্রশ্ন থাকতো, ‘ হোয়াট ইজ হেলথ?’ উত্তরটা একটু বড়ো। তারা উত্তর দিতে গেলে দেখা যেতো, আমি বলেছি দু তৃতীয়াংশ আর তারা বলেছে বাকিটা। মনে হয় আমিই তাদের ছাত্র। পরীক্ষা আমাকেই দিতে হচ্ছে। ভাইবা পরীক্ষার সময় সঞ্জয় কর্মকার বা সুখন সাথে থাকতো। সে তাদের কম্পিউটার ক্লাস নিতো। পাশাপাশি ম্যাটসের প্রশাসনিক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করতো। ভাইবা দেখে সে মুচকি হাসতো। বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বলতো, দাদার কাছে পাস না করলে কার কাছে করবে? আমার মন চায় আমিই দাদার কাছে ভাইবা দিয়ে আসি। তবে তাদের কেউ কেউ সত্তর ভাগ নম্বরও পেয়েছে তাদের অধ্যয়ন ও পারঙ্গমতার কারণে। এদের কেউ কেউ আবার তাদের মায়ের বানানো আমসত্ত্ব দিয়ে যেতো আমার গৃহকর্ত্রীর জন্যে। তিনিও কখনও কখনও তাদের বাসায় ডেকে পায়েসান্নে মুখ মিষ্টি করিয়েছেন। এই শিক্ষার্থীরা বাসায় কেক-মিষ্টি এনে আমার জন্মদিনও উদযাপন করেছে। আমার সেসব শিক্ষার্থী চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে ইন্টার্ন করে এখন বিভিন্ন জায়গায় মাঠপর্যায়ে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে। তারা প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্বটা বেশ ভালোভাবেই পালন করছে। (চলবে)