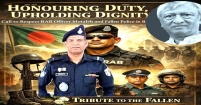প্রকাশ : ২৮ জানুয়ারি ২০২৩, ০০:০০

অর্থনীতি যেমন রাজনীতিকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি রাজনীতিও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। (মার্কসবাদীগণও এ মতবাদ স্বীকার করেন)। অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. ল্যাস্কীর মতে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাদের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত দেখা যায় তারাই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাই এর ব্যতিক্রম নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক জীবনধারাকে প্রভাবিত করে এবং তারা রাজনৈতিক উপাদানের প্রভাব দিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ভূমিকা রাখেন।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনীতির সূচকে উন্নয়নের নানা মাত্রায় বাংলাদেশের অর্জন দেশ এবং সারা বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে। তবে পরিবর্তনের সাথে সাথে আকাঙ্ক্ষা ও চ্যালেঞ্জের জগৎ পাল্টাচ্ছে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতিতে কিছু উদ্বেগের জায়গা ঘনীভূত হয়েছে। সরকারের পরিসংখ্যান সংস্থার প্রদত্ত সর্বশেষ তথ্যমতে, দারিদ্র্যের হার বেড়েছে এবং তা ২৯ দশমিক ৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। কোভিড পূর্ববর্তী সময়ে যা ২০ শতাংশে ছিল। এ দারিদ্র্যের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক হতাশা বর্তমানে চরম সংকটের দ¦ারপ্রান্তে পৌঁছাচ্ছে প্রায়। এসব হতাশা তৈরি হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থনীতি পরিচালনার রাজনৈতিক অর্থনীতি থেকে।
বাংলাদেশ ইদানিং কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন। প্রথমত : দুর্নীতি কি শুধু নৈতিক ব্যর্থতা নাকি তা বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক অর্থনীতির অনুষঙ্গ? দ্বিতীয়ত : সংস্কারে অনীহা কিংবা অদক্ষতার প্রশ্ন না দুর্নীতিগ্রস্ত স্বার্থকে আড়াল করার প্রবণতা? তৃতীয়ত : বাস্তবায়নগত দুর্বলতা কিংবা সক্ষমতার অভাব না মেধার নিরন্তর অবমূল্যায়নের ফল? ইত্যাদি।
বাংলাদেশে অর্থনীতি সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে ঘাটতি সব সরকার আমলে সবসময়ই ছিলো। কিন্তু গত এক দশকে নীতি প্রণয়নের রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। এক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রবণতাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।
প্রথমত : একমাত্রিক উন্নয়ন দর্শন। উন্নয়ন ধারণার অবকাঠামোই সব। এ দর্শন সামাজিক উন্নয়নকে পাশে ঠেলে দিয়েছে। শিক্ষার মানের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভবন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যসেবার মানের চেয়ে হাসপাতাল ভবন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নগর অবকাঠামো ইন্টিগ্রেটেড ও বাসযোগ্যতাকে প্রধান্য না দিয়ে বিচ্ছিন্ন অবকাঠামোর সমাহারে রূপান্তরিত হচ্ছে। একমাত্রিক উন্নয়ন দর্শনের ফল উদাহরণ কল্পে বলা যায়, সড়ক নিরাপত্তার শঙ্কাজনক ঘাটতি এবং নিরাপদ ভ্রমণের অনিশ্চয়তা, শিক্ষার মানের নিম্নগতি, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ছাড়াই স্বাস্থ্যসেবা অধিক ব্যয়বহুল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।
দ্বিতীয়ত : অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে গোষ্ঠী কিংবা শ্রেণীস্বার্থের আধিক্য। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অলিগার্কীব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, যা উৎপাদনশীলতা নিরুৎসাহিত করছে এবং সম্পদ পাচারকে উৎসাহিত করছে। সংকীর্ণ বেসরকারি স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে যে ধরণের পুঁজিবাদী কায়দায় অনৈতিক নিয়ম সাজানো হয় তা উদ্বেগজনকভাবে আর্থিক সংস্থান, ব্যাংক খাত, বিদ্যুৎ, পরিবহনব্যবস্থা, আইসিটি এবং লাভজনক খাতে স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলতে হয়, কেন গ্যাস অনুসন্ধান না করে অতিরিক্ত নির্ভরতায় ব্যয়বহুল এলএনজি আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছিল? কেন ভোলা গ্যাস ফিল্ডে বিদেশী কোম্পানিকে সুবিধা দিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বাপেক্সকে কৌশলগতভাবে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হলো? সার্বিক বিষয়টি অর্থনৈতিক নীতি দিয়ে পরিচালিত হয়নি, বরং গোষ্ঠীস্বার্থ প্রভাবিত রাজনৈতিক অর্থনীতির মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছে। পরিবহন খাতের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিআরটিসি বহু বছর ধরেই একটি রুগ্ন রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি হয়ে আছে। অন্যদিকে রুট পারমিট বরাদ্দ দেয়ার বিষয়টি পরোক্ষভাবে বেসরকারি বাসমালিকদের কব্জাধীন হয়ে আছে। ফলে বিআরটিসি কোথাও তার ওপর ন্যাস্ত দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। বেসরকারি খাতের স্বার্থ দেখতে গিয়ে সুশাসন ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করার এ প্রবণতা কার্যত অপশাসনের অচলাবস্থাকে চলমান রাখার ক্ষেত্রে দায়মুক্তি দেয়। এক্ষেত্রে পি কে হালদারের মামলাটি এসব জুড়ে বসা প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তিযোগ্য অব্যবস্থাপনার প্রতীক হিসেবে গণ্য হতে পারে।
তৃতীয়ত : অন্যায্য অর্থনীতি। যা শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, এমনকি বর্তমানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাদের রাজনীতিতে উচ্চকণ্ঠ নেই তাদের স্বার্থকে উপেক্ষা করার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। গণপরিবহন ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য, উপযোগিতার খরচ, মানসম্মত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ-এর সব ক’টিই মানসম্মত জীবন-যাপনের ভিত্তি। কিন্তু সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর অনেকটা প্রান্তিক হয়ে যাওয়ায় নীতির জগতে এ বিষয়গুলো খাপছাড়া আকর্ষণের ঊর্ধ্বে উঠতে পারছে না। আর ঝুঁকিপূর্ণ পথে রয়েছে মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে যাওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং তরুণ বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব বেড়ে যাওয়া।
সর্বোপরি সচেতন মহলের সাথে একাত্মতা প্রকাশান্তে বললে বলতে হয়, বাংলাদেশ সম্ভবত উন্নয়ন যাত্রার বাঁকবদলের পর্যায়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে সফলতার মুখ দেখা অন্য দেশগুলো মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়েছে, কারণ তারা সতর্ক সংকেতগুলো মানেনি এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলোকে মূল্যায়ন করেনি। এ অবস্থায় বাংলাদেশ কি তার উদ্বেগের জায়গা মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে? বাংলাদেশের স্থিতিশীল উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে কাঠামোগত বাধায় রূপান্তরিত হয়েছে। এটির অপসারণ শুধু সুপারিশ ও শ্রুতিমধুর কথার মাধ্যমে হবে না। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উপলব্ধি, পন্থা এবং দৃঢ় ইচ্ছা-এই তিন জায়গাতেই জোরালো দৃষ্টি এবং প্রেসার প্রয়োজন।
লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক মোঃ হাছান আলী সিকদার, সভাপতি, চাঁদপুর জেলা জাসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা, চাঁদপুর জেলা শিক্ষক নেতা, সমাজ ও রাজনীতি বিশ্লেষক।