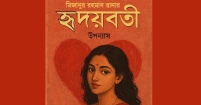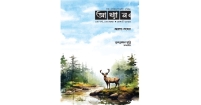প্রকাশ : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ০০:০০
ইতিহাসের শোক : একুশে ফেব্রুয়ারি
ভাষা আন্দোলন কেবল আমাদের মুখের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেনি, দিয়েছে বাঙালির জাতিসত্তার জাগরণের প্রথম অনুপ্রেরণা, দেশপ্রেম, সাহস, আবেগ। এই আন্দোলন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণের উজ্জ্বীবিত হাতিয়ার। পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র বাঙালি জাতি ভাষার জন্যে যুদ্ধ করে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই গর্বিত ইতিহাস হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। আজকের বাঙালির ইতিহাস হাজার বছরের পুরানো। সেই পুন্ডু, রাঢ়, গৌর, নিষাদ, অস্টিক, দ্রাবিড়, আর্য, মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, সুলতান, শাহী, মোঘল, সম্রাট, নবাব, পলাশী, ব্রিটিশ, দ্বিজাতি তত্ত্ব হয়ে আজকের বাঙালি। প্রতিটি রক্তক্ষয়ী ঘটনা প্রবাহ বাঙালির অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রাম। ভাষা আন্দোলন সেই ধারার একটি।
ঐতিহ্যগতভাবে পাকিস্তানে মুসলমানদের বসবাস। উর্দু একটি ইন্দো আর্য ভাষা। এই ভাষায় ফার্সি, আরবি এবং তুর্কির ঘনিষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করেছে। দিল্লীর সুলতান ও মুঘল সাম্রাজ্যের সময় দক্ষিণ এশিয়ায় পারসিক আরবি লিপির কারণে উর্দু ভারতীয় মুসলমানদের ইসলামী সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত ছিলো এবং হিন্দিকে হিন্দু ধর্মের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এ কারণে মুসলমানদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে খাজা সলিমুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নবাব ওয়াকার উল মুলক মৌলভী প্রমুখদের চেষ্টায় ভারতের মুসলমানদের উর্দু ভাষার লিঙ্গুয়া ফ্রঙ্কার উন্নত হয়। অপরদিকে পূর্বাঞ্চলীয় বাংলা নবজাগরণের সময় বেশির ভাগ মুসলিম মনীষী বাংলা ভাষায় সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চা শুরু করে, ফলে পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে বাংলা জনপ্রিয় হয়ে উঠে।
দেশ ভাগের বহু আগ থেকেই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভাষাগত অমিল ছিলো। ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় ভাষা প্রসঙ্গটি আলোচনা করা হয়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে সে সময় প্রাধান্য দেয়া হয় বেশি, ফলে ভাষা বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে রংপুরে প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনে সৈয়দ নওয়াব আলী বাংলাকে ভারতের অন্যতম ভাষা হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানায়। ১৯১৮ সালে ড. মুহাম্মদ শহীদ উল্লাহ বিশ্ব ভারতীয় সম্মেলনে বাংলাকে ভারতের সাধারণ ভাষা করার দাবি তোলেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মৌলানা আকরাম খাঁ বাংলাকে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি তোলেন। একই বছর ১৭ মে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দু করার প্রস্তাব করলে ড. মুহাম্মদ শহীদ উল্লাহ তার বিরোধিতা করেন। ১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএম হলে প্রথম বাংলা সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ২৯ জুলাই দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ড. মুহাম্মদ শহীদউল্লাহ ‘পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা’ শিরোনামে জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওয়ার পর ১৫ সেপ্টেম্বর তমুদ্দুন মজলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা বিতর্ক আয়োজন করে এবং এই তমুদ্দুন মজলিশ ও এর প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলন বেগবান হয়। একই বছর ডিসেম্বর মাসে তমুদ্দুন মজলিশের নেতৃত্বে রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। করাচিতে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার সুপারিশ করলে সেখানে তাৎক্ষণিক পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা তা প্রত্যাখ্যান করে প্রতিবাদ করে এবং দাবি জানায় বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার। এ সময় পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন বাংলাকে অনুমোদিত তালিকা থেকে বাদ দেয় এবং মুদ্রা, ডাক টিকেট থেকে বাংলা তুলে দেয়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত দাবি জানান, গণপরিষদে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের। ১৯৪৮ সালে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। একই বছর ১৯ মার্চ পাকিস্তান গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ২১ মার্চ সোহরাওয়াদী উদ্যানে আয়োজিত সমাবেশ ঘোষণা করেন ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা’ এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ঘোষণা দিলে ছাত্ররা তখনই প্রতিবাদ জানায় এবং বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্যে স্লোগান দিতে থাকে।
দেশ ভাগের সময় পাকিস্তানের জনসংখ্যা ৬ কোটি ৯০ লাখের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লাখ বাংলা ভাষার অধিকারী ছিল। বিশাল এ জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা মেনে নেয়াও ছিল অযৌক্তিক। তাই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কোনোভাবেই জিন্নাহর প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারে নি।
১৯৫০ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার ভাষা উন্নয়ন কমিটি গঠন করে এবং বাংলা বাদ দিয়ে সর্বত্র উর্দু ব্যবহার শুরু করে। এ সময় আবার মিশর বণিক সমিতি পাকিস্তানের কাছে আবেদন জানায়, আরবিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার। ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ ভাষা দিবস উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান হরতাল পালন করে। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন পল্টন ময়দানে জিন্নাহর মতই প্রকাশ্য ঘোষণা করেন, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। তিনি ভেবেছিলেন সুদীর্ঘ চার বছর পর পূর্ব বাংলার কেহ রাষ্ট্র ভাষার ব্যাপারে কোনো কথা বলবে না। কিন্তু পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের বক্তৃতায় প্রকাশ্য বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং ২৭, ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি ধর্মঘট পালন করে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সাথে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবি জানায়। ৩০ জানুয়ারি কাজী গোলাম মাহমুদকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এ সময় বিভিন্ন দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আলাদা আলাদা কর্মসূচি পালন করে। মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি আওয়ামী মুসলিম লীগ সরাসরি অংশগ্রহণ করবে।
সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধর্মঘট, মিছিল, আলোচনা সভা, মানববন্ধন, বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘটে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং ঢাকার রাজপথে ছাত্রদের বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন সরকার পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা যায়। দুপুরের পর ছাত্র নেতাদের মধ্যে আবদুল মতিন এবং গাজীউল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৩টা ১০ মিনিটে মিছিল শুরু করলে পুলিশ লাঠিচার্জ, গ্রেফতার ও গুলিবর্ষণ করে। এতে জব্বার, বরকত, সালাম, রফিক, ৯ বছরের শিশু অলিউল্লাহসহ ৫ জন নিহত হয়, ১৭ জন আহত, ৫২ জন গ্রেফতার হয়। ৩ ঘন্টাব্যাপী সংঘাত চলতে থাকলেও ছাত্রদের স্থানচ্যুত করতে পারেনি পুলিশ। সন্ধ্যা নাগাদ ছাত্রদের সাথে সাধারণ জনতা যুক্ত হয়।
২২ ফেব্রুয়ারি হাজার হাজার ছাত্র জনতা নিহতদের জানাজার নামাজ আদায় করে একটি শোক মিছিল বের করে। সেই মিছিলে পুলিশের গুলিতে শফিউর রহমানসহ আরো ৪ জন নিহত হয়। উত্তেজিত জনতা সে সময় সরকার পক্ষের পত্রিকা দি মনিং নিউজ-এর অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। উত্তেজনা শহর ছাড়িয়ে গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সমস্ত পূর্ব বাংলা আগুন-গর্ভে পরিণত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পাশে শহীদ স্মরণে প্রথম শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা। ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৯৫৪ সালের ৭ মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৫৬ সালে প্রথম সংবিধানে ২১৪নং অনুচ্ছেদে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উল্লেখ করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা করে।
স্বাধীনতার পর ১৯৮৭ সালে এরশাদ সরকার বাংলা ভাষা প্রচলন আইন পাস করে। ১৯৯৯ সালে ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।
১৯৫৪ সালে যুক্তফন্ট নিবার্চন, ’৬৬ সালের ৬ দফা, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভাষা আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করেছে। বাঙালি জাতির শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে ভাষা আন্দোলন যেন এক অবিচ্ছিন্ন অংশ। এ দেশের শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক তাদের কলমের আকরে তুলে ধরেছেন রক্তবর্ণ প্রতিবাদ। একুশ ফেব্রুয়ারি নিয়ে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত গান ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’। কবি আল মাহমুদ লিখেছেন, ‘ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ, / দুপুর বেলার অক্ত/ বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়?/
বরকতের রক্ত’।
কবি আবদুল হাকিম বঙ্গবাণী কবিতায় লিখেছেন- ‘যেসব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী /সে সব কাহার নির্ণয় ন জানি’।
অতুলপ্রসাদ সেন লিখেছেন- ‘মোদের গরব মোদের আশা, আমারি বাংলা ভাষা’।
২১ নিয়ে প্রথম কবিতা ‘কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’ লিখেছেন মাহাবুবউল আলম। প্রথম শহীদ মিনার যখন ভেঙ্গে ফেলা হয় তখন আলাউদ্দিন আল আজাদ লিখেন-‘স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার?/ভয় কি বন্ধু/ আমরা এখনো চার কোটি পরিবার খাড়া রয়েছি তো’।
ভাষা শহীদদের নামে প্রথম কবিতা লিখে হাসান হাফিজুর রহমান। আবু জাফর ওবায়েদ উল্লাহর কালজয়ী কবিতা ‘কোন এক মাকে’।
আল মাহমুদণ্ডএর একুশের কবিতা ফেব্রুয়ারি ২১ তারিখ, জহির রায়হানের উপন্যাস ‘আরেক ফাগুন’, সেলিনা হোসেনের ‘যাপিত জীবন’, শওকত ওসমানের ‘আর্তনাদ’, মুনির চৌধুরীর নাটক ‘কবর’, জহির রায়হানের চলচ্চিত্র ‘জীবন থেকে নেওয়া’, ‘মুখ ও মুখোশ’। আবদুল গাফফার-এর গান ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি?। প্রভাত ফেরির এই গান বিবিসি দর্শক জরিপে বাংলা সেরা গানের তালিকায় তৃতীয় স্থান দখল করে আছে। একুশের বইমেলা, একুশে পদক ইত্যাদি ভাষা আন্দোলনকে চির ভাস্বর করে রেখেছে বাঙালি জাগরণের ইতিহাসে।
লেখক : মোঃ আবদুল বাতেন, প্রভাষক, গৃদকালিন্দিয়া হাজেরা হাসমত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চাঁদপুর।
মোবাইল : ০১৭১৪৪১৭১৭৪