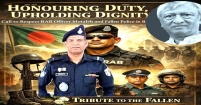প্রকাশ : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ০০:০০
মানুষের ভাষা ভাষার মানুষ

মানুষের মূক মুখে ভাষা কখন জুড়ে বসলো তার কোনো সঠিক হিসেব জানা নেই কারও কাছে। যেহেতু লিখন পদ্ধতির আবিষ্কারও হয়েছে তার অনেক অনেক বছর পরে, তাই মুখের ভাষাকে সবাক মানুষের অতি সূচনালগ্নে লিখে রেখে ভবিষ্যতের জন্যে সংরক্ষণ করার কোনো উপায় ছিল না কোনো মতেই। তাই ভাষার কখন উদ্ভব হলো, কেন এবং কীভাবে হলো, কে বা কারা ভাষার উদ্ভাবন করলো তা জানা দুষ্কর নয় কেবল, অসম্ভবও হয়ে পড়লো। তবে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ হতে যে, মানুষের উদ্ভবের সাথে সাথে ভাষার উদ্ভব হয়নি। ভাষার উদ্ভব মানুষের উদ্ভবের অনেক পরে হয়েছে বলা যায়। ধারণা করা হয়, আদিম মানুষ শিকার করে খেতে গিয়ে ভাষার উৎপত্তি ঘটায়। কেননা শিকার করা বন্যপ্রাণী একাকী খাওয়া যেমন কঠিন তেমনি একা একা হিংস্র বন্যপ্রাণী শিকার করাও কঠিন। হোমো হাবিলিস কিংবা হোমো ইরেক্টাস থেকে নিয়ান্ডার্থাল পর্যন্ত মানুষের পূর্বসূরিরা ভাষার ব্যবহার শেখেনি এটা নিশ্চিত। কেননা, বিজ্ঞানীদের মতামত বিবেচনা করলে বলতেই হয়, স্বর উৎপাদন করার যে যন্ত্র বা ল্যারিংক্স, তা নিয়ান্ডার্থালের ক্ষেত্রে সুবিকশিত ছিলো না। তা ছিলো তাদের গলায় প্রাথমিক পর্যায়ে এবং উপরের দিকে। বিবর্তিত হতে হতে ল্যারিংক্সকে আমরা পেয়েছি আজকের পর্যায়ে। অর্থাৎ এটা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে, ভাষার উৎপত্তিতে হোমো স্যাপিয়েন্সরাই ভূমিকা রেখেছে। যদিও ভাষা বিজ্ঞানী টলারম্যান-এর মতে মানুষের ভাষার ব্যবহারের ইতিহাস পাঁচ লাখ বছরের কম নয়।
আজকের উন্নত জিনবিদ্যা ভাষার ব্যবহার ও ভাষা উৎপাদনের জন্যে মানুষের শরীরে বিদ্যমান জিন ফক্সপিটু-কে (ফর্কহেড বক্স প্রোটিন টু, ঋঙঢচ২) দায়ী করেছে। এই জিনের আবিষ্কর্তা জার্মান বিজ্ঞানী উলফগ্যাং। এটা কেবলমাত্র ভাইব্রেট বা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে স্তন্যপায়ীদের দেহে দেখা গেলেও হোমো স্যাপিয়েন্সের দেহে এটা ছিলো পরিবর্তিত ধরনের। ভাষার উদ্ভব বিষয়ে দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং ক্র্যাটাইলাসের বিতর্কের কথাও উল্লেখ করতে হয়। ক্র্যাটাইলাস নামের সেই সোফিস্ট দার্শনিকের অভিমত ছিলো সকল কিছুর নামকরণের পিছনে একজন নামকর্তার ভূমিকা আছে। এই তত্ত্বকে সক্রেটিস যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দেন এই বলে যে, যদি ভাষার উৎপত্তি আগে থেকেই না হয়ে থাকে তবে নামকর্তা সেই নাম পেলো কোথা থেকে।
ভাষা সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কির কথাকে বিজ্ঞানের তত্ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক বলেই মনে হয়। কেননা নোয়াম চমস্কির মতে ভাষা একটি মানসিক ক্রিয়া কিন্তু মানব অঙ্গসংস্থানবিদ্যা মতে ভাষা উৎপাদনের জন্যে মানব মস্তিষ্কে কিছু অঞ্চল সুনির্দিষ্ট আছে। একে ব্রোকা’র অঞ্চল বলা হয়। আমাদের ভাষা উৎপাদনের এই অঞ্চল হলো ব্রোকা’র অঞ্চল চুয়াল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশ। কোনো ধ্বনিকে শ্রবণ-স্নায়ু মস্তিষ্কে পাঠালে ব্রোকা’র অঞ্চল চুয়াল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশ সেই ধ্বনিকে প্রক্রিয়াজাত করে ভাষা তৈরি করে। এ দুটো অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হলে মুখে বলার গতি শ্লথ হয়ে যায়, কেননা আক্রান্ত ব্যক্তি তখন দ্রুত ভাষা উৎপাদন করতে পারে না। মস্তিষ্কের বাম অর্ধেকে অবস্থিত ব্রোকা’র অঞ্চলের চেয়ে ডান অর্ধাংশের ব্রোকার অঞ্চল কিছুটা দুর্বল। এই অংশ কতিপয় ক্রিয়াপদ উৎপাদন ও কিছু শব্দ বার বার উচ্চারণে ভূমিকা রাখে। কাজেই নোয়াম চমস্কির তত্ত্ব তথা ভাষা উৎপাদন একটি মানসিক প্রক্রিয়া এই কথাটি সর্বাঙ্গে সঠিক নয়। তবে ভাষা উৎপাদনের উদ্দীপকরূপে মানুষের মনের ভূমিকা যথেষ্ট। আসলে ভাষা উৎপাদনে মনের চেয়ে মস্তিষ্কের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নিজের ভাষ্য হতে জানা যায়, তিনি তিন বছর বয়সের আগে কথা বলতে শেখেন নি। তিনি ডিস্লেক্সিয়া রোগে ভুগেছিলেন। ডিস্লেক্সিয়া রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে ভাষা উৎপাদন কেন্দ্রে বিভ্রাট ঘটে। তাদের মস্তিষ্কে ব্রোকা’স এরিয়াগুলো ভালোভাবে বিকাশ লাভ করে না। ফলে তারা শব্দ উচ্চারণে বাধাগ্রস্ত হয়। কোনো শব্দ কীভাবে ভাষায় উচ্চারণ করতে হতো তা তাদের মস্তিষ্ক ঠিক করতে পারে না। আলবার্ট আইনস্টাইনের মস্তিষ্কের বাম পাশের সেরিব্রামে ব্রডম্যান এরিয়া নম্বর ঊনচল্লিশের আকার তুলনামূলকভাবে ছোট ছিলো। এটাই তাঁর কথা বলায় বিলম্বের কারণ ছিলো। জার্মান বিজ্ঞানী অ্যানাটমি বিশারদ করবিনিয়ান ব্রডম্যান মানুষ ও প্রাইমেটের মস্তিষ্কের স্নায়ু-মানচিত্র তৈরি করেন, যাতে তিনি সেরিব্রাম বা গুরু মস্তিষ্ককে বায়ান্নটি অঞ্চলে ভাগ করেন। এই বায়ান্নটি অঞ্চলের মধ্যে ঊনচল্লিশ নম্বর অঞ্চল আমাদের কথা বলার সক্ষমতার সাথে জড়িত। অর্থাৎ এই উদাহরণ থেকে এ কথা বলতেই হয়, ভাবের জন্যে ভাষা মানসিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করলেও ভাষার উৎপাদন কৌশল নির্ভর করে মস্তিষ্কের উপর। কাজেই ভাষা এককভাবে একটি মানসিক প্রক্রিয়া, এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। যে মানুষ ব্যথা পেয়ে কেঁদে উঠে সে আগে ব্যথা অনুভব করে এবং তারপর অনুভূতি প্রকাশ করে। সুতরাং মন নয়, মস্তিষ্কই ভাষার প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণকারী।
আমি একজন শিশুকে জানি যে অতি শৈশবে বলতো, কাকা আমি কাক্কা করবো। কাক্কা মানে হলো মলত্যাগ করা। অর্থাৎ কোন একটা শব্দ দিয়ে শিশু তার প্রয়োজন বা চাহিদা প্রকাশ করতে পারে। সেটা প্রথমবার বুঝতে কষ্ট হলেও পরের বার থেকে বুঝতে আর কষ্ট হয় না। তার মানে মস্তিষ্কে তৈরি হওয়া সংবেদন মনের ভাষায় অনূদিত হলো। এই ভাষা তাকে পারিপাশির্^কতা তৈরি করে দেয়নি। তার সংবেদন এ ভাষাকে ধ্বনি দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নিয়েছে। কোনো কোনো শিশু ছোট বেলায় মাতৃস্তন্য পান করতে চাইলে বলতো ‘মাম’ খাবো। এখনো মাতৃস্তন্য বুঝাতে ‘মাম’ই বলে কেউ কেউ। এই ‘মাম’ তাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। শিশু নিজের প্রয়োজনকে শব্দে অনূদিত করে ভাষার অবতারণা করে মাত্র। তেমনি আবার কেউ কেউ পানি খেতে চাইলেও বলতো বা বলে, ‘মাম’ খাবো। কাজেই ভাষা মূলত মস্তিষ্ক আর মন এ দুয়ের সমন্বয়। এককভাবে ভাষা মনের উৎপাদ নয় মোটেই। আবার কেবল যে মস্তিষ্ক একাকী ভাষার উৎপাদনকারী তা কিন্তু নয়। আমরা ‘টারজান দ্য এইপ ম্যান’ ছবিতে দেখেছি, ক্ষুদ্র শিশু অবস্থায় নিবিড় অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া দুগ্ধপোষ্য মানবকলিকে লালন-পালন করে বড় করে তুলেছে শিম্পাঞ্জি মা। মানব শিশু টারজান উন্নত স্বরযন্ত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শব্দ উৎপাদন কৌশল জানা না থাকায় ভাষা আয়ত্ত করতে পারেনি। অর্থাৎ যন্ত্র থাকলেও প্রকৌশল জানা না থাকায় কেবলমাত্র মানসিক সক্রিয়তা দিয়েও সে কথা বলতে শেখেনি।
ভাষার প্রকারভেদে যেমন জৈব ভাষা, অজৈব ভাষা, মান ভাষা বা প্রমিত ভাষা, সাধু ও চলিত ভাষা, আঞ্চলিক ও উপভাষা, লেখ্য ও কথ্য ভাষা ইত্যাদি পাওয়া যায়, তেমনি ভাষারও সাম্প্রদায়িকতা আছে। আমরা ব্রিটিশ-আমেরিকান ভাষাভেদে যেমন ‘কালার’ শব্দে কখনও ‘ও’ আর ‘ইউ’-কে পাশাপাশি রাখি এবং কখনও ‘কালার’ হতে ‘ইউ’-কে বাদ দেই তেমনি বাংলা ভাষাতেও আমরা কখনো জলকে পানি বলি আর কখনো পানিকে জলই বলি। কিন্তু বাংলাভাষাতেই সহাবস্থান করে ‘জলপানি’ বলে একটা শব্দ আছে তা ভুলে যাই। যদিও জল বা পানি হতে ‘জলপানি’র অর্থ একটু দূরেই বলা যায়।
কবিদের কাছে কবিতা হলো ইশারা ভাষা। আড় বা ইশারা বজায় রেখে কবি কবিতায় তুলে ধরেন শিল্পের ব্যঞ্জনা। এ রকম ইশারা ভাষা ছিলো মধ্যযুগের কবিতায় যখন কবিরা বছর-সংখ্যা লুকিয়ে রাখতেন ভাষার মায়াজালে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,
‘কৃষ্ণ রাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল
বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র শকের বছর।’
এই উদাহরণে বসু হলো এক, ঋতু হলো ছয়, চন্দ্র হলো এক। অর্থাৎ এক হাজার একষট্টি শকাব্দ বুঝাতে এই আড় ভাষার সাহায্য নিয়েছেন কবি। এই ইশারা ভাষায় পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে রাখাই ছিলো কবির উদ্দেশ্য। আগেকার দিনে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে নারীরা অনাকাঙ্ক্ষিত তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের মধ্যে ভাবের বিনিময় সেরে নিতে ল-কথা বা ট-কথা জাতীয় ভাষার আশ্রয় নিতো। এখনও কোথাও কোথাও তা প্রচলিত আছে। এই কৌশলে প্রতিটা শব্দের আগে বা পরে বা মাঝখানে একটা ‘ল’ বা ‘ট’ অনুপ্রবেশ করানো হয়। যে বুঝার সে ঠিকই বুঝে নেয়। সামরিক বাহিনীতেও সাংকেতিক ভাষার প্রচলন দেখা যায়। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ কালরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পশ্চিমা হানাদার বাহিনী আটক করার পর ওয়্যারলেসে বলেছিলো, ‘দ্য বিগ বার্ড ইজ ইন দ্য কেইজ।’ বলা বাহুল্য এই সাংকেতিক ভাষায় তারা সেদিন কী বুঝাতে চেয়েছিলো তা আজ আর কারুরই অজানা নয়। টেলিগ্রাফের মোর্স কোড বলি কিংবা শর্টহ্যান্ডের ভাষা বলি, এসব কিছুই একধরনের সাংকেতিক ভাষা। ঠিক তেমনি কম্পিউটারের বাইনারি ভাষাও এক ধরনের সাংকেতিক ভাষা।
ভাষা নিয়ে অনেক প্রবাদণ্ডপ্রবচন ও বাগধারা প্রচলিত আছে। এ কথা সবাই জানে, এক দেশের বুলি অন্য দেশের গালি। আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে ঠাট্টা করতে গিয়ে অনেককেই বলতে শোনা যায়, বাংলা ভাষা আহত হয়েছে সিলেটে আর নিহত হয়েছে চট্টগ্রামে। বাগধারায় আছে, যে মুখের ভাষায় বোঝে না তাকে লাঠির ভাষায় বুঝাতে হয়। অর্থাৎ কাউকে মুখে বুঝিয়ে না হলে তাকে মেরে বুঝাতে হয়। প্রবাদে বলে, মুখের ভাষায় জয় মুখের ভাষায় ক্ষয়। এ নিয়ে একটা গল্পও প্রচলিত আছে। একজন ঘন ঘন ফেল করা ছাত্রকে শিক্ষক পরামর্শ দিলেন, ভালো করতে হলে ক্লাসে প্রথম হওয়া ছাত্রকে অনুকরণ করো এবং তার চেয়ে ভালো করো। একদিন ক্লাসে প্রথম হওয়া ছাত্র এবং ফেল করা ছাত্র দুজনেই গ্রামে বেড়াতে গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পিপাসার্ত হলো। ফার্স্ট বয় একজন গ্রামীণ কূলবধূকে কলসী কাঁখে দেখতে পেয়ে বললো : মা, আমার বড়ো তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল দেবেন? তার কথায় তুষ্ট হয়ে ঐ নারী তাকে জল পান করালেন। এটা দেখে ফেল করা ছেলে ভাবলো, আমার তো তার থেকেও ভালো করতে হবে। অতএব, সে গিয়ে মা-এর স্থলে বললো, হে আমার বাবার স্ত্রী, আমার পিপাসা পেয়েছে, আমাকে একটু জল দেবেন? কথা শুনেই জল কাঁখে মহিলা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার মাথার ওপর জলের কলস ভেঙ্গে রাগ প্রশমিত করলেন। অর্থাৎ মুখের ভাষার ব্যবহারে মানুষের মন যেমন জয় করা সহজ হয়ে যায়, তেমনি মুখের ভাষার অপপ্রয়োগে এর উল্টোটাই ঘটে। আবার ভাষার প্রক্ষেপণের ধরণও আমাদের অনেক কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। একবার আমি নিজেই পশ্চিমবঙ্গে বারাসাতে কোনো এক ক্লিনিকে ডাক্তারের ডিউটিরুমে বসে আছি। এমন সময় কানে শুনলাম, একটা নারীকণ্ঠ সুমিষ্ট স্বরে বলছে, ‘দিদিমণি গো, আপনার পেচ্ছাপের বেগ হয়েছে? হলে বলবেন, আপনার ইউএসজি করাতে হবে। এমন সুভাষিণী ও সুললিত কণ্ঠ শুনে আমি উদগ্রীব হয়ে বসে রইলাম জানতে এবং দেখতে, নারীটি কে। কিছুক্ষণ পরে ঐ নারী কণ্ঠের অধিকারিণী আমার ডিউটিরুমে এসে বললো, স্যার, আপনার রুমটা ঝাড়ু দেবো কি? বুঝলাম, তিনি আসলে সুইপার। সেদিনের সেই ঘটনা আমাকে কানে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলো, স্বাস্থ্যসেবায় পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকার একটা বড় কারণ হলো মুখের ভাষা প্রক্ষেপণের কৌশল ও ধরণে ব্যবধান। তাদের ভাষা প্রক্ষেপণে যে কোমলতা আছে তা শ্রোতার শ্রবণকে জয় করে নেয়। বহুভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর পুত্র চিত্রশিল্পী মুর্তাজা বশিরের একটা উপ-সম্পাদকীয় লেখার কথা মনে আছে। তাতে তিনি বলেছিলেন, একজন বিতার্কিক মাত্র কিছুক্ষণ আগে প্রমিত ভাষায় বিতর্ক করে শ্রেষ্ঠ বক্তা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বাসায় এসে সেই আনন্দের বর্ণনা মায়ের কাছে করতে গিয়ে আঞ্চলিক এবং আটপৌরে ঘরের ভাষায় তার সে কী উচ্ছ্বাস! তার মানে দাঁড়ালো আবেগকালীন ভাষাই হলো ব্যক্তির প্রকৃত ভাষা। একজন ব্রাহ্মণের আসল দেশ কোথায় তা জানতে না পেরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিদূষক গোপাল ভাঁড় একবার তাকে আড়াল থেকে মারলো ল্যাং। তাতে ঐ ব্রাহ্মণ হোঁচট খেয়ে ডিগবাজী মেরে পড়ে গেলো এবং ব্যথা পেলো। এতে কঁকিয়ে উঠে সে মাকে ডাকলো। অমনি আড়াল থেকে গোপাল ভাঁড় বের হয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বললো, মহারাজ, এই বামুনটা উড়ে। অর্থাৎ উড়িয়া। আসলে দুঃখ-কষ্টের ভাষা হলো অকৃত্রিম। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়ক উত্তম কুমারের ঠোঁটে কোনো এক ছবিতে আমরা একটা গানে শুনতে পেলাম,
‘পাখিদের ভাষা কাকলি
ভ্রমরের ভাষা গুঞ্জন
বিধাতার ভাষা সঙ্গীত
তারই সুরে কথা বলে মন।’
আসলে কান পাতলে প্রকৃতির ভাষা শোনা যায়। যারা সঙ্গীতকার, তারা বলেন, সঙ্গীত হলো ঈশ্বরের ভাষা। অনেকেই ঈশ্বরের সাথে কথা বলার ভাষাকে আবার ‘মৌন’ থাকার সাথে তুলনা করেছেন। সন্ধ্যার গোধূলি-শোভায়, অস্তগামী সূরের লালিমা যখন আকাশকে আবিরে রাঙিয়ে তৈরি করে দৃষ্টির অভিনব ইন্দ্রজাল, পাখিরা কুলায় ফিরে, তখন মৌন ভাষায় ডাকতে হয় ঈশ্বরকে। ঈশ্বর তখন তাঁর সৃষ্টির সাথে মেতে উঠেন আলাপনে। এ কথার পাশাপাশি একটুখানি বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’-র কথা উল্লেখ করতে হয়। বঙ্গবন্ধু খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তী (রঃ) তথা খাজা বাবার দরবারে গিয়ে কাওয়ালদের কণ্ঠে গান শোনেন। তিনি তাদের ভাষা না বুঝলেও তাদের কাওয়ালীর ভক্তিমূলক সুর তাঁকে ছুঁয়ে যায়। তিনি পকেটে পয়সার ঘাটতি থাকলেও সেই সংকট থেকে এক টাকা তাদের বখশিশ দিয়ে আসেন। তার মানে হলো, সঙ্গীতের ভাষাটা বিশেষ রকমের। তা অবুঝ শিশুকে যেমন টানে, তেমনি টানে চেতনাহীন মানুষকেও। গানে গানে আরেকটা ভাষার কথাও আমরা শুনি। আমরা বলি, ‘চোখ যে মনের কথা বলে’। যার চোখ এরকম বাক্সময় তিনি তো আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী সুবর্ণা মুস্তফা। ‘নয়নের আলো’ ছবিতে তাঁর অভিনয়ে চোখ যে কী অসাধারণ কথা বলেছে! তাঁর চোখের ভাষা হাজার কথার শামিল। ছোটবেলায় ক্লাস টু-তে পড়ার সময় একটা গল্প পড়েছিলাম, ‘গ্রেফায়ার্স ববি।’ এই গল্পে পালনকর্তা মালিক গ্রেফায়ারের মৃত্যুর পর তার পালিত কুকুর ববি কিছুই খায় না। কান্নাভেজা চোখে চেয়ে থাকে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে। সেই চোখের ভাষা পড়ে নিয়ে লেখক বলেছে, কুকুরটি তার দুচোখে যেন বলতে চেয়েছে, ‘প্লিজ গিভ মি মাই বান।’ অর্থাৎ, ‘অনুগ্রহ করে আমাকে আমার বনরুটিটি দাও।’ যারা ছবি আঁকে তাদের ভাষা আরও প্রগাঢ়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের দুর্ভিক্ষের ছবির ভাষা কাউকে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিতে হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, ঠাকুরবাড়ির ছেলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ছবির ভাষার মুখরতা বুঝাতে বোদ্ধারা বলতেন, ‘অবনঠাকুর ছবি আঁকে না, ছবি লেখে।’
তেমনি যারা চলচ্চিত্র বানান তাদেরও সিনেম্যাটোগ্রাফির ভাষা অসাধারণ। ‘পথের পাঁচালী’ ছবিতে সত্যজিৎ রায় ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু বুঝাতে দাওয়া থেকে কাঁসার ঘটি ও জল গড়িয়ে পড়ার যে ভাষা তৈরি করেছেন তাতে ঐ অশীতিপর নারী ‘হরি দিন যে গেল সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে’ বলে যে দুঃখানুভূতি দর্শকের মনে তৈরি করেছিলেন, তার চেয়েও তা মর্মস্পর্শী হয়ে শোনা যায়। একই রকমের ভাষার নান্দনিকতা বুঝা যায় সত্যজিৎ রায়ের ‘আগন্তুক’ চলচ্চিত্রে। না দেখা ছোটমামা আসবেন শুনে ভাগ্নী পিঠে বানায়। এক মনে সংশয়, আদৌ এটাই তার ছোটমামা কি না, নাকি সম্পত্তির লোভে ছুটে আসা কোনো দুর্বৃত্ত। কিন্তু আরেক মনে তৈরি হয় ভালোবাসা। তাই ভাগ্নী পিঠে বানায় হৃদয় আকৃতির ছাঁচ দিয়ে। এই যে দোনোমনার ভাষা, তা হাজার কথা লিখলেও এতো বাক্সময় হয়ে ফুটে উঠতো না।
এতোসব ভাষার পাশাপাশি পেশাজীবীদের ভাষাকেও অনেকে টেনে আনেন আলোচনায়। সচিবের ভাষার ধরণ এক রকমের। তারা নাকি কাজ করেন বাস্তবে কম, কিন্তু তাদের ভাষার কারণে কাগজে-কলমে কাজকে বেশি মনে হয়। যে কোনো কিছুকেই তারা ‘নথিতে দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দেওয়া গেলো’ বলে যে ভাষার ব্যবহার করেন, তাতে যেখানে নদীই নাই সেখানে পরের সভায় সেতু নির্মাণও সম্পন্ন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ডাক্তারেরা ইঞ্জেকশনের ভাষায় রোগের সাথে কথা বললেও বেড সাইড টিকেটে তা লিপিবদ্ধ না করায় অলসরূপে প্রতিপন্ন হন।
সবাই কারো না কারো কাছে ভাষা শিক্ষা করলেও নিজের আকাঙ্ক্ষার সাথে না মিললে আমরা বলে উঠি, শেখানো বুলি বন্ধ করো। কিংবা বলি, পাখির মতো শেখানো বুলি কপচিয়ো না। আবার কাউকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে কথা বলতে শুনলেও আমরা বলি কেতাবি ভাষা বন্ধ কর। ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রবহমান নদীর সাথেই তুলনা করেছেন। নদীর যেমন স্থবিরতা নেই তেমনি ভাষাও স্থির নেই। ভাষা নতুন কিছুকে সর্বদাই আত্মীকরণ করে। ত্রিশের পঞ্চপা-বখ্যাত কবিরা কবিতায় আধুনিকতা আনয়নে ভাষার কিছু ডালপালা ছেঁটেছিলেন। তারা আধুনিক কবিতায় পানে, তরে, যবে ইত্যাদি শব্দগুলোকে অপাংক্তেয় ঘোষণা করেছিলেন। আবার প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে আজ আমরা ভাষার অংশ হিসেবে পেয়ে গেছি এআই, সেল্ফি, ডিলিট, আপলোড এই জাতীয় শব্দকে। করোনা অতিমারি এসে আমাদের দিয়ে গেছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স, আইসোলেশন, পিপিই এই শব্দগুলোকে নতুন করে। ভাষায় নতুন শব্দ সৃজন ও সংযোজনের দিক থেকে বলা যায় ফরাসী ভাষা আছে এগিয়ে। এই ভাষায় প্রতি বছর কুড়ি হাজার নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়।
যারা বধির এবং যারা শুনতে পায়, এই দুই ধরনের মানুষ যখন নিজেদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন করে তখন তারা একধরনের ভাষার আশ্রয় নেয়। এ রকম একটি সাংকেতিক ভাষার নাম ‘উরুবু সাংকেতিক ভাষা’ বা ‘উরুবু-কা'পর সাংকেতিক ভাষা'। এটি একটি গ্রামের সাংকেতিক ভাষা। এটি ব্যবহৃত হয়েছিল ব্রাজিলের মারানহো গ্রামের ‘কা’পর’ নামক ক্ষুদ্র সম্প্রদায় দ্বারা। ভাষাবিদ জিম কাকুমাসু ঊনিশ্শো আটষট্টি সালে লক্ষ্য করেন যে, এই সম্প্রদায়ে প্রতি পাঁচশ জনের মধ্যে প্রায় সাত জন বধির। বধিরতার তুলনামূলকভাবে এই উচ্চহার কা'পর সম্প্রদায়ের শ্রবণক্ষমতাসম্পন্ন ও বধির এই উভয় শ্রেণির মানুষকে ভাষা ব্যবহার করার দিকে পরিচালিত করে এবং বেশিরভাগ শ্রবণক্ষম শিশুরা কথ্য ও সাংকেতিক ভাষা শিখে দ্বিভাষিক হয়ে বেড়ে ওঠে। আবার স্পেনের উপকূলে একদল মানুষ আছে যারা ‘লা গোমেরা’ নামের ভাষায় ভাব প্রকাশ করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই ভাষাভাষীরা শিস্ বাজিয়েই কথা বলে। জমজরা বুঝতে পারে এরকম একটা ভাষার নাম ‘ক্রিপ্টোফ্যাশিয়া’। এটা কেবল ভাষাই নয়, বরং এটা অনেকটাই অভিব্যক্তি নির্ভর। এই ভাষা দুই জমজ নিজেরা ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। জুন এবং জেনিফার নামে ওয়েলসের দু জমজ বোন এধরনের ভাষায় কথা বলতো। ক্রিপ্টফ্যাশিয়ার পাশাপাশি ইডিয়োগ্লসিয়া নামেরও একটা ভাষারীতি আছে। তবে এটা একক ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং বোধগম্য নয়। মাঝে মাঝে ক্রিপ্টোফ্যাশিয়া এবং ইডিয়োগ্লসিয়ার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায়। (চলবে)