প্রকাশ : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩৫
ই-বর্জ্য থেকে আয় ও কর্মসংস্থান
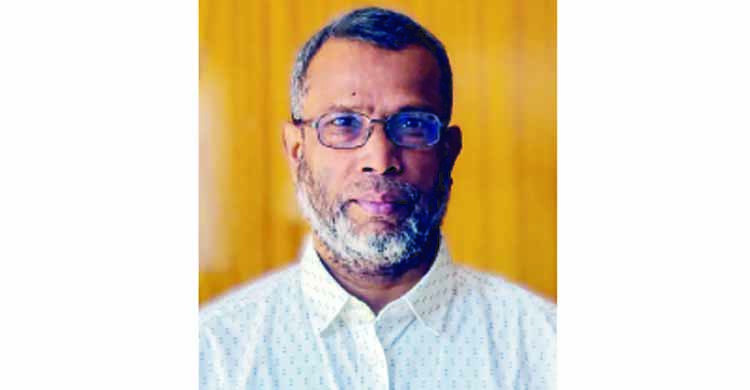
ইলেকট্রনিক বর্জ্য বা ই-বর্জ্য বলতে পরিত্যক্ত বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম বা অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বোঝায়। এগুলো মূলত ভোক্তার বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। যেমন ফ্রিজ, ক্যামেরা, মাইক্রোওয়েভ, কাপড় ধোয়ার ও শুকানোর যন্ত্র, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। কম্পিউটারের সিপিইউ’র মতো কিছু কিছু ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশে সীসা, ক্যাডমিয়াম, বেরিলিয়াম, ক্রোমিয়াম, ইত্যাদির মতো ক্ষতিকর পদার্থ থাকে। এর ফলে ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জড়িত শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি অনেক বেশি এবং এগুলোর নিয়মনীতিহীন ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ থেকে সামগ্রিক মানবস্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। দূষিত হতে পারে পরিবেশ। ডিসপ্লে ইউনিট (CRT, LCD, LED মনিটর), প্রসেসর (CPU, GPU, অথবা APU চিপস), মেমোরি (DRAM অথবা SRAM) এবং অডিও উপাদানগুলো বিভিন্ন কার্যকরী জীবনকাল থাকে। প্রসেসরগুলো প্রায়শই পুরানো হয়ে যায় এবং ‘ই-বর্জ্য’ হিসেবে পরিণত হয়। প্রতি বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩০ মিলিয়ন কম্পিউটার এবং ইউরোপ ১০০ মিলিয়ন ফোন ফেলে দেয়। এভাবে প্রতি বছর আনুমানিক ৫০ মিলিয়ন টন ই-বর্জ্য উৎপাদিত হয়। পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার অনুমান অনুসারে মাত্র ১৫-২০% ই-বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করা হয়। বাকি ইলেকট্রনিক্স সরাসরি ল্যান্ডফিল এবং ইনসিনারেটরে যায়।
বৈশ্বিক ‘ই-ওয়েস্ট মনিটর রিপোর্ট ২০২৪’ অনুযায়ী বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ ই-বর্জ্য উৎপাদনকারী দেশ। বাংলাদেশে গত ২০-২২ বছরে মোবাইল ফোন থেকে ১০ হাজার ৫০৪ টন বিষাক্ত ইলেকট্রনিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়েছে। এভাবে দেশে প্রতিবছর ৩০ লাখ টন ই-বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। যার মধ্যে অব্যবহৃত মুঠোফোন থেকেই তৈরি হচ্ছে প্রায় ১১ লাখ টন। আর পুরানো টেলিভিশন থেকে তৈরি হচ্ছে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার ম্যাট্রিক টন ই-বর্জ্য। অর্থাৎ প্রতি বছর ই-বর্জ্যরে পরিমাণ ৩০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই হিসাবে চলতি বছরের শেষ নাগাদ কোটি টনের ই-বর্জ্যরে ভাগাড়ে পরিণত হবে বাংলাদেশ।
অথচ অনেক ইলেকট্রনিক পণ্যের মধ্যে এমন উপাদান রয়েছে যেগুলোতে মূল্যবান সম্পদ রয়েছে, যার মধ্যে কিছু বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়। ই-পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রক্রিয়ায় এই ই-বর্জ্য থেকে সম্ভাব্য বিপজ্জনক ও বিষাক্ত পদার্থ অপসারণের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণে রূপান্তর করা যায়। যা দূষকগুলোকে ল্যান্ডফিলগুলোতে শেষ হতে এবং পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে বাধা দেয়।
দ্রুত উদীয়মান অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও। শহর-গ্রাম সর্বত্র ইলেকট্রনিক পণ্যের ব্যবহার বেড়েছে। দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা ১৯ কোটি ৩৬ লাখ। একটি মোবাইল সেটের ব্যবহার উপযোগিতা শেষ হওয়ার আগে এর মেয়াদকাল দুই থেকে তিন বছর ধরলেও কয়েক কোটি মোবাইল সেট প্রতি বছর যুক্ত হচ্ছে দেশের ই-বর্জ্যরে ভান্ডারে। এর সঙ্গে পুরানো ও নষ্ট হয়ে যাওয়া কম্পিউটার, টিভি, ফ্রিজ, এসি, মাইক্রোওয়েভসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী তো আছেই।
৭৩ শতাংশ মোবাইল মেরামতকারী পুরানো ও নষ্ট মোবাইল সেট স্টোর রুমে ফেলে রাখেন। আর ৪০ শতাংশ মোবাইল ব্যবহারকারীরা বাসা থেকে শুরু করে যত্রতত্র নষ্ট মোবাইল ফোন ফেলে রাখেন। এভাবে দেশে প্রতি বছর লাখ লাখ সেলফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, এয়ারকন্ডিশনার, ফটোকপি মেশিনসহ ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম অকেজো হয়ে যায়। আর এগুলোর স্থান হয় অন্যান্য গৃহস্থালি ময়লা-আবর্জনার সঙ্গে আস্তাকুঁড়ে বা ডাস্টবিনে। ফলে দিনে দিনে ইলেকট্রনিক বর্জ্যরে একটি বিশাল বাগারে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ। পরিসংখ্যান মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে ই-বর্জ্যরে বার্ষিক এই পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১৬ লাখ টন। অথচ এই অবস্থান থেকে পরিত্রাণের জন্য এখন পর্যন্ত তেমন কোনো ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ রিসাইকেলিং সিস্টেম গড়ে ওঠেনি বাংলাদেশে।
বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট, প্রযুক্তি ও ইলেকট্রিক-ইলেকট্রনিকস পণ্যের ব্যবহার এখন মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িত। ধারণা করা হয়, দেশের টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ও ইলেকট্রিক-ইলেকট্রনিকস পণ্যের বাজার প্রায় ৭০ থেকে ৮০ হাজার কোটি টাকার। এসব ইলেকট্রনিকস ডিভাইসে থাকে ক্ষতিকর ভারী ধাতু। এগুলোর রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে ক্যানসার, শ্বাসকষ্ট, শ্রবণ সমস্যা, শিশু মৃত্যু, জন্মগত সমস্যা, অর্থাৎ প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নেওয়ার প্রবণতাও তৈরি হয়। পাশাপাশি পরিবেশ, পানি ও বায়ু দূষণের কারণে জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে বন্যপ্রাণী ও জলজ প্রাণী ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ছে।
এসব বর্জ্য সংগ্রহ ও রিসাইক্লিং কাজে নিয়োজিত আছে ৫০ হাজারের বেশি শিশু-কিশোর। এগুলোর দূষণের কারণে প্রতি বছর মারা যাচ্ছে ১৫ শতাংশ শিশু। আর ৮৩ শতাংশের বেশি শিশু বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে এসে অসুস্থ হচ্ছে। অনুমান করা হচ্ছে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ বছরে ১০০ কোটি মুঠোফোন উৎপাদন হবে এবং কম্পিউটারের পিসিবিভিত্তিক ধাতু পুনরুদ্ধার ব্যবসা সম্প্রসারিত হবে, যা ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ মানবিক সংকট। ই-বর্জ্য স্বাস্থ্য ঝুঁকির পাশাপাশি পরিবেশের ওপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে। যথাযথ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায় দূষিত করছে পানি, বায়ু ও মাটি। বাড়াচ্ছে পরিবেশের তাপমাত্রা এবং বিনষ্ট করছে জমির উর্বরতাও।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সঠিকভাবে ই-বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবেশসম্মত উপায়ে রি-সাইকেল করতে পারলে তা সম্পদে রূপান্তর সম্ভব হবে। ঠিককমতো একটি মোবাইল ফোন রিসাইকেল করা গেলে এ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব। তাহলে অন্যান্য ই-বর্জ্য থেকে কি পরিমাণ আয় করা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। রাজস্বের ভিত্তিতে ভিওলিয়া বিশ্বের বৃহত্তম বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানি। জল, বর্জ্য এবং শক্তি ব্যবস্থাপনা পরিষেবা প্রদানকারী ফরাসি কোম্পানিটি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে শেষ হওয়া আর্থিক বছরে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি আয় করেছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানিগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। যার মধ্যে বৃহত্তম হলো ‘ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইনকর্পোরেটেড’, টেক্সাসের হিউস্টনে। ২০২৩ সালে তাদের আয় হয়েছে ২০.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
তবে আশার বিষয়, বাংলাদেশেও (গাজীপুর) ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যা ২০২৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া, সরকারের পরিবেশ উন্নয়ন সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন (বেস্ট) এর অধীনে ‘ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট’ প্রকল্পের কাজ চলমান আছে, যা বাস্তবায়ন করছে পরিবেশ মন্ত্রণালয়।
জাতিসংঘের হিসাব মতে, বিশ্বে প্রতি বছর ৪ কোটি টনেরও বেশি ইলেকট্রনিক বর্জ্য উৎপাদিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণচীন– এই দুটি দেশ সারা বিশ্বের ই-বর্জ্যরে এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে। এসব ই-বর্জ্যে অনেক অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ধাতু ও অন্যান্য উপাদান আছে, যেগুলো পুনঃচক্রায়ন করা সম্ভব। লোহা, তামা, সোনা, রূপা, অ্যালুমিনিয়াম, প্যালাডিয়াম ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য অন্যান্য উপাদানগুলোর মোট মূল্য ৫২০০ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি। ২০২৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫৬ মিলিয়ন টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার মাত্র ১৭.৪% আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রহ এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়। এগুলোর অনুমান মূল্য প্রায় ৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
বাকি অংশ প্রায়শই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হয়, যা গুরুতর স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি করছে। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন, মিডিয়ার পরিবর্তন (টেপ, সফটওয়্যার, গচ৩), দামের পতন এবং পরিকল্পিত প্রক্রিয়াকরণের অভাবে বিশ্বজুড়ে ইলেকট্রনিক বর্জ্যরে দ্রুত বর্ধনশীল উদ্বৃত্ত দেখা দিচ্ছে। কিন্তু পরিত্রাণের জন্য রিসাইক্লিং প্রযুক্তি আছে খুবই সীমিত। চীনে ই-বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া বেশ জনপ্রিয়। সেখানে ই-বর্জ্যকে অন্য বর্জ্যরে সঙ্গে মিশিয়ে বা সরাসরি পুড়িয়ে তাপ উৎপন্ন করা হয়, যা বাষ্প তৈরি করে টারবাইন ঘোরায় এবং বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে।
এই কর্মযজ্ঞের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু লোকের কর্মসংস্থান। ই-বর্জ্য সংগ্রহ, বাছাই, ভাঙা ও পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়াকরণে দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীদের কর্মসংস্থান তৈরি করে। বাংলাদেশেও ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নীতি প্রণয়ন করছে এবং গাজীপুরে একটি জাতীয় ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
লেখক : অধ্যাপক ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, আইআইটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।








