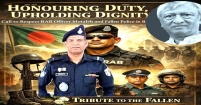প্রকাশ : ১৭ মে ২০২৩, ০০:০০

তছলিম হোসেন হাওলাদার মূলত কবি ও গল্পকার। প্রবন্ধ-নিবন্ধও লিখছেন তিন দশক ধরে। ১৯৭৪ সালে কবিতা লেখার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চায় হাতেখড়ি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘কখনও শাশ্বত’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। এরপর একে একে প্রকাশিত ৬টি গ্রন্থ। এর মধ্যে উপন্যাস ‘স্মৃতির অন্তরালে’ (২০১৪), প্রবন্ধগ্রন্থ ‘মাঠের যোদ্ধা চাই’ (২০১৮), গল্পগ্রন্থ ‘কহর দরিয়ার পানি’ (২০২০) উল্লেখযোগ্য। তিনি বিভিন্ন সময়ে ছোটকাগজ ‘পালক’, ‘সম্প্রীতি’ ও ‘অনপেক্ষ’ সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া চাঁদপুরের সাহিত্যের নবপর্যায়ের প্রথম ছোটকাগজ ‘মৃত্তিকা’র অন্যতম সম্পাদক। তছলিম হোসেন হোসেন হাওলাদার বিভিন্ন সামাজিক ও সাহিত্য সংগঠনে যুক্ত আছেন। বর্তমানে তিনি চাঁদপুর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার সাহিত্যচর্চা ও সংস্কৃতি-চিন্তা নিয়ে ২০২১ সালের জুন মাসে তার সাথে কথা বলেন মুহাম্মদ ফরিদ হাসান। সাক্ষাৎকারটি ২০২১ সালের ৯ জুলাই যুগান্তরে প্রকাশিত হয়।
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান : আপনার সাহিত্যচর্চার সূচনালগ্নের কথা জানতে চাই।
তছলিম হোসেন হাওলাদার : আমার সাহিত্যচর্চার পেছনে কারও অনুপ্রেরণা ছিল না। নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহে কৈশোর থেকে লেখালেখি করি। প্রথমদিকের চর্চা ছিল টুকটাক ও অগোছালো। ১৯৭৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি আমার মা মারা যান। তার মৃত্যুর শোক আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তার মৃত্যুর দুঃখবোধ থেকে আমি প্রথম সচেতনভাবে কবিতা লিখি। মনে আছে, মায়ের স্মৃতির প্রতি নিবেদিত করে পরপর ৪টি কবিতা লিখেছিলাম। সে কবিতাগুলো বাঁধাই করে ঘরে টানিয়ে রেখেছিলাম অনেকদিন। কবিতাগুলো দেখলেই আমার মায়ের কথা মনে পড়ত। আমার প্রথম কবিতা ‘স্বাগতিক শব্দমালা’ ছাপা হয় ১৯৭৯ সালে, মৌলভীবাজারের ‘বর্ণালি’ সাহিত্য-সাময়িকীতে।
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান : কেন লিখেন?
তছলিম হোসেন হাওলাদার : জীবন ও জগৎকে প্রতিনিয়ত দেখছি, আলোড়িত হচ্ছি। সেই দেখা ও অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে ‘লেখালেখি’।
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান : মফস্বলে থেকে সাহিত্যচর্চার সুবিধা-অসুবিধা কী?
তছলিম হোসেন হাওলাদার : মফস্বলে থেকে পূর্বে সাহিত্যচর্চা করার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা ছিল। বর্তমানে কোনো অসুবিধা নেই। প্রযুক্তির এ সময়ে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে মফস্বল ও রাজধানীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রযুক্তিই মফস্বল-রাজধানীর দূরত্ব ঘুছিয়েছে। এখন অজগাঁয়ে বসেও ই-মেইল করে দেশে-বিদেশে লেখা পাঠানো যায়। সে লেখা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সারা দেশের লেখকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা সম্ভব। ফলে স্থানের দূরত্ব এখন নেই। অনেকে মফস্বলে থেকে লিখেন বলে হীনমন্যতায় ভোগেন; যা উচিত নয়। সাহিত্যচর্চার জন্য নিরলস পঠন-পাঠন ও চর্চা প্রয়োজন। চর্চার মধ্যে থাকলে সাফল্য আসবেই। শহরের চেয়ে বরং এখন মফস্বলে থেকে লেখালেখি করার সুবিধা বেশি। প্রকৃতির কাছে থেকে, প্রান্তিক জনজীবনকে দেখে সাহিত্যচর্চা করা যায়। শহরের নাগরিক যাপনে অস্থিরতা আছে, যা সাহিত্যচর্চার জন্য অন্তরায় বলে মনে করি। আগে মফস্বলে ভালো বই পাওয়া যেত না। এখন রকমারি বই বাজারের মতো প্রতিষ্ঠানের কারণে গ্রামে বসেই প্রয়োজনীয় বই পাওয়া যায়।
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান : লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকামুখী হওয়াকে কীভাবে দেখেন?
তছলিম হোসেন হাওলাদার : লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকামুখী হতেই হবে- এমনটা একসময় লেখকরা মনে করতেন। জীবনানন্দ দাশ, আল মাহমুদরা তা-ই ভেবেছেন ও করেছেন। এখনকার সমাজ বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকামুখী হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যেমন- যতীন সরকার, হাসান আজিজুল হক, জাকির তালুকদাররা মফস্বলে আছেন। তা সত্ত্বেও তাদের প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তি বা লেখালেখির কোনো সমস্যা হয়েছে বলে শুনিনি।
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান : কোন কোন বিষয়কে আপনি সচেতনভাবে লেখার অনুষঙ্গ হিসাবে নেন?
তছলিম হোসেন হাওলাদার : আমার পারিপার্শ্বিক আবহের মধ্যে যেসব বিষয় আমার মনে দাগ কাটে, সেসব বিষয় আমার লেখায় উঠে আসে। সামাজিক-রাজনৈতিক অভিঘাত, উল্লেখযোগ্য ঘটনা, প্রতিক্রিয়া, অন্ত্যজ শ্রেণির যাপনকে আমি সচেতনভাবে লেখায় উপস্থাপন করি।
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান : একজন লেখক কি সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারেন?
তছলিম হোসেন হাওলাদার : হ্যাঁ, পারেন। বিশেষত, মানুষের মন ও মননের বিকাশে, চিন্তার পরিবর্তনে সাহিত্যিকরা ভূমিকা রাখেন। যেমন- বেগম রোকেয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারে যে ভূমিকা রেখেছেন, তাতে লেখালেখির ভূমিকাও রয়েছে। প্রত্যক্ষ আন্দোলন-সংগ্রামেও সাহিত্য হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে লেখকদের লেখা বহু গান, কবিতা, গদ্য মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। আর শেষ পর্যন্ত লেখা ও চিন্তাটাই টিকে থাকে। যেমন- দু’হাজার বছর আগের সক্রেটিস স্বমহিমায় এখনো টিকে আছেন।
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান : আপনার প্রিয় লেখক কারা? এ সময় কাদের লেখা ভালো লাগে?
তছলিম হোসেন হাওলাদার : আমি মুগ্ধ হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সৈয়দ শামসুল হক, কমলকুমার মজুমদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত আলী, মহাশ্বেতা দেবী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল হাসান, সৈয়দ আবুল মকসুদ, রফিক আজাদের লেখা পড়েছি। তাদের প্রত্যেকের লেখাই আমার ভালো লাগে। এ সময়ের লেখকদের মধ্যে আন্দালিব রাশদী, মোহিত কামাল, মাসউদুল হক, মাসউদ আহমাদের লেখা ভালো লাগে। একসময় প্রচুর পড়েছি। দিন-রাত এক করে পড়েছি। কিন্তু ইদানীং চোখের সমস্যার জন্য পড়া কম হচ্ছে।
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান : লেখক হিসাবে প্রত্যাশা বা প্রাপ্তি নিয়ে কখনো ভেবেছেন?
তছলিম হোসেন হাওলাদার : সত্যি কথা বলতে, আমি সার্বক্ষণিক লেখক ছিলাম না কখনো। লেখালেখি করতে যে শ্রম দেওয়া প্রয়োজন- তা-ও দিতে পারিনি। সাহিত্যচর্চায় চার দশকেরও বেশি সময় নিবেদিত থেকেছি ভালোবাসা থেকে। সবমিলিয়ে আমি প্রাপ্তির কথা ভাবিনি। তবু কিছু কিছু প্রাপ্তি আমার রয়েছে। অনেকেই আমাকে পুরস্কার-সম্মাননা দিয়েছেন; যা অবশ্যই আনন্দের। তবে, আমি যে সাহিত্যের মাধ্যমে আমার উপলব্ধিটুকু প্রকাশ করতে পারছি, এটাই আমার বড় প্রাপ্তি। আমি প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের ‘শাস্তি’ গল্পটির কথা ভাবি। আমি চিন্তা করি, আমার একটি গল্পই যদি মানুষের কাছে থেকে যায়, তা-ই হবে আমার জন্য বড় প্রাপ্তি।
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান : চাঁদপুরের বর্তমান সাহিত্যচর্চা নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?
তছলিম হোসেন হাওলাদার : বর্তমানে সাহিত্যচর্চায় চাঁদপুর খুবই ভালো অবস্থানে রয়েছে। বিশেষত, আমাদের একঝাঁক তরুণ নিয়মিত জাতীয় পত্রিকায় লিখছে। তাদের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানসম্মত বই প্রকাশিত হয়েছে। লিটলম্যাগও প্রকাশিত হয়েছে অনেক। এ লেখকরা বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কার-সম্মাননা পাচ্ছে। এ বিষয়গুলো আমাকে আশান্বিত করছে।