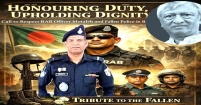প্রকাশ : ০১ মার্চ ২০২৩, ০০:০০

অন্য দেশের মূল্যস্ফীতির তুলনায় একটি দেশের মূল্যস্ফীতি বেশি হলে সে দেশের মুদ্রা তুলনামূলক শক্তি হারাবে। এটা অর্থনীতির একটি মৌলিক নিয়ম। আগে থেকেই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল, এখন ঘাটতি আরো বেড়ে গেল। এজন্যে হঠাৎ করে দ্রুত বড় ধরনের সমন্বয়ের প্রয়োজন হলো। ফলে আগে মুদ্রাবিনিময় হার সমন্বয় না করার একটি শাস্তি বাংলাদেশ পেল। আরেকটি শাস্তি হঠাৎ সৃষ্ট বৈশ্বিক সঙ্কটের শাস্তি। যার ফলে আমাদের টাকার অবমূল্যায়নটা দ্রুত করতে হয়েছে।
চাহিদার তুলনায় ডলারের জোগান কম হলেই ডলারের মূল্যমান বাড়বে (অর্থনীতির সূত্র তাই বলে)। আমাদের ডলার আয়ের বৈধ ক্ষেত্র হলো রেমিট্যান্স এবং রপ্তানি আয়। এ ক্ষেত্রে খুব বড় উত্থান-পতন দেখছি না। তবে সমস্যা কোথায়? ডলারের চাহিদার দিক থেকে সমস্যা হচ্ছে যার কারণ সবাই বলছে কিংবা জানে, আমাদের আমদানিকৃত পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত চাহিদা বাড়েনি, তবে ডলার ব্যয় বেড়ে গেছে। এর জন্য ডলারের চাহিদার ওপর প্রভাব পড়বে সত্য। কিন্তু শুধু এর জন্য ডলারের চাহিদা বেড়েছে বিষয়টি তা নয়। আমরা যেসব পণ্য রপ্তানি করছি তারও দাম বাড়ার কথা। তবে ধরে নেই অসম বিশ্ববাজারে এবং আমাদের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা কম থাকায় সেটি হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ট্রিগ্রিটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, রপ্তানিকারকরা আন্ডার ইনভয়েসিং করে রপ্তানি আয়ের অর্থটা বিদেশে রেখে দিয়েছে। আবার আমদানি পণ্যের দাম বেশি দেখিয়েও অর্থ বাইরে রেখে দেয়া হতে পারে। বলা হচ্ছে আমদানি পণ্যের দাম বেড়েছে, সেটি কোন্ কোন্ পণ্যে বেড়েছে। সব পণ্যেইতো সমান হারে বাড়েনি, বাড়ার কথা নয়। তাহলে কি বাড়তি ব্যয় দেখিয়ে ওভার ইনভয়েসিং করে অর্থ বিদেশে রেখে দেয়া হচ্ছে? এ সন্দেহটি আগে থেকেই ছিলো এবং বেশকিছু তদন্তে এটি ধরাও পড়েছে।
২০০০ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশের মানুষের আমানত ছিল ৪৯৩ কোটি টাকা। ২০২১ সালে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৮ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে এটি বেড়েছে। ২০২৩ সালের শেষের দিকে আমাদের আরেকটি জাতীয় নির্বাচন আছে। প্রশ্ন হলো, এ অর্থ কোথা থেকে গেল। কারা এটা কোথায় এতদিন ধরে জমিয়ে রেখেছিল? অনেকের ধারণা, শুধু প্রবাসী বাংলাদেশীরা উক্ত অর্থ জমা রাখেনি, দেশে অবস্থান করা বাংলাদেশীরাও আছেন। সরকার বলছে, সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের তথ্য চেয়েছি, কিন্তু পাচ্ছি না। তবে বিষয়টি নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। কেন কে টাকা পাঠাল? সরকার তো বলছে, কেউ যদি টাকা বিদেশে না পাঠিয়ে এখানে বিনিয়োগ করে তবে তাকে কম কর দিতে হবে। আরো নানা সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে। তারপরও কেন তারা টাকা বাইরে পাঠাচ্ছে? তার মানে এখানে টাকা রাখাটা তারা নিরাপদ বোধ করছে না। সাধারণ নির্বাচনের আগে আগে ধনী রাজনীতিবিদরা এখানে টাকা রাখাকে নিরাপদ মনে করেন না। কিন্তু কেন? কারণ হতে পারে, নিজেরা হেরে গেলে এবং বিপরীত দল ক্ষমতায় এলে ভয়ের আশঙ্কায় শাসক শ্রেণীই তাদের টাকা বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারে। নির্বাচনের আগে আগে সুইস ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ আমানত জমা হওয়ায় প্রশ্ন উদয় হওয়াটা স্বাভাবিক। ফলে চলতি বছরেও আমদানি ব্যয় বেশি হওয়া এবং সুইস ব্যাংকে টাকা বেশি জমা হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।
অর্থনৈতিক-রাজনীতির আর একটি চ্যালেঞ্জ হলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা। কীভাবে করবে সেটিই দেখার বিষয়। দুটি উপায়ে দেশের ভেতরে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একটি হলো, সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেয়া। বিশেষত কায়েমি স্বার্থকে ঘিরে যেসব সমস্যা তৈরি হয়েছে সেটি নিয়ন্ত্রণে তদারকি জোরদার এবং বাজারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা। ব্যবসায়ীদের অনেক ক্যারোট দেয়া হয়েছে। প্রণোদনা, স্বল্প সুদে ঋণ, শুল্ককর মওকুফ, ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ প্রভৃতি সুবিধা দেয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা এসব সুবিধা নিয়েও অতি মুনাফার লোভ ত্যাগ করতে পারেনি। তারা মজুদ করেছে এবং মাত্রাতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রি করছে। এতে বোঝা যাচ্ছে ক্যারোট পলিসি কাজ করছে না। তাই এখন স্টিক পলিসি গ্রহণ করা উচিত। তবে কোনো স্টিকের কথা প্রায় নেই, থাকলেও সুশাসনের অভাবে তা কার্যকর হয় না। বস্তুত সেনাশাসনের অনাকাঙ্ক্ষিত অধীনতায় ২০০৭ ও ২০০৮ সালের মতো আর স্বাভাবিক সময়ে কখনো হবে না বলেই মানুষের এক ধরনের বিশ্বাস জন্মে গেছে। এটা গণতন্ত্রের জন্য মোটেও শুভ নয়। অপরদিকে ব্যবসায়ীরা ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করতে পারছে না কেন? নিশ্চয়ই ঋণটি উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হয়নি। করা হলে তো মুনাফা আসার কথা। অনুৎপাদনশীল বিনিয়েগে মুনাফা আসবে না। মেগা প্রকল্পে যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তাতেও নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। অর্থ এখনই ব্যয় হয়ে যাবে, কিন্তু ফলাফল আসবে অনেক দেরিতে। ফলে অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির একটি চাপ তৈরি হবে। সরকার শুদ্ধাচারের আইন করেছে, কিন্তু অশুদ্ধাচার এরপরও ক্রমবর্ধমান।
বস্তুতঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকটের দৃশ্যপটে সরকারের কেউ এর সুবিধাভোগী কিনা তাও তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন। সংকটকে নানাভাবে দেখা যায়। একটি হলো সংকটের প্রকাশ আরেকটি হলো সংকটের গভীরতর কারণ। সংকটের মূল কারণগুলো দূর না হলে সংকটের কিছু উপশম নিরাময়ে প্রলেপ দিয়ে সমাধান হবে না। বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান সংকট বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের দেশের ক্ষমতাণ্ডকাঠামো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। বাংলাদেশের ক্ষমতা প্রশাসনের মধ্যে লুক্কায়িত, রাজনীতির মধ্যে পরিচালিত, অর্থনীতি ও ব্যবসার মধ্যে বিস্তৃত। ফুকোর তত্ত্ব অনুযায়ী এ তিনটি পর্যায়েই ক্ষমতা পরিচালিত হয় দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। এ জায়গায় যদি একটি পক্ষের জোট তৈরি হয়ে যায়-অসৎ-আমলা, অসৎ-অর্থনীতিবিদ ও অসৎ-রাজনীতিবিদ, তাহলে তারা একে অন্যকে সহায়তা করবে এবং একচেটিয়াতন্ত্র কিংবা কতিপয়তন্ত্রের উদ্ভব হবে। সেটা কী অর্থনীতি, কী রাজনীতি, কী ব্যবসা সর্বত্রই তা হয়ে থাকবে।
তখন তাদের শক্তি বিগপুশ ছাড়া ভাঙ্গা যায় না। যখন সরকার ওদের বিরুদ্ধে হালকা ব্যবস্থা নেয় তখন তারা চতুর্দিক থেকে একজোট হয়ে তা প্রতিহত করবে। ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে যেসব রাজনীতিবিদ তাদের কাছ থেকে অর্থ ও সুবিধা পায়, তারা পাশে এসে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। সরকার ব্যবস্থা নিতে চাইলেও পিছিয়ে যাবে। সরকার যদি ব্যবসায়ী ও জোটবদ্ধ বা নির্ভরশীল রাজনৈতিক অসৎ বা দুর্নীতিবাজ শক্তিকে যুক্তভাবে মোকাবেলা করার ব্যবস্থা নিতে চায়, তখন যদি প্রশাসনিক শক্তি আবার তার পক্ষে কাজ না করে অর্থাৎ অসৎ ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকদের রক্ষায় প্রশাসনও তাদেরই পক্ষে যায়, তাহলে স্টিক পলিসিও কাজ করবে না। কারণ যাদের দিয়ে কঠোর নীতি ও আইন প্রয়োগ করা হবে, তারাও যদি এ নেক্সাসে যুক্ত হয়ে পড়ে তাহলে কোনো কিছুই আর কাজ করবে না। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে সরে আসা শাসক-দলের ভিতরে ব্যাপারটি হয়েছেও তা-ই। রাজনৈতিক শক্তি, ব্যবসায়িক শক্তি ও প্রশাসনিক শক্তি এক হয়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম করছে। এখানে কোনো নীতিই আর কাজ করছে না। প্রশাসনকে মাঠ পর্যায়ে ঘুষ দিয়েই ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকরা কিনে নেবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তকারীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে অসৎ ও দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও আমলাদের দিয়ে কাজ না করে অপেক্ষাকৃত সৎ রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও আমলাদের দিয়ে কাজ করাতে হবে অর্থাৎ দায়িত্ব দিতে হবে। একে রাজনৈতিক ভাষায় আমরা বলি বিকল্প ক্ষমতা কাঠামো নির্মাণের ইস্যু।
অসৎ ও দুর্নীতিবাজ লোকগুলো অনেক শক্তিশালী হয়ে গেছে এবং এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে সৎ ব্যক্তিদের শাস্তি পেতে হয়। ফলে কেউ আর সাহস দেখাচ্ছে না। এখানে রাষ্ট্রের প্রণোদনা কাঠামো উল্টো হয়ে গেছে। দুষ্টের লালন আর শিষ্টের দমন। শুধু একটি গ্রুপ কখনোই শক্তিশালী হতে পারে না। তিনটি ফোর্স এক হয়েছে বলেই তাদের এত শক্তি। তবে সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকায় সেখানে বিরোধী কোনো আলোচনা হচ্ছে না বললেই চলে। তাছাড়া নির্বাচনটি হয়ে গেছে মানি, ম্যানিপুলেশন ও মাসলনির্ভর। এখানে সাধারণ জনগণের কোনো ভাষা প্রকাশের ক্ষমতা নেই। অসৎ-আমলা, অসৎ-রাজনীতিক ও অসৎ-ব্যবসায়ীরাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। এটি একটি দুষ্টচক্র। এখানে সরকার চাইলেও নির্বাচন তো ঠিকমত করা যাবে না। কারণ ব্যবসায়ীরা তাদের স্বার্থ রক্ষায় বিপুল অর্থ ব্যয় করে তাদের প্রার্থীকে জিতিয়ে নিয়ে আসবে। প্রথমত মনোনয়নই ভালো লোককে দিতে পারা যাবে না। সুতরাং প্রতিযোগিতা হবে খারাপ লোকদের মধ্যে। খারাপ লোকদের মধ্যে যাদের শক্তি বেশি হবে তারাই জিতে আসবে। না জিতলেও একটি খারাপ লোকের বদলে আরেকজন কম খারাপ লোক আসবে। ভালো লোক যদি সংসদে না আসতে পারে বা কম আসে তাহলে সংসদে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে না। এখানে সরকার প্রধানেরও সমস্যা তৈরি হতে পারে। কারণ তিনি জানেন তিনি সংসদ কিংবা দলের নেতাদেরকে খেপিয়ে ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না।
এরূপ অবস্থায় জনগণই পারবে পরিবর্তন আনতে। শ্রীলংকার উদাহরণ হয়তো হবে না, তবে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশও হয়েছিল কিন্তু, তা হয়েছিল দুর্নীতি, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে, কতিপয়তন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে। সমাজে ৫ থেকে ১০ শতাংশ চরম খারাপ এবং ৫ থেকে ১০ শতাংশ চরম ভালো। মাঝখানে যারা আছেন তাদের উপর নির্ভর করে ক্ষমতার ভারসাম্য কোন্ দিকে যাবে? এদেরকে বলা হয় পলিটিক্যাল ভ্যারিয়েবল ফোর্স। এরাই নির্ধারণ করে কারা ক্ষমতায় থাকবে। কিন্তু তারা দোদুল্যমান। একবার ভালোর দিকে, আবার খারাপের দিকে যায়। মানুষ ভালোর দিকে না যাওয়ার কারণ, অনেক ধরনের ভয় রয়েছে। এর মধ্যে খুন, মামলা, হামলা, হয়রানি ইত্যাদি। কিন্তু ইতিবাচক আশা ছাড়া আন্দোলন হয় না। কেউ কি এটি তৈরি করতে পেরেছে? যাদের এটি করার কথা তারাও ঠিকমতো করছেন না। ফলে মানুষ সেরকম নেতৃত্ব খুঁজে পাচ্ছে না। জনতার কাঙ্ক্ষিত সমাজ-রাষ্ট্রের রূপান্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী কিংবা প্রেসার গ্রুপ সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামাজিক বিপ্লবে এগিয়ে আসতে হবে।
লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক মোঃ হাছান আলী সিকদার, সভাপতি, চাঁদপুর জেলা জাসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা, চাঁদপুর জেলা শিক্ষক নেতা, সমাজ ও রাজনীতিবিশ্লেষক।