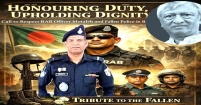প্রকাশ : ১৩ অক্টোবর ২০২২, ০০:০০
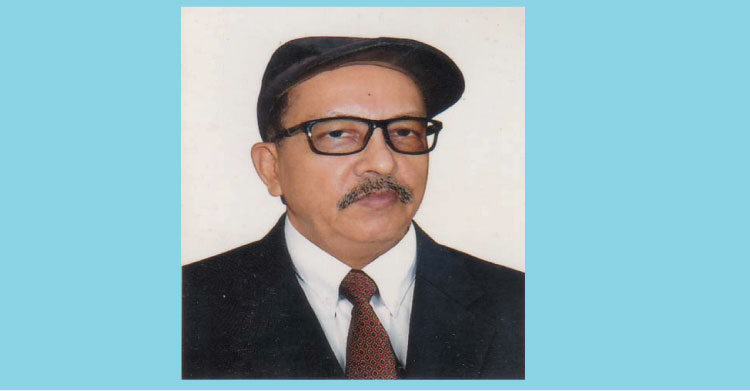
বৃটিশ ভারতীয় সরকার ভারতের কতকগুলো অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে (শ্রেণী-দ্বন্দ্ব, জাতিগত-দ্বন্দ্ব, ভাষাগত-দ্বন্দ্ব, আঞ্চলিক-দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক-দ্বন্দ্ব ইত্যাদি) নানাভাবে প্রভাবিত করার মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বহুভাগে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বটি সব ধরনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রবলতম হয়ে উঠে এবং এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার প্রশ্ন ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোত ও অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত হয়। এবং সে কারণেই ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বৃটিশ ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এই উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় দু’টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান।
বৃটিশবিরোধী এই স্বাধীনতা সংগ্রামে তৎকালীন ভারতের জনগণের সাধারণভাবে ছিল একটা স্বাধীনতার চেতনা এবং সেই সাধারণ চেতনার অর্থ ছিল বিদেশী শাসকদের শাসন থেকে মুক্তি লাভের চেতনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই স্বাধীনতার চেতনা কি বিশেষ অর্থে সকলের জন্য এক ছিলো?-না, তা ছিলো না। তা যদি থাকতো, তাহলে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বৃটিশ ভারতকে ভেঙ্গে দুটুুকরো করতো না। কিন্তু শুধু তা-ই নয়, সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে টাটা-বিড়লা-ইস্পাহানিদের চেতনা এবং ভারতীয় শ্রমিক-কৃষকদের চেতনা কি এক ছিলো?-না তা ছিলো না। সেই সংগ্রামে কি ভারতের সকল ছোট-বড় জাতি ও জাতিসত্তার চেতনা কি এক ছিলো?-না তাও না। স্বাধীনতা চেতনার মধ্যে এ ধরনের পার্থক্যের উদাহরণ দিতে চাইলে আরও দেয়া যায়, কিন্তু এ বিষয়টি মনে রাখা যে, বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতাযুদ্ধে যে ভারতীয় জনগণ অংশগ্রহণ করেছিল এবং অনেক আত্মত্যাগ করেছিলেন, তাদের সকলের চেতনা এক ছিলো না।
বর্তমান বাংলাদেশ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান এবং এখানে মুসলিম লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনকালে মুসলিম লীগের মূল রাজনৈতিক অবলম্বন ছিলো সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের একটা মীমাংসার ভিত্তিতে বৃটিশ ভারত দুভাগে বিভক্ত হয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলিম লীগের এই মূল অবলম্বনটি দ্রুত অকেজো হয়ে পড়ে। পাকিস্তানে এবং তৎসঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানরাই হিন্দুদের পরিবর্তে মূল শোষক, শাসক ও নির্যাতক; যাদের অবস্থান তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে। এই পশ্চিম পাকিস্তানিরা ছিলো পূর্ব পাকিস্তানিদের থেকে জাতিগত ও ভাষাগত এবং আঞ্চলিক দিক দিয়ে পৃথক। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানে এক নতুন দ্বন্দ্ব পূর্ববর্তী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের স্থান অধিকার করে এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙালি-অবাঙালি দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করে এবং ১৯৭১ সালে এই দ্বন্দ্ব বাস্তবত পরিণত হলো প্রধান দ্বন্দ্বে। তবে বাঙালি-অবাঙালি দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হলেও ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমাজে অন্য কতকগুলো দ্বন্দ্বেরও বিকাশ ঘটেছিল। এ গুলোর মধ্যে শ্রেণী দ্বন্দ্ব, সা¤্রাজ্যবাদের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক শক্তি ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী শক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তি ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী শক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্বটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার এজন্যে যে, ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যখনই কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করতে চেষ্টা করেছেন, তখনই তৎকালীন শাসক দল ও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা তাকে ইসলাম বিরোধী, ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানবিরোধী ইত্যাদি আখ্যায়িত করায় প্রথম থেকেই এই অঞ্চলের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যাহত এবং স্পষ্টত একটা সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী চরিত্রও পরিগ্রহ করে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে কোনো গণতান্ত্রিক ও সরকার বিরোধী আন্দোলনের কথা সেই পরিস্থিতিতে ভাবা সম্ভব ছিলো না।
১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এবং ১৯৭২-এ যে সংবিধান প্রণয়ন করে, তাতে যে মূল নীতিগুলো নির্ধারিত হয়, তার মধ্যে ধর্ম-নিরপেক্ষতা ছিলো অন্যতম। এটা ছিল খুব স্বাভাবিক। কারণ, ১৯৪৭ থেকে জনগণের সকল গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর যে ধারাবাহিক আক্রমণ তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকশ্রেণী চালিয়েছিল, সেটা তারা ধর্মের দোহাই দিয়েই সবসময় করেছিল। এজন্য জনগণের এক ব্যাপক অংশের মধ্যে রাজনিিত থেকে ধর্মকে পৃথক করার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল। এই জাগ্রত আকাঙ্ক্ষার প্রতি নমনীয় না হয়ে নতুন বাংলাদেশী শাসকশ্রেণী ও সরকারের উপায় ছিল না। যে কারণে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল, অনেকটা সে কারণেই গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রকেও ঘোষণা করা হয়েছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্য তিনটি নীতিগত স্তম্ভ হিসেবে।
এখানে উল্লেখ করতে হয়, যে কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষ না হয়ে উপায় নেই। অন্যদিকে কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই জাতীয়তাবাদকে একটি মূলনীতি অথবা কোনো ধরনের নীতি হিসেবেই স্বীকার করতে পারে না। প্রত্যেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সা¤্রাজ্যবাদবিরোধী এবং জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করতে তার চরিত্র অনুযায়ীই বাধ্য; কিন্তু কোনো প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই জাতীয়তাবাদী নয়, তার মূল চরিত্র ও নীতি আন্তর্জাতিক হতে হয়। অপরদিকে গণতন্ত্র যে অর্থে বাংলাদেশের সংবিধানে মূলনীতি হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল, তা ছিলো বুর্জোয়া গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র একইভাবে কোনো রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে থাকলে তাকে জগাখিচুড়ি ব্যতীত অন্য কিছু বলা চলে কিনা জানি না।
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে এক ধরনের চেতনার কথা সাধারণভাবে বলা হয়। কিন্তু সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে এমন কিছু কি আছে, যা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলের চেতনার মধ্যে একইভাবে প্রবহমান ছিল? এ প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময় আমরা বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনার বিষয়টি স্মরণ করতে পারি। পূর্বে বলা হয়েছে যে, বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সকল শ্রেণী, জাতি, সম্প্রদায় ও ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী সংগ্রাম করলেও তাদের সকলের স্বাধীনতার চেতনা এক ছিল না। ঠিক তেমনি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যে সকল শ্রেণী, জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায় ও ভাষাভাষী জনগণ তাতে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলো, তাদের সকলের চেতনাও পুরাপুরি এক ছিল না। মূল যে দ্বন্দ্বটি মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবলভাবে প্রধান্যে আসে, সেটি হলো, বাঙালি-অবাঙালি দ্বন্দ্ব। এই অবাঙালিরা শুধু জাতিগতভাবে পৃথক ছিলো না, তারা ছিলো অন্য ভাষাভাষী এবং অন্য অঞ্চলের বাসিন্দা। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে প্রথমেই যে চেতনার কথা বলতে হয়, তা হলো জাতিবিরোধী, ভাষা বিরোধী, অঞ্চল-বিরোধী এক চেতনা। আসলে এই চেতনাই হলো ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী পেটি বুর্জোয়া, বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং তাদের রাজনৈতিক দলগুলোর, বিশেষত আওয়ামী লীগের মূল চেতনা। মুসলিম লীগ যেমন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও তা থেকে সৃষ্ট চেতনাকে অবলম্বন করে বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান নামক একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে আওয়ামীলীগও মূলত জাতিগত দ্বন্দ্ব ও তার থেকে সৃষ্ট চেতনাকে অবলম্বন করেই বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভ করেছিল এবং ১৯৭১- এর ডিসেম্বরে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করেছে বাঙালিদের একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু শুধু জাতিগত দ্বন্দ্ব এবং তার থেকে উদ্ভূত চেতনাই ১৯৭১ সালে, এমনকি তার পূর্ববর্তী পর্যায়েও জনগণের সকল অংশের একমাত্র চেতনা ছিলো না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় জনগণের চেতনার একটা বড় অংশ গঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করার তাগিদের দ্বারা।
বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অঙ্গীকার নিয়ে। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশ ক্রমান্বয়ে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে যেমন সরে গিয়েছে, তেমনি, বিশেষত নিকট অতীত ও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের মূলেও আঘাত পড়েছে। সংসদে বাংলাদেশের সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বিল এই ধারাকে দিয়েছে আইনের স্বীকৃতি। এরপর এ কথা আরও অস্পষ্ট নয় যে, গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণ, সমাজতন্ত্রের অস্বীকার এবং ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা (যদিও পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটি ধর্মনিরপেক্ষতা পুনর্বহাল করা হলেও সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ‘ইসলাম’ ও ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ ঠিকই রয়ে গেছে। সবই একই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক। ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রেখে গিয়েছিল, বাংলাদেশেও অতীত কিংবা বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর কাছে তার প্রায়োগিক মূল্য কম নয়। অতীত থেকে নাকি কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না। কথাটার সত্যতা প্রমাণিত বললে ভুল হবে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার এই পর্যায়ে যেভাবে শুরু হয়েছে এবং সাম্প্রতিক দক্ষিণপন্থী-প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক মহল যেভাবে রাজনৈতিক জীবনে তাদের পুনর্বাসনের পর, তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলছে বা নিচ্ছে তার প্রভাব-বলয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুসারী সচেতন মহল শঙ্কিত।
যে বিষয়টি এখানে উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন যে, ক্ষমতা বহির্ভূত শোষক শ্রেণীর যে অংশটি সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলন এবং এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন, তারা তাদের এই আন্দোলন-কালে জামায়াতে ইসলামী নামক এমন এক প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অঘোষিত আঁতাতের মাধ্যমে যৌথভাবে কাজ করে ছিল, যাদের চরিত্র ১৯৭১ সালে পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। আজকের সরকার বিরোধী আন্দোলনে গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে চক্রান্তমূলক আঁতাতে আবদ্ধ হওয়ার কি কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে?-না তা নেই, এবং থাকার কথাও নয়। কাজেই ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার যেমন জিয়া-এরশাদণ্ডখালেদা সরকারের জন্য প্রয়োজন ছিল, তেমনি তা প্রয়োজন দালাল বুর্জোয়া ও সামন্ত অবশেষের রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতৃত্বাধীন জোটগুলোর জন্য। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং ক্ষমতাবহির্ভূত দালাল বুর্জোয়া ও সামন্ত অবশেষের প্রতিনিধিদের এই শ্রেণীগত ঐক্যের স্বরূপই তাদের ঘোষিত ও অঘোষিত নীতি এবং বাস্তব কর্মতৎপরতার মাধ্যমে রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হচ্ছে, যা থেকে আমরা আদৌ মুক্ত হতে পারছি না। আর পারছি না বলেই আজও মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতিতে প্রভাব ফেলছে। তাই শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক কাঙ্ক্ষিত সমাজ-রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না।
লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক মোঃ হাছান আলী সিকদার, সভাপতি, চাঁদপুর জেলা জাসদ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা, চাঁদপুর জেলা শিক্ষক নেতা, সমাজ ও রাজনীতিবিশ্লেষক।