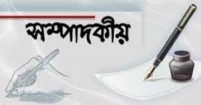প্রকাশ : ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ০৯:০৮
শরীরে মননে স্বাস্থ্য-২
চিকিৎসক ও ঔষধ কোম্পানিগুলোর অস্বাস্থ্যকর জোট ভাঙ্গতে হবে

মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি হলো চিকিৎসা। দেশের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মধ্যে অনেক ফারাক। সঠিক চিকিৎসা পেতে মানুষ ছুটে যায় নিকটস্থ ডাক্তারের কাছে। মানুষের বিশ্বাস ও আস্থায় অনেকটা জুড়ে থাকেন ডাক্তার। আর এই ডাক্তারদের একটি অংশ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছেন। এই অংশের কারণে গোটা ডাক্তার সমাজ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েন। জনকল্যাণমুখী ও বৈষম্যহীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হলে দুর্নীতিগ্রস্ত স্বাস্থ্য খাতকে ঢেলে সাজাতে হবে। স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান অন্য দেশের তুলনায় তলানিতে। এতো কম বিনিয়োগ করে দরিদ্র ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
দেশে যত খাত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয় স্বাস্থ্য খাতে। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ কম থাকা, প্রশাসনিক সুশাসন না থাকা, দুর্নীতি ও অনিয়ম, চিকিৎসকদের মধ্যে বিভক্তি ও মূল্যবোধের অভাব, রোগীর পকেট থেকে চিকিৎসা ব্যয় টানা, বেসরকারি হাসপাতালগুলোর অতিরিক্ত লাভের চিন্তা, মানসম্মত সেবার অভাব, গ্রাম ও শহরে বৈষম্য, বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতের যথাযথ ব্যবস্থাপনা, ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবায় বৈষম্য, কল্যাণমূলক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিকে চ্যালেঞ্জের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা হতে হবে জনকল্যাণমুখী, সুলভ, সাশ্রয়ী ও বৈষম্যহীন।
রোগ মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে অসহায় করে তোলে। দুর্দশাগ্রস্ত দরিদ্র রোগীদের জন্যে অসুস্থতা আরও বেশি পীড়াদায়ক। রোগগ্রস্ত মানুষকে তাদের মৌলিক অধিকার চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্যে হাসপাতাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা অপরিসীম। সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে ‘হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম’ পরিচালনা করা উচিত, যা দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায় ও আর্ত-পীড়িতদের সেবার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় রোগীদের মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অসুস্থতা বিষয়ক বিভিন্ন সহায়তার মাধ্যমে রোগীর মানসিক শক্তি বৃদ্ধি, চিকিৎসার ব্যয় বহন, চিকিৎসককে রোগীর রোগ ও রোগের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান এবং চিকিৎসা শেষে তার পুনর্বাসনের জন্যে সহায়তা প্রদান করা উচিত।
বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার মান প্রশ্নবিদ্ধ--এ নিয়ে জনমনে কোনো সংশয় নেই। প্রায়ই পত্রপত্রিকায় ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু, রোগী ও রোগীর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকদের সংঘর্ষ, চিকিৎসকদের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি ও কর্মবিরতির খবর পাওয়া যায়। আর এসব খবর প্রচার করতে গিয়ে সাংবাদিকরা চিকিৎসকদের প্রতিপক্ষে পরিণত হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়।
সুচিকিৎসার অভাবে প্রিয়জনদের হারানোর বেদনা, হাসপাতালে মানুষের অসহায়ত্ব, চিকিৎসার অভাবে কাতর যন্ত্রণা, চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু আমাদের মনকে নাড়া দেয়। রোগীর পেটে অস্ত্র রেখে সেলাই করা, শেওলাযুক্ত স্যালাইন রক্তে প্রবাহিত করা, ভুল সিজার, মৃত ব্যক্তিকে আইসিইউতে রেখে বিল বাড়ানো, কর্মচারী ও নার্স দিয়ে অস্ত্রোপচার করানোর মতো ঘটনা অসত্য নয়। চিকিৎসকদের নির্ধারিত ফি পরিশোধ করেও প্রাপ্য সেবাটুকু না পাওয়া আমাদের চিকিৎসাসেবার মানকে অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে বলে মনে হয়। চিকিৎসকদের পেশাগত অদক্ষতা ও দায়িত্ববোধের অভাব এর অন্যতম কারণ। এ ছাড়া মানুষের অসচেতনতা, খাদ্যাভাস, খাদ্যে ভেজাল ও বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
অনেক সময় রোগী মারা গেলে অভিযোগ করা হয়, ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসা যে ভুল হয়েছে এটি রোগী বা রোগীর স্বজনরা কিভাবে নিশ্চিত হয় তার যথাযথ ব্যাখ্যা পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে মুদি দোকানেও অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া যায়, যা বিশ্বের কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। বাইরে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ কেনা যায় না, এমনকি ভিটামিন ট্যাবলেট কিনতেও চিকিৎসকের অনুমতি লাগে। অনুমোদিত ফার্মেসি ছাড়া কোথাও ওষুধ বিক্রি হয় না এবং এসব ফার্মেসিতে ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করা থাকে, যাঁরা ক্রেতাকে ওষুধের ধরণ, কার্যকারিতা ও ব্যবহারবিধি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন। আমাদের দেশে ওষুধের গুণগত মান ঠিক আছে কি না, মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে কি না তা সঠিকভাবে মনিটর করার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে ভেজাল ও নিম্নমানের ঔষধে বাজার সয়লাব। এ ছাড়া জ্বর হলে প্যারাসিটামল, ব্যথা হলে ব্যথানাশক, কখনো বা নিজের পছন্দেই অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খায়, চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ কিনতে গেলে অনেক সময় দোকানদার একই গ্রুপের ওষুধের কথা বলে বেশি লাভের আশায় নিম্নমানের বা ভেজাল ওষুধ দিয়ে থাকে। এসব ওষুধ খেয়ে রোগী সুস্থ না হলে বা রোগ জটিল হলে দোষী হন চিকিৎসকরা।
শহরের বাইরের হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সঙ্গে শহরের হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সমন্বয় না থাকায় এবং রোগী বা রোগীর স্বজনদের সঠিক তথ্য বা পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় অনেক রোগী চিকিৎসকের নাগাল পাওয়ার আগেই প্রতারণার শিকার হয়ে অর্থ ও জীবন দুটিই হারিয়ে ফেলে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।
দেখা যায়, দূর-দূরান্ত থেকে সাধারণ মানুষ উন্নত চিকিৎসার আশায় শহরের হাসপাতালগুলোতে ভিড় জমায়। বাড়তি রোগীকে করিডোর বা মেঝেতে জায়গা দিতে গিয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন ঘটে। এই ভিড় কমাতে হলে উপজেলাগুলোতে সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। উপজেলা হাসপাতাল ও জেলা হাসপালগুলোকে সমন্বয়ের মাধ্যমে সেবা দিতে হবে। এ ছাড়া অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। চিকিৎসকের ফি এবং একজন চিকিৎসক প্রতিদিন বা সপ্তাহে সর্বোচ্চ কয়জন রোগী দেখতে পারবেন তার সংখ্যাও নির্ধারণ করে দিতে হবে। এসব বিষয়ে চিকিৎসক নেতাদের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং শাস্তির বিধান রেখে আইন করতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিভিন্ন রিপোর্টে কোনো ভুলের কারণে রোগীর ক্ষতি হলে সেই রিপোর্টের সিগনেটরি চিকিৎসককেও আইনের আওতায় আনতে হবে।
চিকিৎসকদের শুধু প্র্যাকটিসমুখী হলে চলবে না, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় অবশ্যই মনোনিবেশ করতে হবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ছাড়া একজন চিকিৎসক কখনোই বিশেষজ্ঞ হতে পারেন না। তবে আমাদের দেশের চিকিৎসকরা অবশ্যই মেধাবী ও বিচক্ষণ। দেশ ও বিদেশে অনেকেরই খ্যাতি রয়েছে। তাঁদের অবদানে শিশুমৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে, দেশের প্রতিটি শিশুকে টিকাদান কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং রোগ নির্ণয়ে প্রযুক্তিগত ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।
বাংলাদেশের রোগীদের চিকিৎসার জন্যে বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। এর কী কারণ? বিদেশ থেকে ফেরা রোগীদের বর্ণনা থেকে যে প্রধান কারণগুলো স্পষ্ট হয়, তা হলো : ১. বিদেশে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা করানো যায়। ২. উচ্চমানের চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া যায়। দ্রুত রোগ নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসা হয়। ৩. চিকিৎসকরা আন্তরিক ব্যবহার করেন। পর্যাপ্ত সময় ও মনোযোগ প্রদান করেন।
বিদেশের তালিকায় প্রথমত পড়ে ভারত (জুলাই বিপ্লবের পর কিছুটা কমেছে), সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া। যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত দেশও আছে অতি ধনীদের পছন্দের তালিকায়। বিদেশগামী বাংলাদেশি রোগীদের সবচেয়ে বড়ো গন্তব্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। উচ্চমানের চিকিৎসা সুবিধার পাশাপাশি এর কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের স্থলপথে যোগাযোগ। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে ঢাকায় যেতে যতো সময় লাগে, ভারতে যেতে তার চেয়ে কম সময় লাগে। ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের খাবার-দাবার, ভাষা এবং সংস্কৃতির রয়েছে অনেক মিল।
এক হিসাবে দেখা গেছে, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ থেকে ২ লাখ ২১ হাজার ৭৫১ রোগী চিকিৎসার উদ্দেশে ভারতে গেছেন। তারা খরচ করেছেন আনুমানিক পাঁচ হাজার কোটি টাকা। প্রতি বছর বাংলাদেশি রোগীদের ভারতমুখী স্রোত বেড়েই চলেছে। এর কারণ দেশের চিকিৎসা সেবায় জনগণের আস্থাহীনতা, অরাজক অবস্থা, নিম্নমানের সেবা ও উচ্চ খরচ।
বাংলাদেশের রোগীরা ভারতে যান জটিল হার্ট সার্জারি, ক্যানসারের চিকিৎসা, অঙ্গ প্রতিস্থাপন, বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসা, অস্থি ও অস্থিসন্ধির অপারেশন, স্নায়ুরোগ, কিডনি রোগ, মেডিকেল চেকআপের জন্যে। অবাক হলেও সত্য, স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের চেয়ে ভারত পিছিয়ে। মা ও শিশুমৃত্যু হ্রাসের লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়নি ভারত। অথচ সেই দেশটি দিনে দিনে চিকিৎসা পর্যটনের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে! কোনও এক দেশ থেকে অন্য আরেক দেশে সুলভ মূল্যে সুচিকিৎসার আশায় ভ্রমণ করাকে বলা হয় চিকিৎসা পর্যটন। কোনও একটি দেশ নিজেকে চিকিৎসা পর্যটনের গন্তব্যে পরিণত করতে চাইলে প্রথম শর্ত হলো দেশটিকে সুলভ মূল্যে উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। ভারত সেই কাজটি করতে পেরেছে। শুধু বাংলাদেশি রোগী নয়, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ রোগী ভারতে চিকিৎসা নিতে আসেন।
চিকিৎসা সামগ্রী আমদানিতে ভারতে করের পরিমাণ মাত্র ১২ শতাংশ। বাংলাদেশে এই করের হার ৪৫%। একই পণ্য আমদানি বা ক্রয় বিক্রয়ের জন্যে ভারতে মাত্র একবার ভ্যাট দিতে হয়। অথচ বাংলাদেশে বারবার ভ্যাট দিতে হয়। ভারতে সরকার ও করপোরেটেরের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় ও বিপুল বিনিয়োগে বেসরকারি হাসপাতালগুলো উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ, ভেতরের চাকচিক্যপূর্ণ সাজসজ্জা, গ্রাহক যত্ন পরিষেবা, নিয়মিত চিকিৎসা সরঞ্জাম উন্নতকরণ এবং সর্বদা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও চিকিৎসা সেবাকে তারা দ্রুততম সময়ে প্রচলন করতে পেরেছে। রোগীকে সেবা দেওয়ার পূর্ণাঙ্গ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তারা গড়ে তুলেছে।
ভালো ব্যবহার ভারতীয় চিকিৎসকদের নিছক ভালোমানুষী বা মানবিকতার বহিঃপ্রকাশ নয়, এটি তাদের করপোরেট সংস্কৃতির বাধ্যবাধকতা। ভারতের চিকিৎসকদের জবাবদিহি করতে হয়। চিকিৎসা অবহেলার অভিযোগ আমলে নেওয়ার সময় মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া রোগীবান্ধব অবস্থানে থাকে। যা চিকিৎসকদের ভুল করা থেকে সতর্ক থাকতে ও চিকিৎসায় প্রমাণভিত্তিক অনুশীলনে বাধ্য করে।
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, ল্যাব রিএজেন্ট, ভ্যাকসিনের জন্যে আজও আমরা পুরোপুরি আমদানিনির্ভর দেশ। দেশ নিজস্ব উৎপাদন সক্ষমতা তৈরি করতে পারেনি। নিজস্ব উৎপাদিত চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবহার সেবামূল্য কমাতে পারতো। সরকারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কিছু নির্বোধ, অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজনের দখলে। যা অনেক সেবার অবিশ্বাস্য মূল্য তৈরি করছে। তিক্ত হলেও সত্যি, সরকারি খাতের মতো বাংলাদেশের বেসরকারি খাতও ব্যাপকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত।
বিগত বছরগুলোতে আন্ডার গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট ভর্তিতে সীমাহীন দুর্নীতি স্বাস্থ্য খাতে দীর্ঘমেয়াদে দুর্বল, অনৈতিক জনশক্তি সৃষ্টি করেছে। একই সময় চিকিৎসা শিক্ষার মানের ভয়ংকর অবনমন, মানহীন মেডিক্যাল কলেজের অপরিমিত সংযোগ হয়েছে। তারা স্বাস্থ্য খাতে ঝুঁকি তৈরি করেছে। এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা অনেক কম। আবার যারা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের কাছেই রোগীরা যেতে চান। তাই তারা রোগীকে সময় দিতে পারেন খুবই কম। রোগীর তুলনায় দেশের হাসপাতালে শয্যা, চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যা কম। অত্যাধুনিক প্রাগ্রসর ও দক্ষতানির্ভর ডায়াগনস্টিক পরীক্ষাসমূহে ঘাটতি স্পষ্ট। ল্যাবরেটরি পরীক্ষার নির্ভুলতা নিশ্চিতে মান নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার উচ্চমূল্য চিকিৎসা সেবাকে ব্যয়বহুল করছে।
প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অন্তহীন অভিযোগ। তারা রোগীদের সময় দেন না। অবহেলা ও দুর্ব্যবহার করেন। অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় টেস্ট করতে বলেন, পরীক্ষার রিপোর্ট ভুল আসে, একই টেস্টর রিপোর্ট একেক ডায়াগনস্টিকে একেক রকম আসে, ডায়াগনস্টিকে পরীক্ষা না করে রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগ, চিকিৎসকরা প্রেসক্রিপশনে অতিরিক্ত ওষুধ লেখেন, তারা ওষুধ কোম্পানি, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কাছ থেকে কমিশন পান। সারাদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ক্লিনিকে অপ্রয়োজনীয় সার্জারি, সার্জারির নামে প্রতারণা, রোগীদের কাছ থেকে যেনতেন প্রকারে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।
আধুনিক সমাজ দর্শনে ভোক্তাই সঠিক। ভোক্তা ও সেবা প্রদানকারী দুই পক্ষই আজ মনোজাগতিক দুই মেরুতে, নিজেদের অবস্থানে অনড়। একটা দেশের স্বাস্থ্য পদ্ধতি কেমন হবে, কীভাবে কাজ করবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই দেশটির নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কীভাবে নির্মিত হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং পুরো সিস্টেমের আচরণ। অতএব, নীতিনির্ধারক ও জনগণের অগ্রগামী অংশকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সঠিক নীতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে গড়ে তুলতে হবে শক্তিশালী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা।
চিকিৎসকদের বাইরে অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা সহায়ক কর্মী, যেমন-নার্স, হেলথ টেকনোলজিস্ট, ওয়ার্ড বয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। তাদের দক্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্যে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
চিকিৎসকদের কমিশন দেওয়া বন্ধ করতে হবে; সেই সাথে চিকিৎসক ও ওষুধ কোম্পানিগুলোর অস্বাস্থ্যকর জোট ভাঙ্গতে হবে। এ জন্যে সরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ ও ডায়াগনস্টিক পরীক্ষাসমূহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে পারলে সিংহভাগ অসৎ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
হাসপাতালগুলোর পরিবেশ নিয়ে ভালোভাবে ভাবতে হবে। কিছু কিছু হাসপাতাল আছে সুস্থ মানুষ আসলেও অসুস্থ হয়ে পড়ে। শুধু চিকিৎসায় নয়, হাসপাতালে এসে মানুষ যেন মানসিক প্রশান্তি পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবেশটা এমন হতে হবে রোগী যেন মনে করে সে হাসপাতাল নয় বাড়িতে আছে। বর্তমানে সরকারি হাসপাতালগুলোতে শিশুদের জন্যে একটা কর্নার নির্ধারণ করে সেখানে কিছু রাইড রাখা হয়েছে। অত্যন্ত সুন্দর এবং ভালো সিদ্ধান্ত। এ রকম করে রোগীদের জন্যে পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। হাসপাতালে একটি লাইব্রেরী রাখা খুব বেশি প্রয়োজন। বইও এক ধরনের মেডিসিন। হাসপাতালের বাইরের অংশকে ফুলে ফুলে সাজিয়ে রাখতে হবে। হাসপাতালের ভেতর এবং বাইরে পরিষ্কার রাখতে হবে।
লেখক পরিচিতি : সাধারণ সম্পাদক, ফরিদগঞ্জ প্রেসক্লাব; প্রতিষ্ঠাতা : ফরিদগঞ্জ লেখক ফোরাম।