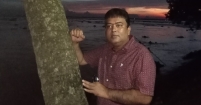প্রকাশ : ০৩ এপ্রিল ২০২৪, ০০:০০
দলিতের মুক্তিতে আম্বেদকর ও বৌদ্ধধর্ম

“আমি এমন ধর্মকে মানি যে স্বাধীনতা, সাম্যতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ শেখায়।“ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর
মানুষ জন্মমাত্রই কিছু মৌলিক অধিকারের দাবিদার হয় যার মধ্যে স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা ও স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার মুখ্য। ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোত্র কিংবা জন্মস্থানের ভিন্নতা দিয়ে মানুষকে দাবিয়ে রাখা বা দলিত করা যাবে না। কিন্তু বৈদিক যুগে সনাতনী সমাজে চতুর্র্বণাশ্রম প্রথা বা বর্ণভেদ প্রথার কারণে মানুষের মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হত চরমভাবে। এতে মানুষকে মানুষরূপে না দেখে বরং দাসরূপে দেখার প্রবণতা ছিল। ফলে সব মানুষের সমানভাবে ধর্মালয়, শিক্ষালয়, জলাশয় কিংবা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার ছিল না। ঋকবৈদিক যুগের শুরুতে আর্য বর্ণ ও দস্যু বর্ণ, এই দুই বর্ণ দিয়েই মানুষকে আলাদা করে বোঝাত যা মূলত গায়ের বর্ণের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হতো। আর্যদের কাছে অনার্যরা ছিল দস্যু বা দাস। ঋকবেদের দশম মন্ডলে প্রথমবারের মতো চতুর্বর্ণের উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে পেশার ভিত্তিতে সমগ্র মানব সমাজকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণের কাজ হল জ্ঞানচর্চা, ক্ষত্রিয়রা ছিল যোদ্ধা ও শাসক , বৈশ্যের কাজ ছিল উৎপাদন করা এবং শূদ্ররা ছিল অন্য তিন বর্ণের সেবায় নিয়োজিত। প্রাথমিক ভাবে এই বিভাজন পেশা ও শ্রম ভিত্তিক হলেও পরবর্তী সময়ে তা জাতিভিত্তিক সামাজিক বিভাজনে পরিণত হয়, যেখানে ব্রাহ্মণরা পরিণত হয় সমাজের সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী শ্রেণিতে এবং বিপরীতপক্ষে শূদ্ররা হয়ে যায় অধিকারহীন মানহীন শ্রেণিবিশেষ। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে এই বর্ণভেদ প্রথা যেন হয়ে উঠে আরও তীব্র এবং সর্বনাশী। ব্রাহ্মণদের সর্বসুবিধা ভোগের পাশাপাশি কিছু মানুষ ক্রমশ হয়ে উঠে অস্পৃশ্য। এরাই ধীরে ধীরে দলিত শ্রেণি নামে অভিহিত হয়। উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের আগে ব্রিটিশ রাজত্বে আদম শুমারিকালে ডিপ্রেসড ক্লাস বা অবহেলিত শ্রেণি নামে একটা জনগোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করা হয়। এই ডিপ্রেসড জনগোষ্ঠীরই অনূদিত রূপ হলো দলিত শ্রেণি। অর্থনীতিবিদ এবং নৃতাত্ত্বিক সংস্কারক ভীমরাও রামজি আম্বেদকর 'দলিত' শ্রেণির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেন। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অধিকারবঞ্চিত সকল মানুষকে দলিতের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করেন। দলিতদের অনেকেই চতুর্র্বণাশ্রমের বাইরে পঞ্চম বর্ণ বা পঞ্চমা নামেও অভিহত করে। প্রকৃত অর্থে ' দলিত ' শব্দটি মারাঠি ভাষা হতে উদ্ভূত যার অর্থ দমিত বা চাপিয়ে রাখা বুঝায়। তবে বর্তমানে ভারতীয় আদালত কর্তৃক দলিত শব্দটির ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে এবং কেরালায় তা ব্যবহৃত হয় না। সাংবিধানিক পরিভাষা অনুযায়ী, গত দুহাজার আঠার সালের সেপ্টেম্বর থেকে দলিতদের 'তফসিলি জনজাতি' হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। দুহাজার এগার সালের শুমারি অনুযায়ী ভারতে দলিতের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ কোটির অধিক যা তাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ষোল ভাগ। ভারতে দলিতদের অধিকাংশই মহারাষ্ট্র এবং কেরালায় বাস করে। বাংলাদেশে দলিতদের সংখ্যা প্রায় পঁয়ষট্টি লাখ।
শুধু অবাঙালি দলিত হরিজন নন, বাঙালি দলিতরাও অচ্ছুত, অস্পৃশ্য। চর্মকার, মালাকার, কামার, কুমার, জেলে, পাটনী, কায়পুত্র, কৈবর্ত, কলু, কোল, কাহার, ক্ষৌরকার, নিকারী, পাত্র, বাউলিয়া, ভগবানীয়া, মানতা, মালো, মৌয়াল, মাহাতো, রজদাস, রাজবংশী, কর্মকার, রায়, শব্দকর, শবর, সন্ন্যাসী, কর্তাভজা, হাজরা প্রভৃতি সম্প্রদায় আজ আমাদের স্বাধীন দেশে অস্পৃশ্যতার শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ প্রচারিত লিফলেট অনুযায়ী বাংলাদেশে পরিচ্ছন্ন পেশায় নিয়োজিত বাঁশফোড়, হেলা, লালবেগী, ডোমার, রাউত, হাঁড়ি, ডোম (মাঘাইয়া) ও বাল্মিকী এ আট জাতের জনগোষ্ঠী নিজেদের হরিজন দাবি করেন। পরিচ্ছন্ন সেবায় নিয়োজিত বলে শুধু তারাই বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও অন্য জনগোষ্ঠীরও হরিজন আছেন। তারা ব্যবসা বা অন্য কাজ করেন।
সমাজের বর্ণবাদী মানুষেরা দলিতদের অস্পৃশ্য করে রেখেছে বিভিন্ন অযুহাতে। তারা দলিতদের হেয় করে দেখে বলেই তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য নিজেদের মতো করে তৈরি করেছে। তৎকালীন সরকারি সংজ্ঞা মোতাবেক দলিতরা গাছ তলায় ঘুমায়, ব্রাহ্মণকে পূজা করে না, তারা গো-মাংস ভক্ষণ করে, তারা কোন উচ্চবর্গের গুরুর কাছে দীক্ষা নেয় না, তারা মৃতদেহ সমাহিত করার মাধ্যমে সৎকার করে, তারা লোহার অলঙ্কারাদি ধারণ করে এবং কুকুর,গাধা প্রভৃতি অন্ত্যজ প্রাণী তাদের সম্পত্তি। তারা কোন নির্দিষ্ট জায়গায় স্থায়ী না থেকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে। কোন উচ্চবর্গের হিন্দু যদি তাদের সংস্পর্শে আসে তবে তার মৃত্যুদন্ড সুনিশ্চিত।
দলিতদের মুক্তিতে আম্বেদকর :
কেবল দলিতদের ইতিহাসেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবং ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের পুনর্জাগরণের ইতিহাসে বাবা সাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি কেবল স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী ছিলেন না, তিনি ভারতের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতিও বটে। ঊনিশশো নব্বই সালে তাঁর জন্মশতবর্ষে ভারত সরকার তাকে সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' (মরণোত্তর) খেতাব প্রদান করে নিজেদের ধন্য করে। লোকেরা তাঁকে বাবা সাহেব নামে ভালোবেসে ডাকে। আবার তাঁর নেতৃত্বে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত দলিতদের কাছে তিনি নতুন যুগের বোধিসত্ত্ব।
ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত দলিত হিন্দু রামজি মালোজী সাকপাল এবং ভীমা বাঈ এর চতুর্দশ তথা কনিষ্ঠ সন্তান হলেন আম্বেদকর। মহারাষ্ট্রের মহও গ্রামে মহর নামের অস্পৃশ্য অন্ত্যজ শ্রেণিতে তাঁর জন্ম। সৌভাগ্যক্রমে বৃটিশরাজ সেনাবাহিনীতে কর্মরত নিচুজাতের মানুষের ছেলেপেলেদের পড়াশুনার জন্যে আলাদা স্কুল করেছিল তাই নির্বিঘ্নে তাঁর প্রাইমারি পড়াশুনা সমাপ্ত হলো। কিন্তু মাধ্যমিক স্কুলে যাওয়ার সাথে সাথেই শুরু হলো অস্পৃশ্যতার যন্ত্রণা। স্কুলের পিয়ন উঁচু থেকে পানি ঢেলে দিলে সেই পানি আঁজলা ভরে খেতে হতো আম্বেদকরকে। যেদিন কোন কারণে স্কুলে পিয়ন আসতো না, সেদিন আম্বেদকরের পানি পান করা হতো না। পিপাসা লাগলেও বিনা পানি পানে তাঁর স্কুল শেষ হতো। ঊনিশশো সাত সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম অস্পৃশ্য হিসেবে ভারতের বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তাঁর এই সাফল্য দলিত সম্প্রদায়কে উদ্দীপ্ত করে তোলে এবং অধিকার আদায়ের আশা যোগায় । ঊনিশশো বার সালে তিনি বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি এবং রাজনীতি বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এবং বারোদা রাজ্যে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন।
ঊনিশশো সাতাশ সালে আম্বেদকর মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলায় পানীয় জল ব্যবহারকে কেন্দ্র করে মাহার সত্যাগ্রহ শুরু করেন। এরপর তিনি হিন্দুধর্মের বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথার মূলভিত্তি তথা ‘মনুস্মৃতি’ গ্রন্থটি প্রকাশ্যে আগুনে পোড়ান।
ঊনিশশো বত্রিশ সালে দলিত নেতা আম্বেদকরের প্রচেষ্টায় নতুন সংবিধানে অস্পৃশ্যদের জন্য আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতির ফলে কংগ্রেসের ভোট পাছে কমে যায় এবং মুসলিম লীগের সুবিধা হয় এই কূটকৌশলের কারণে মহাত্মা গান্ধী এতে বিরোধিতা করেন। গান্ধী উনিশশো বত্রিশ সালের সেপ্টেম্বরে অনশনে বসেন। চতুর গান্ধী ভুবনজয়ী দলিত ক্রিকেটার পালওয়াঙ্কর বালুকে ডেকে নিজের খুঁটিরূপে ব্যবহার করেন। আম্বেদকর গান্ধীর অনশন ও চতুরতার কারণে পিছু হটলেও
তিনি গান্ধীর ভূমিকা মেনে নিতে পারেননি। ঊনিশশো তেত্রিশ সালে গান্ধী অস্পৃশ্য দলিতদের হরিজন নাম দিয়ে আন্দোলন স্তিমিত করতে চাইলেও আম্বেদকর এটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি।
দলিতদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের পরিবর্তে আসন সংরক্ষণের নীতির মাধ্যমে বর্ণ হিন্দু ও অবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছিল যার নাম ছিল পুনা চুক্তি। এর পর থেকেই অস্পৃশ্য হিন্দুদের সরকারি নামকরণ হয়েছিল তফশিলি জাতি বা শিডিউল কাস্ট। এতকিছুরও পরও সমাজে দলিতদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার হতে বঞ্চিত রাখা হয়। আম্বেদকর দলিতদের এইভাবে নির্যাতিত হতে দেখে ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেন, কারণ বৌদ্ধ ধর্মে কোন জাতপাত ভেদ নেই। এটা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে। এতে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির হাতে বুদ্ধের প্রধান সেবক আনন্দকে নিঃশঙ্কোচে জলপান করতে দেখে তারা প্রত্যেকেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং বুদ্ধের মৈত্রী লাভ করেন। দলিত হিন্দুদের জ্ঞানবান নেতা দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে নিজের মনকে প্রস্তুত করে বিপুল সংখ্যক দলিত হিন্দু অনুসারীসহ ঊনিশশো ছাপান্ন সালে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। হিন্দু ধর্মের উচ্চবর্গের অমানবিক অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আম্বেদকরের এই প্রতিবাদ সারা ভারতকে নাড়িয়ে দেয়।
আঠারোশ আটানব্বই সালে পন্ডিত ইয়োথি থাস তামিলনাড়ুতে শাক্য বৌদ্ধ সমাজ ( যা ভারতীয় বৌদ্ধ সমিতি নামেও পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করে দলিতদের জন্য হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় বিকল্প হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মকে উপস্থাপন করেন। থাসের প্রচেষ্টার ফলে উনিশশো পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে তামিল দলিতদের মধ্যে একটি বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে ওঠে। আম্বেদকরবাদী আন্দোলনের সমান্তরালে ভারতীয় বৌদ্ধ সমিতি শ্রীলঙ্কায় প্রতিষ্ঠিত থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে।
তথ্যপঞ্জি
১. Omvedt, Gail. Buddhism in India : Challenging Brahmanism and Caste. 3rd ed. London/New Delhi/Thousand Oaks: Sage, 2003.
২. Anand Teltumbde (2016)| Dalits: Past, Present and Future| Taylor & Francis
৩. Lars Fogelin (2015)| An Archaeological History of Indian Buddhism| Oxford University Press
৪. ডঃ শুচিস্মিতা রায় পাল,দলিত আন্দোলন
৫. আনারুল হক আনা, বাংলাদেশের হরিজন ও দলিত জনগোষ্ঠী