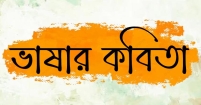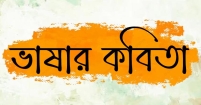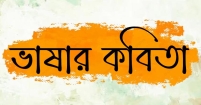প্রকাশ : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৯
খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ড জীবন

(চল্লিশতম পর্ব)
আমি ও আমার দিদিমা
আমি ও আমার ভাইবোনদের জীবনে ঠাকুরদা-ঠাকুরমা (পিতামহ-পিতামহী) এবং মাতামহকে জীবিত দর্শনের সুযোগ হয়নি। পিতামহ-পিতামহী আমাদের মা-বাবার বিবাহের আগেই প্রয়াত হয়েছেন। মাতামহ জীবিকার উদ্দেশ্যে তৎকালীন বার্মা গিয়ে আর দেশে ফিরে আসার সুযোগ হয়নি। তিনি ঊনিশশো বিরাশি সালে ওখানেই প্রয়াত হন। ফলে তাঁকেও আমাদের স্বচক্ষে দেখা হয়নি। এমনকি দূরালাপনীতেও কথা হয়নি। কেবল চিঠির যোগাযোগ এবং লোক মারফত খবর আদান-প্রদানে আমার মা ও মামারা জানতেন, তাদের পিতা বার্মায় জীবিত আছেন এবং তাদের জন্যে জীবনযাপনের আবশ্যিক অর্থ সময়মত পাঠাতেন। বাংলাদেশে এসে জীবিকার সংস্থান নিয়ে তাঁর সংশয় ছিলো বিধায় একবারের জন্যে স্বভূমে ফিরে আসেননি। তাই সংগত কারণেই আমাদের যত আদর ও আব্দার আমার দিদিমার কাছেই মজুদ ছিলো। আমার বাবাও বালকবেলায় তাঁর মা হারানোর উদ্ভূত ঘাটতিতে আমার দিদিমা তথা তাঁর শাশুড়ি মাকে নিখাদ মাতৃতুল্য সমীহ ও ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবেই শাশুড়ির মাঝে মাকে প্রতিষ্ঠিত করে আমার বাবা তাঁর ঘাটতি দূর করেছিলেন। আমাদের গ্রামের যাঁরা বয়স্ক নারী ছিলেন, বাবার কাকীমা গোত্রীয়, তাঁরাও বাবার কাছ থেকে তেমনই আদর ও ভালোবাসা পেয়েছেন। এদের একজন হলেন আমার ঠাকুরমা শ্রেণির শশীবালা বড়ুয়া এবং সমুদ্রজা বড়ুয়া। এ দুজনকেও বাবা বেশ মাতৃভক্তিতে শ্রদ্ধা করতেন এবং সপ্তাহান্তে তৎকালীন দশটাকা করে হাতখরচ দিতেন।
আমার দিদিমা সরোজা বালা বড়ুয়ার সাথে আমার স্মৃতি বেশ প্রখর। তিনি বঙ্কিম-শরৎ পড়ে পড়ে নিজের মনোজগত আধুনিক করে তুলেছিলেন। আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা, দেবীচৌধুরানী এগুলো তাঁর পড়া ছিলো বেশ কয়েকবার। তাঁকে যখন আমি প্রথম দেখি আমার বুঝদার বয়সে, তিনি তখন চোখে চশমা দিতেন। মাথায় একরাশ কাশফুল। সাদা জমিনের শাড়ি, কালো বা নীল পাড়। এটাই তাঁর ছবি। তাঁর পায়ের দুটো বৃদ্ধাঙ্গুলের অগ্রভাগের হাড় সামনের দিকে প্রবর্ধিত। এটাও তাঁর একটা শনাক্তকরণ চিহ্ন। তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে আমার মেজদা সেই বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছেন। আমার দাদুর নাম রঘুনন্দন বড়ুয়া। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় এটার উচ্চারণ হতো রউনানন্দন বলে। আবার রসুনকে বলা হয় রউন। তখনকার দিনে স্বামীর নাম স্ত্রীরা মুখে আনতেন না। তাই আমার দিদিমাও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় রসুন ও রঘুনন্দনের উচ্চারণ কাছাকাছি বিধায় আমার দিদিমা বিয়ের পরে কখনও রসুনকে রসুন বলতেন না। বরং বলতেন সাদা পিঁয়াজ। এ বিষয়ে একটা চমৎকার গল্পও প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তির নাম ছিলো বেলা। তার স্ত্রী তাকে হাট থেকে দুটাকার বেলা বিস্কুট আনতে বলেছিলেন। যেহেতু স্বামীর নামও বেলা, তাই বলার সময় তিনি বলেছিলেন, ‘আঁরলাই দুই টেঁয়ার তুঁউই (তুমি) বিস্কুট আইননো।’ কিন্তু স্বামী বেচারা তা বুঝতে না পারার কারণে সারা হাট ঘুরেও কোনো বিস্কুট না পেয়ে খালি হাতে ফিরে আসলেন। ঘরে এসে পেরেশানি মুখে স্ত্রীকে বললেন, ‘’আঁই গোডা হাডত ঘুরি খনো তুঁউই বিস্কুট ন ফাইলাম।’’ তার কথা শুনে স্ত্রী হেসে খুন। তারপর বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, ‘’বিস্কুটর নাম আর তোঁয়ার নাম ত এককই।’’ শুনে স্বামী হো হো করে হেসে উঠলেন। আমার দিদিমার ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে এ রকম হতো। যারা তাঁর এ বিষয়টি জানতেন না, তারা অবাক হয়ে থাকতেন, সাদা পিঁয়াজ জিনিসটা আবার কী! আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় কালুরঘাট সেতু পার হয়ে হেঁটে হেঁটে তাঁর বারো বছর বয়সী ছোট ছেলেকে নিয়ে তিনি আমাদের গ্রামে আসতেন। তখন ব্রিজে পাহারায় থাকা খান সেনারা তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, ‘এয়া বুড্ডি, কাঁহা যা তা হ্যায়?’ তিনি বেশ ডাঁটের সাথে জবাব দিতেন, ‘হাম চায়না বুড্ডিস্ট হ্যায়। মেরি বেটিকো পাস যাতা হ্যায়।’ এটুকু বললেই নাকি তিনি ছাড় পেতেন আমাদের বাড়ি আসতে। শৈশবে তিনি যখন আমাদের বাড়ি আসতেন তখন কারও পেট ফাঁপলে পেটের ওপরে কেরোসিন মেখে দিতেন। এই ছিলো তাঁর থেরাপি। এটা তখনকার দিনে অধিকাংশ ঘরেরই চিত্র ছিলো।
ছয় বছর বয়সে আমাকে পাগলা কুকুরে কামড় দেয় ঘাড়ে-গর্দানে। সে সময় জেলা পরিষদে আবেদন করে আমার জন্যে র্যাবিজ ভ্যাক্সিন আনানো হয়েছিলো। প্রতিদিন নাভির চারপাশে একটা করে মোট চৌদ্দ দিন আমাকে ইঞ্জেকশন নিতে হয়েছিলো। এই ইঞ্জেকশন মারানোর জন্যে মামাবাড়িতে আমাকে টানা চৌদ্দদিন থাকতে হয়। দিদিমার তত্ত্বাবধানে থেকে তাঁদের গ্রামে এলএমএফ ডাক্তার শায়েস্তা খানের কাছে সকাল দশটার দিকে গিয়ে ইঞ্জেকশন মারতে হতো। তাঁর কাছে যতদিন ছিলাম ততদিন দুপুরের দিকে মনটা উদাস হয়ে যেতো আমার বাড়ির জন্যে। রাস্তার দিকে ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আমি গাড়ি গুণতাম। বাস, বেবিট্যাক্সি ইত্যাদি। চট্টগ্রাম শহর থেকে কালুরঘাটগামী বাসগুলোকে তখন বলা হতো কালুরঘাইট্যা মুড়ির টিন। কারণ, মুড়ির টিনে যেভাবে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে উপচে পড়ানো অবস্থায় মুড়ি ভরানো হতো, তেমনি করে এইসব বাসেও যাত্রী উঠানো হতো। বাসগুলো অতি ব্যবহারে জীর্ণ ছিলো। সামনের দিকে প্রবর্ধিত অংশে থাকতো ইঞ্জিন। দেখতে শিশু ঐরাবতের শুঁড়ের মতো মনে হতো। গাড়ি স্টার্ট দিতে হতো সামনের মুখ দিয়ে হ্যান্ডেল ঢুকিয়ে জোরে ঘুরিয়ে। কখনও কখনও রেডিয়েটরের পানি মাঝ রাস্তায় শুকিয়ে গিয়ে ধোঁয়া উঠতো। তখন গাড়ি থামিয়ে হেল্পার কাছের কোনো পচা পুকুর বা ডোবা থেকে বালতিতে পানি এনে বনেট খুলে তা ভরিয়ে তুলতো। এই বাসগুলো ছিলো বিভিন্ন বাণীর নোটিসবোর্ডের মতো। অনেকটা আজকের গ্রাফিতির মতো। ভেতরের দেওয়ালে লেখা থাকতো--গাড়িতে ৫০, ১০০ টাকার ভাংতি নাই। মালামাল নিজ দায়িত্বে রাখুন। আগে নামতে দিন, লাইনে দাঁড়ান। ব্যবহারে বংশের পরিচয়। কখনও দায়িত্ব বানানটা আমি শুদ্ধ লিখতে দেখিনি। সব সময় দেখতাম ‘দ্বায়িত্ব’ লেখা। সব বাসের পেছনে একটা কথা লেখা থাকতো : ‘ পেইন্টার ও ডেইন্টার ডেম বাবু।’ এ কথার অর্থ বুঝতে আমার বেশ সময় লেগেছিলো। দুপুর বারোটা বাজলেই ইব্রাহিম ম্যাচ ফ্যাক্টরির সাইরেন বেজে উঠতো। হু-উ-ৎ করেই। তখন দিদিমার তোড়জোড় শুরু হয়ে যেতো দুপুরে আহার সমাপ্তির জন্যে। কালুরঘাট শিল্প এলাকা বলেই চাঁদগাঁও বড়ুয়া পাড়ায় টেনারির দুর্গন্ধ ভেসে আসতো। কখনও কখনও এর দৌরাত্ম্যে টেকা দায় ছিলো। আমাদের এক দাদু ভান্তে (বৌদ্ধ ভিক্ষু) হয়ে আমাদের গ্রামে ছিলেন। গৃহীজীবনের সম্পর্কে তিনি আমার মায়ের কাকা ছিলেন। তিনি আমাদের মামাবাড়ি নিয়ে ঠাট্টা করে বলতেন, ‘চানগাঁ / হেয়ালর গু দি পান খা।’ আমরা শুনে হেসে দিতাম। হেয়াল মানে শেয়াল। চানগাঁ মানে চাঁদগাঁও। এরকম কিছু চর্চা চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকাকে নিয়ে প্রচলিত ছিলো। যেমন : বাঁশখালি বানান করতে দিয়ে বলতো, বাঁশের গিরা / তেলইনের কালি : বাঁশখালি। তেলইন মানে এলুমিনিয়ামের পাতিল। আবার পটিয়া বানান করতে গেলে বলে, কঁঅলর গু / পোঁদের টিয়া : পটিয়া। কঁঅল মানে কোয়েল। এরকম হেঁয়ালিগুলো আসলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা এলাকাকে পচানোর একটা রসালো কৌশল ছিলো।
দিদিমার বাড়িতে একটা নিবিড় গাছপালাপূর্ণ এলাকা ছিলো, যাকে বলা হতো ঘোনা। এর পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা খাল। তাতে জল ছিলো যতো তার চেয়ে বর্জ্য ছিলো বেশি। একদিন এই ঘোনায় গ্রামের অন্য ছেলেদের সাথে খেলতে খেলতে আমার সন্ধ্যা হয়ে যায়। সময়মত ঘরে না ফেরায় দিদিমা আমাকে খুঁজতে বের হলেন। খুঁজে পেয়ে বুড়ি একটু ঝালও ঝাড়লেন। মাঝে মাঝে তিনও ঘি দিয়ে বড়ো বড়ো শিম রাঁধতেন, আলু ভাজির মতো কুচি কুচি করে। একে মৌফুলি শিম বলতো। খেতে বসলে নাকে তার সুঘ্রাণটাই ছিলো বেশ। রান্না করতে গেলে দিদিমা তরকারিতে টেস্টিং সল্ট ব্যবহার করতেন। এই টেস্টিং সলটের নাম ছিলো আজিনা মোটো। এটা মনে হয় বার্মা থেকে আসতো। দিদিমার এই টেস্টিং সল্টপ্রীতি বার্মা থেকেই তৈরি। হতে পারে, দাদুই তা শিখিয়েছিলেন। দিদিমার হাতে ফরাস শিমের রান্নাও বেশ মজাদার ছিলো। একে আজকাল কিডনি বিন বলে। আজকের ডিজিটাল রান্নাঘরের যুগে এর বিচিকে বলে রাজমা। আর আমরা জানি ‘ফরাস শিমের বিচি’ বলে। দিদিমার কোমড়ে একটা খইলতা চিলো। খইলতা হলো ছোট কাপড়ের তৈরি টাকার থলি যা কোমরে লুকোনো থাকতো। দড়ি টানলে মুখ বন্ধ হয়ে যেতো আর দড়ি শিথিল করে মুখ খোলা হতো। আধুনিক নারীদের বটুয়া মনে হয় আগেকার নারীদের খইলতার বিবর্তিত রূপ। তিনি আমাকে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বের হলে বড়ুয়া পাড়ার মুখে কল্যাণ মামার চায়ের দোকান থেকে পুয়া পিঠা কিনে খাওয়াতেন। মার দিদিমা তাঁর গ্রামের মহিলা সমিতির নেত্রী ছিলেন। সামনে থেকে সংগঠনকে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি মুষ্টিভিক্ষার চাল সংগ্রহে বের হতেন। বৌদ্ধ বিহারের কঠিন চীবর দানের সময় তাঁর একটা উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব থাকতো। তিনি জাঁদরেল নেত্রী ছিলেন। দু হাত পেছনে দিয়ে বেশ রাশভারী ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি গ্রামের পথে হাঁটতেন। বড়ো হয়ে আমি আমার দিদিমার মুখচ্ছবিতে কবি কামিনী রায়ের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাই। তাঁর কাছে থাকাকালীন তিনি গ্রামের বাইরে কোথাও গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, আমি যাবো কি না। প্রথমে না করতাম। কিন্তু পরে তিনি না থাকলে আমি একা থাকবো ভেবে বলতাম ‘যাবো’। শেষ মুহূর্তে বলার কারণে তিনি রুষ্ট হয়ে সাথে নিয়ে যেতেন। তবে যেতে যেতে তাঁর চিত্ত হৃষ্ট হয়ে যেতো।
আমার চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার দক্ষতা তৈরিতে আমার দিদিমার ভূমিকা প্রগাঢ়। তখন আমার ছোটমামা থাকতেন ওমানে। তাঁকে চিঠি লেখানোর জন্যে আমাকে নিয়ে বসতেন। মনে হতো মহাভারত লিখতে মুনি ব্যাসদেব আর গণেশ বসেছে একসাথে। তিনি কঠিন কঠিন আঞ্চলিক শব্দে ডিকটেশন দিতেন। সেই আঞ্চলিক শব্দগুলো প্রমিত ভাষায় অনুবাদ করতে আমার বেশ বেগ পেতে হতো। দেরি হলে মাঝে মাঝে ঘেটঘেটি জুটতো কপালে। ঘেটঘেটি মানে বিরক্তির বকা। তবে বেশিরভাগই প্রশংসা জুটতো। বাক্য নির্মাণ পছন্দ হলে তিনি বলতেন, হ্যাঁ অ নাতি, বঅর ভালা অইয়ে। আমার বাবার ভয়ে তিনি যেদিন আমার ইঞ্জেকশন মারা শেষে বাড়ি ফেরার সময় হলো, সেদিন চুল কাটার সেলুনে নিয়ে গিয়ে মাথা ছাঁটিয়ে দিয়েছিলেন।
ঊনিশশো একানব্বইয়ের ঘূর্ণিঝড়ের সময় দিদিমা শহরে আমাদের বাসায় ছিলেন। তখন ঘূর্ণিঝড়টা বেশ শক্তিশালী ছিলো। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিলো সুনামি। সুনামিকে তখন এলাকায় বলা হতো জলকম্প। কর্ণফুলি নদী হতে এক একটা ঢেউ দশ-বারো ফুট উঁচু হয়ে লোকালয়ে আছড়ে পড়েছিলো। হাওয়ায় ছিলো আগুনো হিংস্রতা। গাছের পাতা পুড়ে বাদামী হয়ে যায়। বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি পড়ে রাস্তা আটকে যায়। গাড়িঘোড়া বন্ধ ছিলো। বিদ্যুৎ ছিলো না বেশ কয়েকদিন। জায়গায় জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে যায়, তার ছিঁড়ে যায়। পুরো শহর-গ্রাম হয়ে যায় তাণ্ডবের ভয়াবহ পরিণাম। আমার দিদিমা তখন বাড়িওয়ালি জমিদার। তাঁর দু-তিন ঘর ভাড়াটিয়া ছিলো। দিদিমা খবর পেলেন, তারা খাবার পানি সংকট ও ঘরের চাল উড়ে যাওয়ায় অনিরাপত্তায় ভুগছেন। তাঁকে বাড়িতে যেতে হবে। কে নিয়ে যাবে? তখন আমি কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র। আমার ওপর অর্পিত হলো এ মহান দায়িত্ব। রিকশা চড়ে, বেবিট্যাক্সি চড়ে, কখনও হেঁটে হেঁটে ভেঙ্গে ভেঙ্গে আমরা আইয়া-নাতি (আইয়া মানে দিদিমা) পথ পাড়ি দিলাম ঘূর্ণিঝড়ের পরেরদিন। যেখানে বড়ো গাছের গুঁড়ি পড়ে পথ আটকে আছে, সেখানে বুড়িকে কোলে নিয়ে পার করালাম। আমার দিদিমা শারীরিকভাবে অতিশয় হাল্কা ওজনের মানুষ ছিলেন। তাঁকে কোলে করে দুর্গম পথ পাড়ে দিতে আমার তেমন বেগ পেতে হয়নি। যাওয়ার পথে বেশি কষ্ট হয়েছিলো বাদুরতলা আরাকান রোডে। ওখানে ধ্বংসলীলা বেশি ছিলো। বহু কষ্টে সেদিন আমার দিদিমা পৌঁছালেন তাঁর নিজ বাড়ি। বাড়িতে পৌঁছেই তাঁর ব্যস্ততা শুরু। মোটামুটি অল্প সময়েই তাঁর ও ভাড়াটিয়াদের ক্ষতিগ্রস্ত ঘর তিনি সংস্কার করে ফেললেন।
আমার দিদিমার তেমন কোনো কঠিন রোগ ছিলো না। শুধু ক্রনিক ডিসেন্টেরি ছিলো। ঊনিশশো বিরানব্বই সালে দিদিমা পরকালে পাড়ি জমান ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে। দিদিমার এই প্রয়াণ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণকালীন অবস্থার মতোই মনে হলো আমার কাছে। বুদ্ধও চুন্দ স্বর্ণকারের কাছে আহারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হন। আমার দিদিমাও দীর্ঘদিন রোগে না ভুগে ডায়রিয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমি চিকিৎসক হওয়ার পরে বুঝতে পারি, দিদিমা আসলে ডায়রিরাধর্মী আইবিএস (ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম)-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন। দিদিমার প্রয়াণে আমাদের একমাত্র আদরের বটচ্ছায়াটিও হারিয়ে গেছে কালের অন্তরালে। (চলবে)