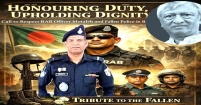প্রকাশ : ১৭ নভেম্বর ২০২৩, ০০:০০

রাষ্ট্র যেহেতু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সেহেতু রাজনীতি দেশ বা রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড বা পিলার। আর রাজনীতিবিদরা তার কারিগর বা পরিচালক। কিন্তু রাজনীতিবিদদের স্থান ব্যবসায়ীরা দখল করে নেয়--এটাই এখন সেই যুগ। রাজনীতিবিদদের জন্যে রাজনীতি কঠিন কিংবা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, যা থেকে আদৌ মুক্ত হতে পারবে কিনা? তবে সেটা সময়ই বলে দিবে। রাজনীতি যেমন অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে, ঠিক তেমনি অর্থনীতিও রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।
অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. ল্যাস্কীর মতে, ‘অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাদের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত দেখা যায় তারাই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন।’ কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাই এর ব্যতিক্রম নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিংবা রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্থনৈতিক জীবনধারাকে প্রভাবিত করে এবং তারা রাজনৈতিক উপাদানের প্রভাব দিয়ে শ্রেণীস্বার্থ কিংবা অর্থনৈতিক স্বার্থ আদায় করে থাকে।
আমাদের দেশে রাজনীতির পিলার এখন আমলা আর ব্যবসায়ীদের দখলে। ফলে রাজনীতিবিদরা কোণঠাসা অথবা নির্জীব-জীবন্ত প্রায়। এরই ফলস্বরূপ আশঙ্কাজনক হারে জাতীয় সাংসদ সংখ্যা বাড়ছে ব্যবসায়ীদের। তারপরে দেখা যাচ্ছে আমলাদের সংখ্যাধিক্য। কিন্তু বলতে পারেন, একজন ব্যবসায়ীও এদেশের মানুষ ও নাগরিক। তারও অধিকার আছে সাংসদ হওয়ার এবং রাজনীতি করার। তাহলে অসুবিধা কোথায়? আরও বললে বলতে পারেন, একজন সাংসদের প্রধান কাজ কী? প্রকৃত পক্ষে মোটা দাগে সাংসদের কাজ চারটি। প্রথমত ও প্রধানতম কাজ হলো, আইন প্রণয়ন করা, দ্বিতীয়ত, জাতীয় এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্কমূলক আলোচনা, তৃতীয়ত, সরকারের আয়-ব্যয় ও বাজেট অনুমোদন, চতুর্থত, সংসদীয় কমিটিগুলোর মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।
একাদশ (বর্তমান) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীদের পেশা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক) সংগঠনটি বলেছে, শপথ নেয়া সাংসদদের ১৮২ জনই (৬১ দশমিক ৭ শতাংশ) পেশায় ব্যবসায়ী এবং টিআইবি’র এক গবেষণা বলছে, একাদশ (বর্তমান) জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে ২২তম অধিবেশনে (জানুয়ারি ২০১৯ থেকে এপ্রিল ২০২৩) আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন সরকারি ও বিরোধীদল মিলে গড়ে ২৫ জন আইনপ্রণেতা, যা মোট সংখ্যার মাত্র ৭ দশমিক ১ শতাংশ। তাই বলতে হয়, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অথবা নিজেদের প্রধান কাজের ক্ষেত্রে যদি সাংসদরা আইন প্রণয়নে দুর্বলতা কিংবা সময় ও শ্রম না দেওয়ার কারণে ভূমিকা পালন করতে না পারেন, তাহলে কেন তারা সাংসদ হতে চাচ্ছেন? আর প্রায় ৬২ শতাংশ সদস্যই ব্যবসায়ী কেন? তাদের প্রধান কাজ যদি না পারেন কিংবা না করবেন তাহলে ব্যবসায়ীদের মাঝে আইনপ্রণেতা হওয়ার এতো প্রবণতা কেন? এ পদের কোনো নির্বাহী ক্ষমতাও নেই। আইন প্রণয়নের বাইরে তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে সেটাও সংসদসংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে সাংসদরা নির্বাহী বিভাগকে উপদেশ বা পরামর্শই দিতে পারেন। সরকারের যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বা কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাদের নয়। এ দায়িত্ব নির্বাহী বিভাগের। আইন প্রণয়ন বা সংসদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সাংসদের প্রধান দায়িত্ব হলেও সেই কাজটিতেই তাদের আগ্রহ কম। অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নে তাদের তেমন ভূমিকা রাখতে দেখা যায় না। যার কারণে অনেক ক্ষেত্রে কয়েক মিনিটে বড় বড় আইন পাস হতে দেখা যায়।
বললে বলতে পারেন, যে কোনো পেশার মানুষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। জনপ্রতিনিধিও হতে পারেন। এটি এককথায় তাদের অধিকার। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, কোনো নির্দিষ্ট পেশার মানুষের রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে ধাপগুলো আছে, সে ধাপগুলোয় উল্লেখযোগ্য অবদান না রেখে সরাসরি সাংসদ হওয়ার আগ্রহ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া এবং সাংসদ হতে পারাটাও। এটাও দেখা যাচ্ছে, ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বা সাংসদ হচ্ছেন না। ব্যবসায়ীরা সাংসদসহ রাজনৈতিক অঙ্গনকে প্রায় তাদের দখলীভূত করেছেন। তারা এখন রাজনীতিটাকে ব্যবসা তথা বিনিয়োগে পরিণত করেছেন। বিনিয়োগের মাধ্যমে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে নানা সুবিধা অর্জন করা যায়। যে বিনিয়োগ করা হয় তার তুলনায় অনেক বড় বড় উপযোগিতা পাওয়া যায়। এটি এক ধরনের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার কারণে রাজনীতিতে ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। তাদের (ব্যবসায়ী) রাজনীতি কতোটুকু জনকল্যাণমূলক সেটি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। সাংসদ হিসেবে তাদের যেসব দায়িত্ব রয়েছে, সেগুলো যথাযথভাবে পালন করার দৃষ্টান্ত খুবই কম।
পার্লামেন্টারী ফর্ম অব গভর্নমেন্ট সিস্টেমে সরকারের কাঠামোর দিক থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আইন বিভাগের সদস্য হিসেবে সাংসদের নির্বাহী দায়িত্ব পালনের কোনো সুযোগ নেই। এ দায়িত্বটা কেবল নির্বাহী বিভাগেরই। তবে মন্ত্রিসভার সদস্যরা একইসঙ্গে আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের সদস্য হওয়ায় তাদের ক্ষেত্রে দ্বৈত ভূমিকার সুযোগ থাকে। নিয়ম অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কাজ স্থানীয় সরকার ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব। সাংসদরা শুধু পরিকল্পনায় থাকেন, বাস্তবায়নে তাদের ভূমিকা নেই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, সরকারের বড় বড় প্রকল্পে তাদের সুপারিশ এবং হস্তক্ষেপ থাকে। কোন্ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কোন্ কাজ পাবে, কে পাবে না, সেগুলো ঐসব প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার চেয়ে সাংসদের সুপারিশ কিছু ক্ষেত্রে বেশি গ্রহণযোগ্য। পণ্যের বাজারে সিন্ডিকেট গড়ে তুলে যেসব ব্যবসায়ী বাজার অস্থিতিশীল করছেন তাদের রক্ষায় সাংসদ বা মন্ত্রীদের এগিয়ে আসতে অনেকটা দেখা যায়। ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ভাঙ্গা অসম্ভব বলেও মন্তব্য করেছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে সাংসদ হওয়া একজন মন্ত্রী।
এখন যারা সুস্থ ও আদর্শিক ধারার রাজনীতির ধারক-বাহক তারা ঐসব ব্যবসায়ীর কারণে কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছেন। যার ফলে রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্যে অনেক রাজনীতিবিদ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার জন্যে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ব্যবসার সাথে জড়িত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। যেসব ব্যবসায়ী রাজনীতিতে আসছেন ক্রমেই তাদের প্রভাব বাড়ছে, রাজনীতিকে পুঁজি করে তারা স্বার্থ হাসিল করছেন। যেটি দীর্ঘমেয়াদে দেশের গণতন্ত্রের জন্যে হুমকি তৈরি হবে। এছাড়া অনেক সময় রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ বেশি গুরুত্ব পায়। ফলে এটি দেশ ও গণতন্ত্রের জন্যে ভাল ম্যাসেজ নয়।
অন্য দিকে চিন্তা করলে দেখা যায়, ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক কারণে নানারকম ক্ষমতা ভোগ করেন সমাজ ও রাষ্ট্রে। ভিআইপি, সিআইপিসহ বেশ কিছু ক্যাটাগরিতে তাদের সুবিধা ও সম্মান দেয় রাষ্ট্র। এতো কিছুর পর যখন একজন ব্যবসায়ী সংসদে অধিষ্ঠিত হন, তখন তার নির্বাচিত আসনের রাজনৈতিক নেতারা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। আর ঐ ব্যবসায়ীর ক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে কখনো কখনো ঐসব সাংসদ হয়ে উঠেন অপ্রতিরোধ্য। এবং অনেক ক্ষেত্রে আইন-কানুন বিধিবিধান ভঙ্গ করার প্রবণতা দেখা যায়। একই সঙ্গে তারা প্রভাব খাটিয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা বলয় সৃষ্টি করেন।
রাজনীতিবিদ না হওয়ায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদের যোগাযোগ থাকে অনেক কম। তাই যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তারা শ্রেণী স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না। আর পারেন না বলেই রাষ্ট্র বা জনগণের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ক্ষমতা তখন এককেন্দ্রিক তথা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। এবং প্রকৃত রাজনীতিবিদরা হয়ে যান অসহায়। এতে করে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের গণতন্ত্র এবং দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাতীয় স্বার্থ। অপরদিকে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কম থাকায় ব্যবসায়ী থেকে সাংসদ এবং মন্ত্রী হয়ে যাওয়া এসব নেতার পক্ষে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতির টেবিলে দেশের স্বার্থ নিয়ে কথা বলার যোগ্যতাও থাকে না খুব একটা। তখন আঞ্চলিক রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্র বড় ধরনের ক্ষতিতে পড়ার শঙ্কা দেখা দেয়। যেটি একটি প্রজন্ম, একটি সমাজ ও একটি দেশকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারে।
শেষান্তে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান থাকলো, আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রকৃত রাজনীতিবিদ এবং দলের ত্যাগী রাজনীতিবিদের প্রাধান্য দিয়ে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্যে মনোনয়ন প্রদান করবেন। অন্যথায় দেশের কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র, রাজনীতি এবং সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
অধ্যাপক মোঃ হাছান আলী সিকদার, সভাপতি, চাঁদপুর জেলা জাসদ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা; চাঁদপুর জেলা শিক্ষক নেতা; সমাজ ও রাজনীতি বিশ্লেষক।