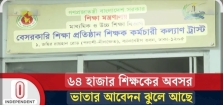প্রকাশ : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৪৯
এসএসসিতে পাঠদান ও পরীক্ষাকাঠামোতে যে সংস্কার জরুরি

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এসএসসি পরীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ১০ বছরের শিক্ষার একটা জাতীয় স্বীকৃতি। নব্বইয়ের দশকেও এই পরীক্ষায় গড়ে ৪০-৪৫ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করত। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ফেল করত। সেটাই ছিল অনেকটা প্রতিষ্ঠিত ও স্বাভাবিক চিত্র।
কিন্তু তখনো সরকার এই ব্যাপক ফেলের সমাধানের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি, কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি; বরং শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, স্কুলে স্কুলে রাজনৈতিক প্রভাবযুক্ত কমিটি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার গুণগত মানকে আরও খারাপই করেছে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণেও টেকসই ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।
বিগত এক দশকে সরকারি নির্দেশে, এসএসসিতে পাসের হার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। ৮০-৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী ‘পাস’ করছে, এমন এক বাস্তবতায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। যেখানে প্রকৃত যোগ্যতার মূল্যায়ন অনেক সময়েই উপেক্ষিত হয়েছে। পাস করা শিক্ষার্থীরা কতটুকু জেনে পাস করছে, সেসব বিষয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে।
এই পরিপ্রেক্ষিতে এ বছরের এসএসসি ফলাফল এক বিস্ময় জাগিয়েছে। এ বছর প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। পাস করেছে গড়ে ৬৮ শতাংশ শিক্ষার্থী। বাকি ৩২ শতাংশ, তথা ৬ লাখ শিক্ষার্থী ফেল করেছে। ২০০০ সালের আগেও দেশে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই ছিল ৬-৭ লাখ; অর্থাৎ শুধু ফেল করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা একসময়কার পুরো দেশের পরীক্ষার্থীর সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এটাকে আমি সংকট হিসেবেই দেখি।
‘ম্যাট্রিক ফেল’, বাংলাদেশে এটি একটি ভয়ংকর সামাজিক ট্যাবু। যারা ফেল করেছে, তাদের মানসিক অবস্থা কল্পনা করলেই বোঝা যায়, এই বয়সে তারা কতটা ভেঙে পড়ে। অনেকেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। কেউ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। আবার কেউ চিরতরে হারিয়ে যায় কর্মসংস্থানের প্রধান স্রোত থেকে। অনেকেই সমাজের বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। এদের মধ্যে নারী শিক্ষার্থীদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। প্রশ্ন হলো, এই ব্যর্থতা কি শুধুই শিক্ষার্থীর?
একদমই না। একজন শিক্ষার্থী ফেল করলে তার দায় কেবল তার নয়; বরং সেটি প্রতিষ্ঠানের, শিক্ষকের, পাঠ্যক্রমের এবং গোটা শিক্ষাব্যবস্থার। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রাকৃতিক মেধা, মনোযোগ, আগ্রহ সমান না হতেই পারে; কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কাজই হলো তাকে নির্ধারিত একটি মানদণ্ডে নিয়ে আসা। তাই ফেল করা শিক্ষার্থীদের দোষ না দিয়ে, স্কুল এবং শিক্ষানীতির সীমাবদ্ধতা নিয়েও ভাবা জরুরি। অপর দিকে সঠিক যাচাই ছাড়া পাস করানোও সমানভাবে ক্ষতিকর এবং অগ্রহণযোগ্য। এর ফলে সমাজে ‘দুধ’ আর ‘ঘি’-এর দাম এক হয়ে যায়। সবাই পাস করে, কিন্তু কে কতটা যোগ্য, তা আর বোঝা যায় না। যোগ্যতা ও অযোগ্যতার মধ্যে বিভাজন মুছে যায়।
এই বিপর্যয় থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ তুলে ধরছি।
প্রথমত, জাতীয় বোর্ডভিত্তিক একক পরীক্ষার ধারণা নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। অঞ্চলভিত্তিক পরীক্ষা চালু করার কথা ভাবা যেতে পারে, যেখানে স্থানীয় বাস্তবতা ও শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন হবে।
আমেরিকার হাইস্কুল ডিপ্লোমা সিস্টেম একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে। সেখানে শিক্ষার্থীরা একাধিক ধরনের ডিপ্লোমা পায়, যা মূলত প্রতিটি শিক্ষার্থীর মেধা, আগ্রহ, দক্ষতা ও লক্ষ্য অনুযায়ী তৈরি। একইভাবে, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেও বহুস্তরীয় সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা চালু করা যেতে পারে।
জনবহুল দেশে অবশ্যই কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকবে, তবে সব শিক্ষার্থীকে একই পর্যায়ের পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করাও অকার্যকরই। চলমান পদ্ধতি বহু যুগ ধরে প্রচলিত, কিন্তু সবার জন্য সমাধানযোগ্য হয়ে ওঠেনি। এত বিপুল শিক্ষার্থী প্রাকৃতিকভাবেই একই মেধা, একই যোগ্যতা, একই আগ্রহ নিয়ে বেড়ে উঠবে না। সুতরাং তাদের সবাইকে একই প্রশ্নের পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করাই-বা কতটুকু যৌক্তিক!
ক্লাসের পাঠদান কখনোই কার্যকর হয়ে উঠছে না। অথচ ক্লাসের পাঠ ক্লাসেই শিক্ষার্থীরা বুঝে নেওয়ার কথা। শিক্ষার্থীদের তুলনায় শিক্ষকদের অনুপাত কম। এটা বিবেচ্য। কিন্তু ক্লাসের পাঠদানেও অনেক শিক্ষকের আছে অনভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণের অভাব ও অনাগ্রহ; বিশেষ করে গ্রামের স্কুলগুলোতে।আরও একটি বড় সংস্কার প্রয়োজন পরীক্ষা কাঠামোতে। বর্তমানে জাতীয় পরীক্ষায় ১০-১২টি বিষয়ের ওপর পরীক্ষা নিতে হয়, যা শিক্ষার্থীদের ওপর বেশ চাপ তৈরি করে। বোর্ড পরীক্ষায় যদি সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত না করে, কিছু নির্ধারিত বিষয়ে নেওয়া হয়, তবে মানসিক চাপ কমবে। শিক্ষার্থীরা ভালো করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া যারা ফেল করে, তাদের পুরো বছর অপেক্ষা না করে শুধু ফেল করা বিষয়ের ওপর দ্রুত পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া উচিত। একজন শিক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য বাইরে রেখে দেওয়া মানে, তার মানসিক শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং ভবিষ্যৎ সবকিছুকে নষ্ট করে ফেলা। এটি একেবারেই অমানবিক ও অগ্রহণযোগ্য।
নরওয়ে ও জার্মানিতে শিক্ষার্থীরা যদি একাডেমিক পর্যায়ে ভালো না করে, তাহলে তাদের জন্য কারিগরি বা ভোকেশনাল ট্র্যাক দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পেশাগত দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং একে সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে ছোট করে দেখা হয় না। জার্মানিতে এটা ‘ডুয়াল ট্রেনিং সিস্টেম’ নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একই সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ শেখে এবং তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে, যার ফলে তারা শিক্ষাজীবন থেকে কর্মজীবনে নির্বিঘ্নে প্রবেশ করতে পারে। বাংলাদেশেও একটি বিকল্প ও মানবিক শিক্ষাকাঠামো গড়ে তুলতে পারি, যেখানে ফেল মানেই শেষ নয়, বরং নতুন পথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ।
অবশেষে, এই বিপুলসংখ্যক ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে যেন শিক্ষা বা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ংকর অভিজ্ঞতা তৈরি না হয়, সে জন্য কর্মমুখী শিক্ষা, নিম্নমানের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, এবং বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা জরুরি। আমাদের স্কুলগুলোতে শুধু পাস নয়, শেখা ও গড়ে ওঠার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ছয় লাখ ছেলেমেয়ে যেন হারিয়ে না যায়। পরীক্ষায় ফেল শুধু তাদের ব্যর্থতা হিসেবে না দেখে, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাব্যবস্থাও যেন উদ্বিগ্ন হয়। পরিবর্তনের জন্য কাজ করে। এটাই হোক আমাদের দায়িত্ব।