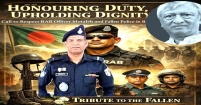প্রকাশ : ২০ আগস্ট ২০২৪, ০০:০০
অন্তর্বর্তী সরকার শাসন-শোষণ ও বৈষম্য প্রক্রিয়ার ঊর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্র সংস্কার করতে পারবে?

বাংলাদেশের নবীন প্রজন্ম এ দেশটিকে উদ্ধার করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রাজপথে নেমে এসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান তথা গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। তারা অসম সাহসী ও বীর এক প্রজন্ম। এ প্রজন্মকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু এর জন্যে পাশাপাশি তাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন তাদের উদ্যোগ দিশা না হারায়। শেখ হাসিনাকে হটিয়ে এদেশের মানুষের প্রত্যাশার পারদ এখন অনেক উপরে। মানুষ দৃশ্যমান প্রাপ্তিযোগ চাইবে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার ঘ্রাণ পেতে শুরু করেছে। নতুন নির্বাচনের জন্যে সরকারকে চাপ দিবে। ক’দিন পরই শুরু হবে মিটিং-মিছিল এবং নানামুখী চাপ। বিভিন্ন ধরনের দাবি-দাওয়ার ফিরিস্তি লম্বা হতে থাকবে। এই ধারায় যদি আমরা যাই, তা হলে না হবে রাষ্ট্র সংস্কার, না হবে পরিবর্তন।
গণঅভ্যুত্থানের চারদিন পর ড. ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকারের প্রধান কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে শুধু একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান নয়। এই সরকারের প্রধান অঙ্গীকার রাষ্ট্র সংস্কার, রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত। কোটা সংস্কার আন্দোলন রাষ্ট্র সংস্কারের আন্দোলনে পরিণত হয়। এরপরই শুরু হয় গণবিস্ফোরণ। কাজেই অতীতের তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলোর সঙ্গে বর্তমান অন্তর্র্বতী সরকারের মৌলিক পার্থক্য আছে। ১১ জানুয়ারি ২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া বাংলাদেশে অতীতে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলো গঠিত হয়েছিল, সেই সব সরকারের প্রধান কাজ ছিল একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা। ১/১১-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পাশাপাশি রাজনীতি শুদ্ধিকরণের চেষ্টা করে। কিন্তু এবার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন বললে অত্যুক্তি হবে না।
স্বভাবত প্রশ্ন উদিত হয়, রাষ্ট্র সংস্কার আসলে কী? রাষ্ট্র কাঠামোর মেরামত-স্বরূপ পথটাই বা কী? এখন এ সম্পর্কে নানাজন যে যার মত মতামত দিচ্ছেন। শিক্ষক নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকেও এই সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্র যেন নিপীড়নমূলক না হয়, সেটাই রাষ্ট্র সংস্কারের মূল আকাঙ্ক্ষা। রাষ্ট্র যেন বৈষম্যহীন হয়, সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র সংস্কারের দাবি। কিন্তু সেটা কীভাবে করা যেতে পারে? তা এখনও স্পষ্ট নয়।
এবারের আন্দোলনে যে চমৎকার স্লোগানের উদ্ভব হয়েছিল, তা হচ্ছে ‘বৈষম্য মানি না’। কিসের বৈষম্য এটি না বলতে পারলে কিন্তু বৈষম্য ধারণাটি মূর্ত হয় না।
আমরা সাধারণত জানি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্য হচ্ছে সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য। সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নানা ধরনের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের বৈষম্য। এছাড়া জেন্ডার-বৈষম্য, ধর্মীয়-বৈষম্য, জাতিতে জাতিতে বৈষম্য, শ্রেণীগত বৈষম্য প্রভৃতি। এগুলো শত শত বছর ধরে সমাজে বিদ্যমান এবং মানবজাতির সর্বজনীন লক্ষ্যই হচ্ছে সভ্যতার অগ্রযাত্রার মাধ্যমে তা ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা।
এতো আত্মত্যাগের পর আবার যদি কোনো নতুন সাম্রাজ্যবাদ বা মৌলবাদের আদর্শপুষ্ট ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক শক্তি বা আরো বৈষম্যপূর্ণ কোনো সরকার শূন্য আসনে এসে বসে, তাহলে ছাত্রসমাজ এবং জনগণের এ গৌরবময় আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেটি নিশ্চয় ছাত্র-জনতা আদৌ চাইবেন না। তাই রাজনৈতিক প্রশ্নটিকে কিছুটা হলেও বিবেচনায় ছাত্র-জনতার না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিদ্যমান ডানপন্থী বা বামপন্থী কিংবা ধর্মভিত্তিক প্রতিযোগী রাজনৈতিক দলগুলো কি এখন পর্যন্ত ক্ষমতায় গিয়ে কে কী করবেন এ রকম কোনো কর্মসূচি দিয়েছে? আন্দোলনের ফসল হিসেবে আজ যে অন্তর্র্বতীকালীন সরকার তৈরি হয়েছে, তাদেরও কি কোনো ১০০ কিংবা ২০০ দিনের ইতিবাচক কর্মসূচি বা পরিকল্পনা আছে? এমনকি তরুণদের মধ্যে যারা অন্তর্র্বতী সরকারে আছেন তাদের কাছে কি নিজেদের বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান এবং বৈষম্যহীন-সমাজ প্রতিষ্ঠার কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি আছে? এখন পর্যন্ত তাদের দাবিগুলো তাদের ভাষায় ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে তাড়িয়ে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিলোপ বা যে কোনো উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্য, সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন, মৌলবাদী ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ববাদ বা রাষ্ট্রধর্ম মতবাদ অথবা ব্লাসফেমি আইন ব্যবহার করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তথাকথিত ‘নাস্তিক’ বা ‘আহমদিয়া’ ট্যাগ লাগিয়ে নিপীড়ন ইত্যাদি প্রবণতায় রয়েছে মৌলিক বৈরিতামূলক বিরোধ। কিন্তু এরই মধ্যে এসব প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে কি তারা সচেতন? যদি এ ব্যাপারে তারা সচেতন হন তাহলে তাদের এবং তাদের সরকারের উচিত বিলম্ব না করে এ বিষয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা।
এখন কথা হলো, শিক্ষার্থীদের আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে সফল হয়েছে। তাদের চোখে-মুখে যে ক্ষোভ ও প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠেছিল তা প্রশমন হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন। তার লক্ষণ এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে। ঝানু রাজনীতিবিদদের বিপরীতে আবেগের বশে সাময়িক জয় পাওয়া গেলেও আসল চ্যালেঞ্জ সামনে। পুলিশ নিজেদের জানমাল রক্ষায় সাময়িক নিষ্ক্রিয় থাকবে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যান্য বাহিনী তো মাঠে আছে। তারপরও সরকার পতনের দিন বিকেলেই যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে তা ছিল বড়ো ধাক্কা। বাধাহীনভাবে সবাইকে গণভবনে ঢুকতে দেয়া কি অনিবার্য ছিল? তাদের তো সংসদ ভবনের ওপর ক্ষোভ ছিল না। তাহলে সেটা অরক্ষিত রেখে অরাজকতা সৃষ্টির সুযোগ করে দিল কারা? পাশাপাশি বিরোধী নেতা-কর্মী ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঘরবাড়ি বা উপাসনালয়ে হামলা হতে পারে--এমন অনুমান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হলো না কেন? দীর্ঘ দেড় দশক নানাভাবে অত্যাচারিত ও সুবিধাবঞ্চিত হওয়ায় ক্ষমতাসীন অনেকের ওপর রাগ-ক্ষোভ থাকবে এবং সুযোগ পেলে তাদের ঘরবাড়িতে আক্রমণ হবে সেটা অনুমান করা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে বিষয়গুলো দেখার কেউ নেই। সাধারণ মানুষ সেটা বুঝলেও নীতিনির্ধারকগণ কেন সেটা বুঝতে পারলেন না এমন অনেক প্রশ্ন সামনে আসা শুরু হয়েছে। আসলে ছাত্র-জনতাকে নেতৃত্ব দেয়া আর ঝানু রাজনীতিক ও আমলাদের কৌশলকে পাশ কাটিয়ে সঠিক পথে থাকা সহজ নয়। তাই সামনের পথ অতি বন্ধুর। কেননা অসৎ আমলা-ব্যবসায়ী- রাজনীতিবিদ সবাই নিজ নিজ স্বার্থে সংঘবদ্ধ। তারা গোষ্ঠীস্বার্থ সিদ্ধিতে দেশ বা জনগণের কল্যাণকে সহজেই জলাঞ্জলি দিতে পারে।
বেশির ভাগ তরুণ যে দলই করুক না কেন বা দলের প্রতি যে প্রত্যাশাতেই তারা সমবেত হন না কেন, বাস্তবে সমস্যা সমাধানের একটি সুনির্দিষ্ট রূপকল্প তারা কিন্তু তাদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত পাননি। একটি বৈষম্যহীন সমাজে প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে কাজ এবং কাজ অনুসারে পারিশ্রমিকসহ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার জন্যে সমাজের কী ধরনের মৌলিক রূপান্তর প্রয়োজন হবে তা নিয়ে তরুণদের ও প্রতিযোগী দলগুলোর ধারণা আজও অস্পষ্ট। প্রতিযোগী আদর্শগুলো নিয়েও খোলামেলা ধারণা অনেকের নেই এবং জাতির কাছে উন্মোচিত নয়।
মোট কথা, যারা নির্যাতন, গুম-খুনের সঙ্গে জড়িত, যারা লুণ্ঠন করেছে, অর্থ পাচারকারী, নির্যাতনকারী তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু ভিন্ন মতের অভিযোগে কাউকে নিগৃহীত করা যাবে না। এটা করা হলে এই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। দুর্নীতিবাজ, চাটুকার, সুবিধাভোগী আর ভিন্ন মতাবলম্বী এক পাল্লায় উঠানো যাবে না। মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মুক্তচিন্তা প্রকাশের সুযোগ বন্ধ করলে আমরা আবার অন্ধকার পথে হাঁটতে শুরু করবো। এজন্যে প্রয়োজন মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন।
আজ রাষ্ট্রব্যবস্থার যে অবস্থা, সে অবস্থায় ছাত্র-জনতার কাঙ্ক্ষিত সংস্কার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে শুধু তাদের আট দফা বা নয় দফা দাবি মানলে তা পূর্ণ হবে না। এজন্যর ‘বৈষম্য’ সমস্যার মূলে প্রবেশ করতে হবে। নির্ভরশীল ও স্বজনতোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনীতি থেকে মুক্ত একটি সমাজভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সর্বাগ্রে কায়েম করতে হবে গণতান্ত্রিক সুশাসন ও তিন বলয় বা এমের (Money, Muscle, Manupulation) প্রভাবমুক্ত সুষ্ঠু নির্বাচনী ব্যবস্থা।
অধ্যাপক মোঃ হাছান আলী সিকদার : সভাপতি, চাঁদপুর জেলা জাসদ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা, চাঁদপুর জেলা শিক্ষক নেতা; সমাজ ও রাজনীতি বিশ্লেষক।