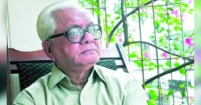প্রকাশ : ২০ মার্চ ২০২৪, ০০:০০
চাঁদপুর : ডেডলাইন ১৯২১

ভারতে চা উৎপাদনের ইতিহাস ১৮৪ বছরের পুরানো। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসামে চা চাষের গোড়াপত্তন করে ১৮৩৯ সালে। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা মূলত চীনের চা-চাষ দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই ভারতে পরীক্ষামূলক চা-চাষের জন্যে চীন থেকে আনা হয়েছিল চা-বীজ, চারা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও চা-চাষে দক্ষ শ্রমিক।১ কিন্তু চীনের শ্রমিকদের সঙ্গে কোম্পানি বেশিদিন কাজ করতে পারেনি। একসময় চীন থেকে শ্রমিক আমদানি বন্ধ করে দেয়া হয়। তাদের বিকল্প হিসেবে কোম্পানি-সংশ্লিষ্টরা চা বাগানে এদেশীয় শ্রমিকদের নিয়োগ দেয়া শুরু করেন। এর মধ্য দিয়ে চা-শ্রমিক হিসেবে ভারতীয়দের যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে চা-চাষের সূচনা হয় ১৮৪০ সালে, চট্টগ্রামে। বাণিজ্যিকভাবে চা-বাগানের যাত্রা শুরু হয় আরও ১৪ বছর পরে, ১৮৫৪ সালে।২ ইংরেজ হার্ডসনের উদ্যোগে পনেরশ একর জায়গা জুড়ে ‘মালনীছড়া চা-বাগান’টির পত্তন করা হয়। পরে হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারেও চা-বাগান করা হয়।
১৯৪০ সালে আসামে বিভিন্ন পদে শ্রমিকরা চা-বাগানের কাজ করত। তাদের জন্য মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করেছিল ব্রিটিশ কোম্পানি। চা-বাগানে নিয়োগকৃত কর্মচারীদের পদগুলো হল : সুপারিনটেন্ডেন্ট (১ জন), ফার্স্ট অ্যাসিসট্যান্ট (১ জন), সেকেন্ড অ্যাসিসট্যান্ট (১ জন), চাইনিজ ব্ল্যাক টি মেকার (১ জন), সহকারী চাইনিজ ব্ল্যাক টি মেকার (১ জন), চাইনিজ টি-বক্স মেকার (১ জন), চাইনিজ ইন্টারপ্রেটার (১ জন), চাইনিজ গ্রিন-টি মেকার (২ জন), চাইনিজ টি-বক্স মেকার (১ জন), চাইনিজ লিড ক্যানিসটার মেকার (১ জন), নেটিভ ব্ল্যাক টি মেকার (২৪ জন), নেটিভ গ্রিন টি মেকার (১২ জন), নেটিভ কার্পেন্টার (১ জন), কুলি সর্দার (১ জন), মাহুত (৪ জন), মাহুত মেইটস (৪ জন), সইয়ারস (৪ জন), ডাক রানার্স (২ জন) এবং দফাদার্স (৪ জন)।৩
বাণিজ্যিকভাবে চা-বাগান স্থাপনের শতবর্ষেও পানীয় হিসেবে চা পূর্ববঙ্গে খুব জনপ্রিয় ছিল না। চা-গবেষক ইসমাইল চোধুরীর তথ্যমতে, ১৯৪৭ সালে এ অঞ্চলে চা উৎপাদিত হত প্রায় ১৮ মিলিয়ন কেজি। রপ্তানি হত ১৫ মিলিয়ন কেজি। ১৯৭১ সালে চায়ের উৎপাদন হয় ৩১ মিলিয়ন কেজি। এ তথ্য থেকে বুঝা যায়, সময়ে সময়ে চায়ের উৎপাদন বেড়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে চা-শ্রমিকের সংখ্যাও বেড়েছে।৪
পূর্ববঙ্গে ১৯৪৭ সালে অঞ্চলে উৎপাদিত চায়ের ৬ ভাগের ১ ভাগ দেশীয়বাজারে রাখা হত। সংখ্যার হিসেব করলে মাত্র ৩ মিলিয়ন কেজি। অন্যদিকে, ইতিহাসবিদ এরিয়া র্যাপোটের তথ্যমতে, ১৮৩০ সালে ব্রিটিশরা প্রায় ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড চা পান করতো। মূলত তারাই এই ভূখণ্ডে চা-কে জনপ্রিয় করেছে। বিশেষ করে ১৯৩০ সালের মন্দায় ভারত থেকে চা রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচতে দেশীয় বাজারে চা বিক্রি করতে কোম্পানিগুলো ব্যাপক প্রচারণা চালায়। প্রচারণার অংশ হিসেবে বিনামূল্যে চা, দুধ ও চিনি বিতরণ করা হয়। এমনকি শিখিয়ে দেয়া হয় চা বানানোর কৌশলও।৫ এভাবেই ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে চা জনপ্রিয় পানীয়তে পরিণত হয়।
২০২১ সালে বাংলাদেশের ১৬৭টি বাগানে চা উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্যমতে, ২০২২ সালে চা উৎপাদিত হয়েছে প্রায় ৯৯.৮২৯ মিলিয়ন কেজি। চা রপ্তানি হয়েছি হয়েছে ০.৭৮ কেজি।৬
২০২১ সালের জরিপ মতে, বাংলাদেশের বাগানগুলোতে ১ লাখ ৪০ হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করেন। যার মধ্যে নারী শ্রমিক ৭০ হাজার ৭৬৯ জন, পুরুষ ৬৯ হাজার ৪১৫ জন। অন্যদিকে চা শ্রমিকদের পরিবার মিলিয়ে পাঁচ লাখের মতো মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত এবং তারা ৯০ ভাগ অবাঙালি। ২০১৪-১৬ সালের তথ্যানুযায়ী, চা-বাগানে প্রায় ৮০টি জনগোষ্ঠী এবং ১৩টি প্রচলিত ভাষা রয়েছে।৭
সময়ের আবর্তনে চা শ্রমিকের সংখ্যা এবং চায়ের উৎপাদন বাড়লেও বঞ্চনা নির্মূল হয়নি। ১৮৪০ সালের শ্রমিকদের বঞ্চনা ও দুঃখের ইতিহাস ২০২২ সালের শ্রমিকদের মতো ছিল না। এই সময়ে এসে চা শ্রমিকদের বঞ্চনা পূর্বের চেয়ে কম হলেও এর ব্যাপ্তি কম নয়। আধুনিকতম সময়ে তারা যেসব স্বাভাবিক সুবিধাবঞ্চিত, তা সমাজে অকল্পনীয়। অথচ চায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের বিকাশে তাদের অবদান অবিস্মরণীয়। তখনও চা বাগানের শ্রমিকরা প্রায়ই তাদের যৌক্তিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করতেন, এখনও শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন।৮ তাদের সংগ্রামের ইতিহাস যেন শেষ হওয়ার নয়।
‘মুল্লুকে চলো’ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট
চা শ্রমিকরা বহুকাল থেকেই ছিল নির্যাতিত-নিপীড়িত। ব্রিটিশ অফিসারদের হাতে অত্যাচারিত হওয়া ছিল নিত্যদিনের বিষয়। মানুষ বা শ্রমিক নয়, তাদের গণ্য করা হত ক্রীতদাস হিসেবে। শ্রমিকরা যে সবসময় নির্যাতন মাথা পেতে নিত, তেমনটি নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি যতই ঘনিয়ে এসেছিলো, ততই শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও প্রতিবাদ বাড়ছিলো। গবেষক ড. রজনী কান্ত দাস লিখেছেন, ‘ইউরোপীয় অফিসারদের লাথি, ঘুসি এবং কুলিদের উপর নানারূপ দৈহিক নির্যাতন প্রায়শই বাগানগুলিতে সংঘর্ষের অবস্থা সৃষ্টি করত।’১ তাঁর হিসেব মতে, আসামের চা বাগানসমূহে কেবল ১৮৯১ সালেই ১০৬টি দাঙ্গাহাঙ্গামার ঘটনা ঘটে।২ বিশ শতকের শুরু থেকে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হচ্ছিল। শ্রমিকরা অনুধাবন করতে সক্ষম হন দাবি আদায়ে সংঘবদ্ধতার বিকল্প নেই। এ কারণে শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। শত শহীদের রক্তে গ্রন্থে অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ লিখেছেন, ১৯২০ সালে শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ৪০, এক বছরের ব্যবধানে ১৯২২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৫-এ।৩
চা শ্রমিকদের মজুরিও ছিল নামমাত্র। ড. চমনলাল তাঁর কুলি- দ্য স্টোরি অব লেবার এন্ড ক্যাপিটাল ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থে লিখেছেন, ১৮৮০-১৯১৪ সাল পর্যন্ত চা বাগানের পুরুষ শ্রমিকরা প্রতিমাসে গড়ে ৬ টাকা ২ আনা ৩ পয়সা, নারী শ্রমিকরা ৪ টাকা ১ আনা ৫ পয়সা এবং শিশু শ্রমিকরা ২ টাকা ১৩ আনা ৭ পয়সা মজুরি পেত। ১৯১৮-১৯১৯ সাল পর্যন্ত চা বাগানের পুরুষ শ্রমিকরা প্রতিমাসে গড়ে ৬ টাকা ৫ আনা ৯ পয়সা, নারী শ্রমিকরা ৫ টাকা ১ আনা ৫ পয়সা এবং শিশু শ্রমিকরা ৩ টাকা ১ আনা ৫ পয়সা মজুরি পেত।৪ ড. দেওয়ান চমনলাল চা শ্রমিকদের বেতন, বোনাস ও অন্যান্য ভাতার হিসেবে ধরে এই গড় মজুরি নির্ধারণ করেন।
১৮৬৩ সালের জুন সংখ্যায় চা শ্রমিকদের ওপর নির্মম নির্যাতনের বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যে প্রকাশ করে সোমপ্রকাশ। নদীয়া জেলার কৃষ্ণপুরের সন্তান রূপচাঁদ বিশ্বাস চা শ্রমিক ছিলেন। তার স্মৃতিচারণের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের সামগ্রিক চিত্রটি অনুধাবন করা যাবে :
চা-করগণ কুলিদিগকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া থাকেন। কুলিদিগকে ১০। ১২ টাকা বেতন প্রদানের কথা বলিয়া কাছাড়ে লইয়া যাওয়া হয়, বাস্তবিকপক্ষে শেষে তাহারা ২।১ টাকার অধিক পাইতে পারে না। কুলিদিগকে সচরাচর যে সকল দ্রব্য আহার করিতে দেয়া হয় তা অতিশয় কদর্য। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তাহা গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুগণেরও আহারযোগ্য নহে। অথচ এই আহারী দ্রব্যের নিমিত্তে কুলিদিগের বেতন হইতে মাসে মাসে দুই টাকা কাটিয়া লওয়া হয়।...আহার ও বাসস্থানের ঈদৃশ অপকৃষ্টতায় কুলিদিগের মধ্যে অনেকেই উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদিগের যথোচিত চিকিৎসা করাও হয় না। যেমন পীড়া হয় অমনি পঁচিয়া গলিয়া মরিয়া যায়। চা-করগণ যে সকল অত্যাচার করেন, তাহার আর বিচার হইতে পারে না।৫
১৮৮৩ সালে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় বলা হয়েছে : ‘আসাম প্রদেশ কুলির বধ্যভূমি, চা-কর ও নীলকর সাহেব বাহাদুর সেই বধ্যভূমির জল্লাদ।’ এমনই ছিলো চা-শ্রমিকদের প্রতি নির্যাতন-শোষণ-রক্তপাতের সংবাদভাষ্য।
অন্যদিকে চা-বাগান মালিকরা কোনো আইনের তোয়াক্কা করতেন না। নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্রীতদাস ও লভ্যাংশ বৃদ্ধির যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করতেন তারা। ১৮৭০ সালে প্ল্যান্টেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী, শ্রমিকদের দিনে ৯ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো এবং ১৬ বছরের কম বয়সীদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না। কিন্তু চা-বাগান মালিকদের কাছে আইন কেবলই কাগজে-কলমে ছিল। কোনো শ্রমিকের চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেও তাকে স্বদেশে ফিরতে দেয়া হত না। কেউ ফিরতে চাইলে তার নামে মিথ্যে অভিযোগ এনে সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হত। চা বাগানে শ্রমিক হত্যার ঘটনাও ঘটত।৬
প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯১৪-১৯১৮) চা-বাগান মালিকরা অভাবনীয় মুনাফা অর্জন করেন। তখন শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি বা অন্য সুবিধা প্রদান করা হয়নি। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পরপর বাগান মালিকরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন। লোকসানের পরিমাণ হ্রাস করতে তারা শ্রমিকদের মজুরির পরিমাণ কমিয়ে দেয়। দৈনিক হিসেবে তাদের নতুন মজুরি নির্ধারণ করা হয় তিন পয়সা।৭ এছাড়া শ্রমিকদের অন্যান্য সুবিধা বন্ধ করে দেয়া হয়।
মূলত শ্রমিকরা পূর্বের মজুরি দিয়েই ঠিকমতো খাবার পেত না, জীবন কায়ক্লেশে চলত। তাই মজুরি কমায় যে কোনো উপায়ে দেশে ফেরা ছাড়া শ্রমিকদের উপায় আর রইলো না। নিম্ন মজুরি ও প্রতিনিয়ত নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ পেতে বাঁচার আশায় ১৯২১ সালের মে মাসে আসামের চা-বাগান শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে ছিলো অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ। শ্রমিকরা চা-বাগান ছেড়ে শুরু করেন স্বদেশযাত্রা, তাদের ভাষায়- ‘মুল্লুকে চলো’।
মুল্লুকে চলো আন্দোলন
১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯২১ সালের শুরু থেকে এ আন্দোলনের ঢেউ প্রবল উচ্ছাসে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের সূচনালগ্নে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কিছু কলেজ ছাত্র চা শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা যাচাইয়ে ব্রতী হন। তাদের কাছে চা-শ্রমিক জীবনের করুণচিত্র উপস্থাপিত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ শ্রমিকদের ওপর পড়বে- এমন আশঙ্কায় বাগান মালিকরা চা-বাগানে স্বেচ্ছাসেবক ও কংগ্রেস কর্মীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। কেবল তা-ই নয়, চা-বাগানের বিষয়ে বাইরের কারো সাথে কথা বললে শ্রমিকদের শাস্তির ভয় দেখানো হয়।১ যদিও এই হুমকি-ধমকিতে শেষ রক্ষা হয়নি। একদিকে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ, অন্যদিকে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও কষ্ট- সবমিলিয়ে আসামের চা-শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখে স্ব-স্ব গ্রামে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়। গবেষক শচীন দত্ত লিখেছেন :
উত্ত্যক্ত হয়ে চা শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত করল, বছরের পর বছর কর্তৃপক্ষের অমানুষিক অত্যাচার আর সহ্য না করে, সদলে কাজ ছেড়ে আপন আপন গ্রামে ফিরে যাবে। কর্তৃপক্ষ তখন তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন তাদের ঋণ এবং স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী বাধ্যবাধকতার কথা।২
এসব বাধা-হুমকির তোয়াক্কা করেননি চা শ্রমিকরা। ১ মে ধলাই ভ্যালিতে শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির জন্য জনসভা হয়। ২ মে চরগোলা ভ্যালিতে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। ৩ মে আনিপুর চা-বাগান থেকে ৭৫০ জন (পরিবারসহ) শ্রমিক বেরিয়ে পড়ে। চা-বাগান মালিকরা তখন ১৪৪ ধারা জারি করে রেখেছিলো। শ্রমিক বের হওয়ার খবর সুরমা বরাক উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়লে অন্য বাগানের শ্রমিকরাও বাগান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।৩ গবেষক বিবেকানন্দ মোহন্ত তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন, কেবল চরগোলা ভ্যালি থেকে মুলুক চল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল ৮১১২ জন।
চা শ্রমিকদের মুখে স্লোগান ছিলো ‘গান্ধী মহারাজ কী জয়’। গন্তব্য করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন থেকে চাঁদপুর হয়ে গোয়ালন্দ, তারপর স্ব-স্ব মুল্লুকে ফেরা। চা-বাগান মালিকরা পূর্বেই রেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাজশ করে রেখেছিলো। রেলকর্তারা শ্রমিকদের প্রথম দিকে কিছু টিকেট দিলেও পরে তা বন্ধ করে দেয়।
মালিকরা যে কোনো উপায়ে শ্রমিকদের বাগানে ফেরাতে চেয়েছিলো। তারা ভেবেছিল করিমগঞ্জে ট্রেনের টিকেট না পেলে শ্রমিকরা মুল্লুকে ফিরতে পারবে না। কিন্তু শ্রমিকরা প্রাণপণে দাসত্ব থেকে মুক্তি চেয়েছিলো। তাই টিকিট না দিলেও তাদের আটকানো যায়নি। অনেক শ্রমিকই পায়ে হেঁটে চাঁদপুরের দিকে যাত্রা শুরু করেন এবং চাঁদপুর পৌঁছেন। ততদিনে স্থানীয় কংগ্রেসি ও খিলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে শ্রীশচন্দ্র দত্ত, নৃপেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, ইন্দ্রকুমার দত্ত, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অখিল চন্দ্র দত্ত, কামিনী কুমার চন্দ্র, হরদয়াল নাগ, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখের চেষ্টায় নারী-শিশু ও বৃদ্ধরা ট্রেনযাত্রার সুযোগ পায়।৪
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীশচন্দ্র দত্ত তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন,
করিমগঞ্জস্থ অনেকগুলি চা-বাগানের ২০/২৫ হাজার (?) শ্রমিক বাগান পরিত্যাগ করিয়া করিমগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সমগ্র শহরে একটা চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হইল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে আমরা এই চা শ্রমিকদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিলাম এবং তাহাদিগকে দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম।
ফলে হাজার হাজার চা-শ্রমিক চাঁদপুরে এসে জড়ো হন। এখান থেকে চা-শ্রমিকরা গোয়ালন্দ হয়ে কলকাতা ও উত্তর ভারতে যেতে পারবে। ১৯২১ সালের সরকারি তদন্ত কমিটির তথ্যমতে, ৯ মে সর্বপ্রথম স্থানীয় কর্মকর্তাগণ চাঁদপুরে চা শ্রমিকদের আগমনের বিষয়টি লক্ষ করেন। ১৬ মে ত্রিপুরার কালেক্টর মি. ওয়ারেস চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার কিরণচন্দ্র দেবকে জানান, প্রতিদিন গড়ে ২০০ জন শ্রমিক চাঁদপুরে আসছে। মি. ওয়ারেস ১৫ মে সরেজমিনে দেখেছেন, চাঁদপুর রেলস্টেশনে ১৬০০ জন কুলি বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করছেন।৫
স্যার হেনরি হুইলারের রিপোর্ট অনুসারে, কর্মকর্তাদের দাতব্য তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করে মি. ওয়ারেস প্রথম ধাপে ১ হাজার কুলিকে বিশেষ স্টীমারযোগে গোয়ালন্দে প্রেরণ করেন। পরে ১৬ ও ১৭ মে আরও ১৩৮৭ জন কুলিকে সরকারি খরচে গোয়ালন্দে পাঠান। এর মধ্যে স্থানীয় প্রশাসন বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করেন- শ্রমিকদের এভাবে প্রত্যাবাসনের ব্যয় মেটানোকে তারা সমর্থন করেন না। ফলে ১৭ মে থেকে চা শ্রমিকদের আর গোয়ালন্দে পাঠানো হয়নি।৬
মূলত, এমন কঠোর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পেছনে চা-বাগান মালিকদের হাত ছিলো। তারা কোনোভাবে চাননি শ্রমিকরা মুল্লুকে ফিরে যাক। তাদের লাভের জন্যেই শ্রমিকদের বাগানে ফেরাতে তারা মরিয়া ছিলেন। তাই চা-শ্রমিকদের ঠেকাতে মালিকপক্ষ বাংলা সরকারের সহযোগিতা চান। গভর্নরকে বলা হলো, ‘শ্রমিকদের চলে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে এই আন্দোলন বন্ধ করুন।’ বিশেষ করে শ্রমিকদের বাগানে ফিরিয়ে নিতে ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি মি. ম্যাকফারসনকে চাঁদপুরে পাঠানো হয়। তিনি চাঁদপুরে এসে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। ফলে শ্রমিকদের প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। বদলে যায় প্রশাসনের সদয় আচরণও।
দুঃখজনক হলেও সত্য, শ্রমিকদের কাছে অর্থ ছিল না। টিকেট কাটার পয়সা নেই। হাজার হাজার শ্রমিক অনাহারে-অর্ধাহারে আটকা পড়লেন চাঁদপুরে। কতজন শ্রমিক চাঁদপুরে আটকা পড়েছিল, এ বিষয়ে একাধিক তথ্য পাওয়া যায়। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে, চাঁদপুরে আটকে পড়া চা শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৪ হাজার।৭ অন্যদিকে গবেষক সুকোমল সেন তাঁর বইয়ে শ্রমিকদের সংখ্যা ৩ হাজার উল্লেখ করেছেন।৮
১৯২১ সালের সরকারি তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত চাঁদপুরে ৩ হাজার শ্রমিক অবস্থান করেছিলো। এর আগে অবশ্য মি. ওয়ারেস ২৩৮৭ জনকে কয়েক ধাপে স্টিমারযোগে গোয়ালন্দ প্রেরণ করেছিলেন। বেসরকারি তদন্ত প্রতিবেদন মতে, ১৯ মে তারিখে চাঁদপুরে অবস্থানরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ হাজারের বেশি।৯
অনাহারে ক্লিষ্ট এবং নির্মম নির্যাতনের সবরকম সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও চা-শ্রমিকরা বাগানে ফিরে যায়নি। তারা মুল্লুক যাত্রার সিদ্ধান্তেই অটল ছিলেন। কেননা তারা উপলব্ধি করেছিলেন, মুল্লুকযাত্রার মাধ্যমেই আসবে তাদের প্রকৃত মুক্তি। সেখানে তারা মানুষের মতো বাঁচতে পারবে।
চা-শ্রমিকদের ইতিহাস
তথ্যসূত্র :
১. হোসাইন মোহাম্মদ জাকি, ‘চা শ্রমিকদের ইতিবৃত্ত’, প্রথম আলো, ২০ নভেম্বর ২০১৯। ২. প্রার্থ শঙ্কর সাহা, ‘শতবছর পর মুল্লুক চলো আন্দোলনের সুলুক সন্ধান’, ঢাকা : প্রথম আলো, ১৯ মে ২০২১। ৩. নিতিন ভার্মা, ‘কুলিজ অব ক্যাপিটালিজম : আসাম টি এন্ড দ্য মেকিং অব কুলি লেবার’, জার্মানি : উব এৎুঁঃবৎ ঙষফবহনড়ঁৎম, পৃ. ২৪-২৫। ৪. সায়েদুল ইসলাম, ‘চা যেভাবে জনপ্রিয় পানীয় হয়ে উঠলো বাংলাদেশে’, বিবিসি বাংলা, ২১ মে ২০২২। ৫. সায়েদুল ইসলাম, পূর্বোক্ত। ৬. িি.িঞবধনড়ধৎফ.এড়া.নফ। ৭. ফিলিপ গাইন, ‘চা শ্রমিকদের অবদান ও বঞ্চনা’, বণিক বার্তা, ৩০ জুন ২০২১। ৮. সালাউদ্দিন শুভ, ‘চা-কন্যাদের দুঃখের কথা’, প্রতিদিনের সংবাদ, ১১ মার্চ ২০২১।
‘মুল্লুকে চলো’ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট
তথ্যসূত্র :
১. ড. রজনী কান্ত দাস, প্লান্টেশন লেবার অব ইন্ডিয়া, কলকাতা : প্রবাসী প্রেস, ১৯৩১ পৃ. ৯৫। ২. প্রাগুক্ত। ৩. অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ, শত শহীদের রক্তে, কলকাতা : তুলি-কলম, শ্রাবণ ১৩৬৭, পৃ. ১০৫। ৪. ড. দেওয়ান চমনলাল, কুলি- দ্য স্টোরি অব লেবার এন্ড ক্যাপিটাল ইন ইন্ডিয়া, ভলিয়ম ২, প্রকাশকাল : ওরিয়েন্টয়াল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৩২, পৃ. ১৮। ৫. সোমপ্রকাশ, ১ জুন ১৮৬৩। ৬. সুকোমল সেন, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-১৯৭০), প্রথম খণ্ড, কলকাতা : নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫, পৃ. ১০০। ৭। প্রাগুক্ত, ১০৩।
মুল্লুকে চলো আন্দোলন
তথ্যসূত্র :
১. শচীন দত্ত, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অনুবাদ : প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ভারত : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৭, পৃ. ২৬। ২. প্রাগুক্ত, ২৬। ৩. বিবেকানন্দ মোহন্ত, চরগোলা এক্সোডাস ১৯২১, শিলচর : সৃজন, ২০১৪, পৃ. ৮৮। ৪. প্রাগুক্ত, ৮৮। ৫. এইচ.এন মিত্র (সম্পা.), দ্য ইন্ডিয়ান অ্যানুয়েল রেজিস্ট্রার, ১৯২২-১৯২৩, (সম্পা.), কলকাতা : দি অ্যানুয়েল রেজিস্ট্রার অফিস, ১৯২৩, পৃ. ৭৫৯। ৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫৯। ৭. শচীন দত্ত, পৃ. ২৭। ৮. সুকোমল সেন, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-১৯৭০), প্রথম খণ্ড, কলকাতা : নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫, পৃ. ১০০। ৯. এইচ.এন মিত্র (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫৯। ১০. এইচ.এন মিত্র (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫৯।