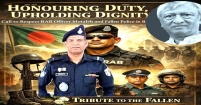প্রকাশ : ৩০ এপ্রিল ২০২৩, ০০:০০

বাংলাদেশে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা সভা-সমিতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও রাজনৈতিক বক্তৃতায় প্রায়ই বলে থাকেন, দেশে আইনের শাসন (Rule of Law) নেই। আর সরকারি দলের নেতা-নেত্রীরাও বলে থাকেন, আইনের শাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। সরকারি ও বিরোধী দলের বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা বৈসাদৃশ্য থাকলেও গভীরভাবে বাস্তবতার আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, বক্তব্যগুলো অপ্রিয় অসত্য নয়। বাংলাদেশে আইনের শাসন নিশ্চিত হওয়ার বিধান সংবিধানে সংযোজিত থাকলেও তা আদৌ কাঙ্ক্ষিতরূপে বাস্তবায়িত হতে পারে নি।
১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষের জীবন ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বাস্তবে রূপ পাওয়ার পর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর আমাদের মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, “আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে ------”। যা ওই সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে আইনের শাসনের মূল দর্শন হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। উক্ত সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদে আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার ওয়াদা করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং ৪৪ অনুচ্ছেদ ও ১০২ অনুচ্ছেদে এগুলো বলবৎকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৭ ও ২৬ আইন বিভাগের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে দিচ্ছে যে, সংবিধান ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কোন আইন পাস করা যাবে না। আরো উল্লেখ্য, অনুচ্ছেদ ৭, ২৬ ও ১০২ (২) সুপ্রীম কোর্টকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার (Judicial review) ক্ষমতা দিয়েছে। অতএব আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ তাদের সীমা লংঘন করলে সুপ্রীমকোর্ট তাদের কাজকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে।
আইনের শাসন বলতে বুঝায়, শাসক ও শাসিত একই আইনের অধীনে থাকবে। আর ওই আইনের অধীনে শাসনকে বুঝায়, যে আইনটি গণতান্ত্রিক অর্থাৎ যে আইনের ভিত্তি জনগণের পূর্ণ সম্মতি সাপেক্ষ। আইনের শাসনের পক্ষে তথা আইনের শাসন নিশ্চিতকরণের জন্যে সংবিধানে উক্তরূপ বিধিব্যবস্থা থাকলেও আইনের শাসনের প্রথম ও প্রধান পূর্বশর্ত হলো সাংবিধানিক বা পূর্ণ গণতান্ত্রিক সরকার। আর সাংবিধানিক সরকার (Constitutionalism) প্রতিষ্ঠিত হলে উক্ত সরকার একটি আইনসভার নিকট জবাবদিহি থাকবে, যে আইনসভা সুষ্ঠু ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে। উক্ত আইনসভায় সরকারের পক্ষে অগণতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন করা সম্ভবপর হবে না, পর্যাপ্ত আলোচনার মাধ্যমেই প্রণয়ন হবে, সরকারের প্রতিটি কাজের সমালোচনা হবে। ফলে সরকার কখনো Rule of Man -এর ভূমিকায় যেতে পারবে না।
আর গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বহুদলীয় গণতন্ত্র থাকবে। ফলে সরকার একনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবে না। কারণ তাহলে তাকে পরবর্তী নির্বাচনে ভরাডুবি খেতে হবে। বিরোধী দলগুলো সমালোচনা ও প্রতিবাদের মাধ্যমে সরকারকে সর্বদা গণতান্ত্রিক রাখবে। সাংবিধানিক সরকার যেহেতু সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যায়, কাজেই ইহা নির্বাচনের সময় জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি (Mandate) অনুযায়ী আইনের শাসনের বিপক্ষে কাজ করতে পারে না। আইনের শাসন নিশ্চিত করার মানসিকতা নিয়েই তাকে কাজ করতে হয়। উক্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ অবশ্যই থাকবে। ফলে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করবে এবং সরকার স্বেচ্ছাচারীভাবে অধিকারগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।
বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বিভিন্ন উন্নত বিশ্বের ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একসময় তাদের ইতিহাস রাজা বাদশাহদের একনায়কসুলভ ভয়াবহ স্বৈরশাসন প্রত্যক্ষ করেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজার সাথে পার্লামেন্টের বিরোধের ফলস্বরূপ ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং ১৬৮৯ সালে অধিকারের বিল (Bill of Rights) প্রণীত হয়, যার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে, রাজা আইন ও পার্লামেন্টের অধীনে থাকবে। এভাবে রাজার মানুষের শাসনের (Rule by man) পরিবর্তে আইনের শাসন (Rule of Law) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তৎকালীন বৃটেনেও স্বৈরীক্ষমতা অনেকটা ছিল, এখনও আছে এবং পৃথিবীর সকল সরকার ব্যবস্থাতেই স্বৈরী বা বিশেষ ক্ষমতা আছে এবং হয়তো থাকবে। নিবর্তনমূলক আটক (Preventive Detention), সরকারিভাবে নাগরিকের সম্পত্তি অধিগ্রহণ, বিভিন্ন সময়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে বিশেষ স্বৈরীক্ষমতা প্রয়োগ, বিশেষ স্বেচ্ছাচারী আইন প্রণয়ন, অর্পিত-ক্ষমতাপ্রসূত আইন (Delegated Legislation এর মাধ্যমে শাসন বিভাগকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি প্রায় সকল সরকার ব্যবস্থাতেই আছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়।
বর্তমানকালে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আইনের শাসন ধারণাটির পরিধি আরও ব্যাপকতর হয়েছে। ১৯৪৮ সালে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল ১৯৭৬ (International Bill of Human Rights 1976), এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক কভেন্যান্ট ও আন্তর্জাতিক আইনজীবী কমিশনের বিভিন্ন কংগ্রেস ও সম্মেলনের ফলে এখন আইনের শাসন বলতে শুধু গণতান্ত্রিক আইন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচকে বোঝায় না, বরং এসব উপাদানসহ মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ ও জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানকে বুঝায়। কারণ ক্ষধার্ত ও অভাবী মানুষের কাছে আইনের শাসন অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। ‘আইনের রক্তচোখ ক্ষুধার্ত মানুষকে আইন মানতে বাধ্য করতে পারে কিন্তু এর প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান আদায় করতে পারে না।’ (ড. এম এরশাদুল বারী- আইনের শাসন ও মানবাধিকার, পৃ : ১৪)। এ কারণে এখন শুধুমাত্র ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকারের পরিবর্তে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের উপর, যা জনগণকে একটি যুক্তিসংগত জীবনধারণের মান নিশ্চিত করতে পারে।
আইনের শাসন বলতে ব্যাপক অর্থে সাংবিধানিক সরকারকে বুঝায়। আর সাংবিধানিক সরকার হলো গণতান্ত্রিক। সরকারের শাসনের ভিত্তি হলো আইন। উক্ত আইন গণতান্ত্রিক হলেই আইনের শাসন বা সাংবিধানিক সরকার নিশ্চিত হয়ে যায় না। ওই গণতান্ত্রিক আইনটি সঠিকভাবে মেনে চলা হচ্ছে কিনা এবং উক্ত আইনে সৃষ্ট অধিকারসমূহ জনগণ সত্যিকারভাবে ভোগ করতে পারছে কিনা এ সবের ওপরই আইনের শাসনের সাফল্য নির্ভর করে। আইনের শাসনের অঙ্গীকার রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে কতকগুলো বিধান সংযোজন করা হলেও তা বাস্তবায়নে উপেক্ষা করারও কিছু বিধান রয়েছে। আর প্রত্যেক সরকারই আইনের শাসনের বিরোধী-বিধান সমূহের সুযোগ লুফে নিচ্ছেন, যার ফলস্বরূপ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না।
এক. আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি হলো একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ। শুধু নিয়োগপদ্ধতির বিধান ব্যতীত সুপ্রীম কোর্টের (Higher Judiciary) স্বাধীনতা সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু নিম্ন আদালতের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়নি। কারণ নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ নির্বাহী বিভাগের হাতে ন্যাস্ত। ম্যাজিস্ট্রেটগণ একইসাথে বিচার বিভাগীয় ও নির্বাহী উভয় ক্ষমতা প্রয়োগ করছে। যার ফলে তাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। অতএব ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আইনের চোখে সমতা নিশ্চিত হতে পারছে না।
দুই. নিবর্তনমূলক আটকের বিধান কেবলমাত্র যুদ্ধকালীন সময়ে রাখা উচিত। কিন্তু সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদে এমন বিধান করা হয়েছে যে, সম্পূর্ণ শান্তির সময়ে সরকারের এ ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগে অপব্যবহার করেছে এবং করছে। যার ফলে গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে সমতা এবং আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার (অনু : ৩১) নিশ্চিত হয়নি। সুতরাং শান্তির সময় নিবর্তনমূলক আটকের বিধান আইনের শাসনের পরিপন্থী।
তিন. সংবিধানে ৭০ অনুচ্ছেদ থাকার কারণে সরকারি দলের সংসদ সদস্যগণ সরকার কর্তৃক উত্থাপিত বিলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারে না, সংসদ সদস্যপদ হারাবার ভয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস তারা পায় না। ফলে সরকার অনায়াসে অগণতান্ত্রিক আইনও পাস করায়ে নিতে পারে। আইনের শাসনের যে মূল ভিত্তি, সেটি হচ্ছে আইনটিকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক হতে হবে, আইনটি অবশ্যই সংসদে পর্যাপ্ত আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের পর পাস হবে। সেটি কিন্তু ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে সম্ভবপর হচ্ছে না। তাই ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে আমাদের দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়ে দলের শাসন (Rule of Party) জন্ম নিচ্ছে।
চার. সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চাকুরি সংক্রান্ত যে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু যেহেতু উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারকের নিয়োগ ও চাকুরির নিশ্চয়তা সংবিধানে কিছু বলা নেই এবং যেহেতু এরূপ ট্রাইব্যুনালকে সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ারে রাখার কোনো বিধানও সংবিধানে নেই, সুতরাং ইহা আইনের শাসনের পরিপন্থী বলা যেতে পারে।
পাঁচ. অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা সংবিধানে রাখা অযৌক্তিক নয়, কিন্তু তা এমনভাবে রাখা উচিত যেন সংসদকে পাশ কাটিয়ে নির্বাহী বিভাগ কোনো অগণতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন না করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের সংবিধানে যে বিধান করা হয়েছে, তাতে নির্বাহী বিভাগ খেয়াল খুশিমত সংসদের দুই অধিবেশনের মাঝখানে প্রায় প্রতিবারেই কয়েকটি করে অধ্যাদেশ জারি করে। ফলে দেশের আইনের কম-বেশি একটি অংশ অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রণীত। ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে প্রায় প্রতিটি অধ্যাদেশই সংসদে পাস হয়ে যায়। অধ্যাদেশ প্রণীত আইন সর্বদাই আইনের শাসনের বিরোধী। কারণ এরূপ আইন সংসদে পর্যাপ্ত আলোচনার পর পাস হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রে অধ্যাদেশ কর্তৃক সৃষ্ট আইন কার্যকর করার পর সংসদে উত্থাপিত হয়।
ছয়. দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান যুদ্ধকালীন সময় ব্যতীত সমর্থন করা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগ যে কোনো সময়ে প্রয়োজনে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারে, মৌলিক অধিকারগুলোকে স্থগিত করতে পারে। বিরোধী দলের মুখ বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু শান্তিকালীন অবস্থায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও মৌলিক অধিকার স্থগিত করে দেয়া স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় বহন করে, যা আইনের শাসনের বৈশিষ্ট্যে পড়ে না।
সাত. মহাহিসাব রক্ষক ও অডিটর জেনারেল (CAG) একটি স্বাধীন সাংবিধানিক পদ। সরকারি অর্থ ব্যয়ের ওপর অডিট করা এবং অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত অনিয়ম ও অভিযোগ তৈরি তাঁর কাজ। পৃথিবীর প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশে ‘CAG’ পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল রাখা হয়। তাঁকে নিয়োগের ক্ষেত্রে ‘সরকারি হিসাব সংক্রান্ত কমিটি (PAC)’-এর সাথে আলাপের বিধান আছে। ‘CAG’ তার কাজের স্বাধীনতার স্বার্থে তাঁর পুরো স্টাফকে তিনি নিজেই নিয়োগ দান করেন। কিন্তু বাংলাদেশে ‘CAG’ কে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়িত্বশীল রাখা হয়েছে, আর ‘CAG’-এর পুরো স্টাফকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ করে রাখা হয়েছে। ফলে ‘CAG’ তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে না। ফলে সরকার বিভিন্নভাবে বরাদ্দকৃত টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করার সুযোগ পাচ্ছে। কাজেই ‘CAG’-এর পূর্ণ স্বাধীনতার অভাব হেতু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে বাধা পাচ্ছে।
বস্তুতঃ আইনের শাসন নিশ্চিতকরণকল্পে কতিপয় বিধান সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে ঠিক, কিন্তু আইনের শাসনের পরিপন্থী যে সকল বিধান সংযোজন করা হয়েছে তার ফলে আইনের শাসনের কার্যকারিতা অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ন হচ্ছে অহরহ। আইনের শাসন নিশ্চিত করণার্থে মৌলিক মানবাধিকার ও আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিন্তু সংবিধানে ১৮টি মৌলিক অধিকার সংযোজিত করা হলেও বাংলাদেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এ অধিকারগুলো অর্থহীন, যদি না অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও কাঙ্ক্ষিত আইন-সহায়তা (Legal Aid) না পায়। অপর দিকে উল্লেখ্য, স্যার আইভর জেনিংস ‘The Law and the Constitution- P-47’ গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন “প্রকৃত অর্থে আইনের শাসন বলতে একটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা তথা সাংবিধানিক সরকারকে বুঝায়, যেখানে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুধু অনুমোদিত নয় বরং একটি উত্তম গুণ (A Positive Merit); রাজনীতি শুধু গ্রহণযোগ্য (Allowed) নয় বরং উৎসাহিত করা হয়। যেখানে এ বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে সেখানে আইনের শাসনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি নির্গত হয়।”
তথ্য-সহায়ক গ্রন্থ :
১. সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ-মোঃ আব্দুল হালিম, জুন ১৯৯৭
২. বাংলাদেশের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া-মোঃ রফিকুল ইসলাম (রফি), এন এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, জানু-২০১৭
৩. আইনের শাসন ও মানবাধিকার-ড. এম. এরশাদুল বারী, ঢাকা
৪. Sir Ivor Jennings : The Law and The Constitution (Fifth edition)
৫. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক উন্নয়ন-ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, আনন্দ প্রকাশন, এপ্রিল-২০১৬
৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত)-অক্টোবর, ২০১১
৭. বাংলাদেশ প্রতিদিন-৩১ জানুয়ারি-২০২২
লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক মোঃ হাছান আলী সিকদার, সভাপতি, চাঁদপুর জেলা জাসদ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা; চাঁদপুর জেলা শিক্ষক নেতা, সমাজ ও রাজনীতিবিশ্লেষক।