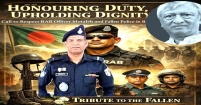প্রকাশ : ১৭ জুন ২০২৩, ০০:০০

যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র বিচারপতি লর্ড উল্ফ বিচার ব্যবস্থার সঙ্কট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ‘বিলম্ব এবং ব্যয়’কে। যে কারণে তিনি বিকল্প উপায়ে মামলা নিষ্পত্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আমাদের দেশে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র মামলার ফাঁদে ফেলে অজস্র অর্থ ও সময়ের অপচয় সম্পর্কে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি এম রুহুল আমীন দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, ‘সত্য গোপন করে এবং জাল কাগজ দিয়ে যে কেউ তার অনুকূলে আদালতের রায় নিতে পারে।’ এ সমাজে অপরাধের অন্তর্নিহিত স্বরূপ কতটা আমরা উদ্ঘাটন করতে পারি? বস্তু থেকে চিন্তা, চিন্তা থেকে কাজ, কাজ থেকে ফলাফল, ফলাফল থেকে মূল্যায়ন। তদ্রƒপ আমাদের চিন্তা ও মনন মানবীয় আবেগ ও প্রবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত। রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার নিয়ত পরিবর্তনশীলতার ধারায় যুক্ত হয় নতুন সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা এবং বিচারব্যবস্থা। তারই ধারাবাহিকতার আলোকে ‘ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে’ মোবাইল কোর্ট অনেকটা সমাদৃত বিচার কার্যক্রম।
যেখানে অপরাধ, সেখানেই বিচার। মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যাওয়া বিচার। অর্থাৎ চোখের সামনে ঘটে যাওয়া অপরাধের প্রকাশ্য বিচার। এটাই মোবাইল কোর্টের স্বরূপ। ১৯৫০ সালে মাদ্রাজ হাই কোর্টের মাধ্যমে যার সৃষ্টি ট্রায়াল অ্যাট দ্যা পিস অব অকারেন্স, না দেখা অপরাধ এবং বাস্তবে দেখা অপরাধ; এ দুয়ের মাঝে রয়েছে বিশাল তফাৎ। বাস্তবে যা দেখা হয়নি, তার বিচারে প্রয়োজন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ। আর বাস্তবতা হলো, বিচার আদালত বিচার দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু আদালতে বাদী বা সাক্ষী নেই, তারিখ পড়ছে বারবার, অনেকক্ষেত্রে সমন বা ওয়ারেন্ট দিয়েও সাক্ষী আনা যাচ্ছে না। আবার আদালতে এসে ঘটনার সময়কার স্মৃতি ভুলে দুর্বল সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে, এমনকি প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরাও ভয়ে কিংবা অন্য কোনো স্বার্থে মুখ খুলছে না। এছাড়া থাকে অজ্ঞাতনামা আসামি, তদন্ত কর্মকর্তাদের গাফিলতি ও ত্রুটি, অভিযোগনামায় সত্য গোপনের চেষ্টা, পারিপার্শ্বিক প্রমাণ মুছে ফেলা ইত্যাদি ইত্যাদি।
উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১০ সালে পরিবেশ অধিদফতরের দায়ের করা এক মামলায় এখনো চার্জশীট উপস্থাপন হয়নি। সাগর-রুনি হত্যা মামলার শুনানির তারিখ ৯৩ বার পিছানো হয়েছে, যার আসামী আদৌ চিহ্নিত করতে পারছে না কেউ। বছর গড়িয়ে যায়, অপরাধীও অদৃশ্য বালিয়াড়িতে হারিয়ে যায়। ফলে বিচার অনিষ্পন্ন রয়ে যায়। এরপর আছে সমাজের দুষ্ট ক্ষত মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রবণতা। বিচার উপেক্ষা বা বিলম্বিত বিচারের সংস্কৃতি সৃষ্টি করে অপরাধের ক্রমবৃদ্ধি। আমাদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫২ ধারা আদালতকে তাঁর অধিক্ষেত্রের যে কোনো স্থানে বসে বিচার করার এখতিয়ার দিয়েছে। এসব প্রেক্ষিতে সরকারি সম্পদ, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কেন্দ্রিক অপরাধ দমনে মোবাইল কোর্ট অনন্য শক্তি। মোবাইল কোর্টের হাতে প্রকাশ্যে অপরাধীর দৃশ্যমান শাস্তির ইতিবাচক প্রভাব পড়ে আইনের শাসনের সূচকেও।
মোবাইল কোর্টের সেতু বেয়ে বিএসটিআই, পিডিবি, বিআরটিএ, ওয়াসা, ডিপিডিসি, রাজউক, বন্দর, তিতাস গ্যাস, পরিবেশ অধিদফতরসহ বহু প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বাস্তবতায় দেশের উচ্চ আদালত খাদ্য ও সড়ক নিরাপত্তা, পরিবেশ ও নদ-নদী রক্ষাসহ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট জনগুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ে নির্বাহী বিভাগকে যে নির্দেশনা দিচ্ছে, তার সফল বাস্তবায়নে নিরন্তর কাজ করছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ।
আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, প্রসিকিউশন সংস্থার প্রতিনিধি বা বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে এমনকি মিডিয়াকে সামনে রেখে যৌক্তিক প্রমাণসহ গভীর অনুসন্ধানী চোখ ও মন নিয়ে মোবাইল কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটকে বিচার কাজ করতে হয়। অপরাধকে সামনে রেখেই জনসম্মুখে অপরাধীর স্বীকারোক্তি, তাই অপরাধ ঘটিয়ে মোবাইল কোর্টের সামনে মিথ্যা বলার বা মামলার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। তবে নির্দোষ ব্যক্তি ভুলক্রমে মোবাইল কোর্টে দণ্ডিত হলেও উচ্চ আদালত থেকে অবধারিতভাবে মুক্তি পেতে পারে। এমনকি ন্যায়বিচারের প্রশ্নে ডিএম কিংবা এডিএম কোর্ট থেকেও জামিনে মুক্তি লাভ করতে পারে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের আদেশের বিরুদ্ধে ডিএমণ্ডএর কাছে আপিল, এরপর বিজ্ঞ দায়রা জজের কাছে রিভিশন, সর্বশেষ আছে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে রিট দায়ের। অতএব, মোবাইল কোর্টের আদেশ বা রায় অপরিবর্তনীয় নয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা খাদ্যে ভেজাল, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, ভূমিদস্যুতা, পরিবেশ-দূষণ, হাসপাতালে অপচিকিৎসা, সিন্ডিকেট ব্যবসা, অবৈধ ভবন নির্মাণ, মানহীন পণ্য উৎপাদন, অবৈধ ইটভাটা, গ্যাস-বিদ্যুৎ চুরি, মাদক সেবন ও ব্যবসা, নদ-নদী দখল, নিষিদ্ধ-ইলিশ শিকারসহ অগণিত দিগন্তে ছড়িয়ে থাকা অপরাধের বিরুদ্ধে নিরন্তর অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। কত নিষ্ঠায়, ত্যাগে ও শ্রমে মানুষের কষ্ট লাঘব এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতি রোধ এবং সুশাসনের সহযোগিতায় মোবাইল কোর্ট, তার হিসাব অপরিমেয় এবং বলার নয়।
জেল-জরিমানা যত স্বল্পই হোক, মোবাইল কোর্টের অভিঘাত পড়ে নাগরিক জীবনে, প্রতিষ্ঠানে, অর্থনীতিতে, সমাজে। তবে শুধু দণ্ড প্রদানে দায়িত্ব শেষ নয়, মোবাইল কোর্টের বাস্তবতার ভূমিকায় অপরাধ থেকে সমাজকে পরিত্রাণ দেয়া সম্ভব, যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে সুশাসনের মাত্রিকতায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস সম্ভব। চট্টগ্রাম বন্দর, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিদ্যুৎ সেক্টরে মোবাইল কোর্টের ভূমিকা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নাগরিকদের মধ্যে শাণিত হচ্ছে আইনমান্যতার প্রবণতা, সেটিও মোবাইল কোর্টের সার্থকতা। আবার প্রতিটি মোবাইল কোর্টই আইনের ক্যাম্পেইন। এতে ভোক্তা অধিকার, নাগরিক অধিকার সম্পর্কে মানুষ সচেতন হচ্ছে। খাদ্যে ভেজালের অনেক অজানা তথ্য জাতির সামনে উপস্থাপনে অনেকটাই ভূমিকা রাখছে মোবাইল কোর্ট। তাই পরিবেশ দূষণ ও খাদ্যে ভেজালের কষ্ট-বেদনায় দগ্ধ মানুষ মোবাইল কোর্টের নিরবচ্ছিন্ন অভিযান পেতে চায়, এর ছন্দপতন হলে জ্যামিতিক হারে বাড়বে অপরাধ।
বিচারিক আদালতের তফসিল বহির্ভূত হলেও এমন অপরাধ কিন্তু বিচারিক আদালতে যাচ্ছে। শুধু ২০১৩ থেকে ২০১৮ সালের পরিসংখ্যান মতে, মোবাইল কোর্টে ৬ লাখ ৩৫ হাজার মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, জরিমানা আদায় হয়েছে ২০৯ কোটি টাকা। এ বিপুল সংখ্যক অপরাধের মামলা বিচার বিভাগের ওপর এক বাড়তি চাপ হতে পারতো। তবে কতটা মোবাইল কোর্ট হলো, কত জরিমানা হলো, তার সংখ্যাগত মূল্যায়ন নয়, মানদণ্ডের ভিত্তি হতে হবে ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক মান। ন্যায়বিচার, সততা ও যোগ্যতা একসূত্রে গাঁথা। আমরা আশা করতে পারি, মোবাইল কোর্টের অভিযাত্রায় বিচারিক আদালতসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সিভিল সোসাইটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকরা একাত্ম হই। আইন না মানার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট শক্তিশালী অস্ত্র, এর যথার্থ প্রয়োগে সমাজের অবক্ষয় দূর করা সম্ভব।
লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক মোঃ হাছান আলী সিকদার, সভাপতি : চাঁদপুর জেলা জাসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা, চাঁদপুর জেলা শিক্ষক নেতা, সমাজ ও রাজনীতিবিশ্লেষক। রচনাকাল : ২৫/০২/২০২৩