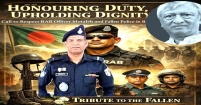প্রকাশ : ১৪ এপ্রিল ২০২৩, ০০:০০
আমাদের বৈশাখ

এসো হে বৈশাখ, এসো এসো।
|আরো খবর
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক॥
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক॥
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।
রচনাকাল (বঙ্গাব্দ) : ২০ ফাল্গুন, ১৩৩৩
রচনাকাল (খৃস্টাব্দ) : ৪ মার্চ, ১৯২৭
রবীন্দ্রনাথের এই গানটি দিয়েই আমাদের ১লা বৈশাখের মর্মবাণী উপলব্ধি করা যায়। এর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। আছে বাঙালির আত্মার সম্পর্ক।
পূর্বে এতদঞ্চলে চান্দ্র-সৌর বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে ১ বৈশাখ পালিত হতো। সেটি ইংরেজি এপ্রিল মাসের ১৪ বা ১৫ তারিখ পড়তো। বর্তমানে গ্রেগরি বর্ষপঞ্জি অনুসারে বাংলাদেশে প্রতিবছরই ১৪ এপ্রিল ১ বৈশাখ পালিত হয়।
বাংলা দিনপঞ্জির উদ্ভাবক কে? তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও মুঘল সম্রাট আকবর খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে বাংলা সনের গণনা কার্যকর করেন-এটি বহুল প্রচারিত।
ষড় ঋতুর প্রভাবে বাঙালির জীবন আবর্তিত হয়। একেক ঋতু একেক আবেদন নিয়ে নিজেকে হাজির করে। আদি বাঙালি সেভাবেই নিজেকে প্রকৃতির কাছে সমর্পণ করেছে। আর পলিমাটি সমৃদ্ধ এই বাংলার মাটি-বীজ, ফুল, ফল, ফসলে চারিদিক পল্লবিত হয়েছে। যদিও বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিতে আমদের মেধা মননকে বেশি উজ্জীবিত রাখি। কিন্তু বর্তমান সময়ে বাংলার অর্থনীতিকে সাসটেইনেবল বা টেকসই করতে কৃষির কোনো বিকল্প নেই। এটি বাঙালির জন্য পরম পাওয়া। এই মাটি, এই জলবায়ু, এই আবহাওয়া এই ভেতো বাঙালিকে গড়ে তোলে পরম সহিষ্ণু।
আর তাই করোনার পর উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানরা যখন অর্থনীতির চাকা ঠিক রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন, তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী বেশ জোর দিয়েই বলেন, আপনার এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখবেন না। ফসলের অভাব হবে না আপনাদের। অর্থনীতির চাকা সচল রাখুন। সত্যি তো এই আমার বাংলাদেশ।
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাম্
শস্য শ্যামলা-আসুন
দেশমাতার বন্ধনা করি।
সে অনেকদিন আগের কথা। তখন জমিদারি প্রথা। প্রকৃতপক্ষেই কৃষির ওপর নির্ভর ছিলো এতদঞ্চলের জীবন প্রবাহ। গরিব প্রজাদের উৎপাদিত ফসলের ওপর খাজনা, মাশুল/শুল্ক পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা ছিলো চৈত্র মাসের শেষদিন পর্যন্ত।
সারা মাস জুড়েই দেনা পরিশোধের জন্য মরিয়া দেনাদার, আর পাওনাদার পাওয়ার জন্যে মরিয়া। তাই চৈত্র বাঙালির জন্যে বড় খাটাখাটনির মাস। কারো চোখে ঘুম নেই, কাজের শেষ নেই। পুরুষেরা বাহিরের কাজে মনোযোগী আর নারীরা ঘরের কাজে মনোযোগী। চৈত্র মাস ধরেই চলে গাজীর পাঠ, পুঁথি পাঠ, শিব পার্বতী নাচ। ফেরিওয়ালা হাঁক দিয়ে যাচ্ছেন চৈত্রের দুপুরে।
এ সময়ে চৈত্র মাসে ঘরে ঘরে অসুখ বিসুখের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় বড় বেশি। জলবসন্ত, কলেরা, হাম, লুতি, খোস-পাঁচড়া, চোখ উঠা এ ধরনের ছোঁয়াচে রোগের প্রাদুর্ভাব গ্রাম্যজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামে ডাক্তার নেই বললেই চলে। ফলে চৈত্র সংক্রান্তির দিন আচার আচরণের মাধ্যমে দিনটিকে প্রতিষেধক হিসেবে গড়ে তোলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। চৈত্র সংক্রান্তির দিন খুব ভোরে নিম পাতা আর কাঁচা হলুদ বেটে সারা শরীরে মেখে স্নান করে। সেদিন কোনো মাছ-মাংস নয়। বরং বনাজী গাছপালা, লতাপাতা এরকম ৫০ থেকে ৮০ ধরনের জিনিস দিয়ে তেল ছাড়া নিরামিষ রান্না করা হয়। অবশ্য কেউ কেউ তেল দিয়েও রান্না করে। কিন্তু যারা তেল ছাড়া রান্না করে তারা শেষে ঘি আর ভাজা গুঁড়ো মশলা ঢেলে দেয়। ভাজা মশলায় রান্না এই পাচন এ ঘর থেকে ওঘরে, ওঘর থেকে এঘরে আসে। সেখানে বন আইট্টা থেকে বিভিন্ন ধরনের কচু, বিভিন্ন ধরনের তরকারি, টক, তিতা, কাঁচা হলুদ সব পদই থাকে। একে বলা হয় পাচন। দুপুরে পাচন, লুচি, সুজি, আলুর দম মিষ্টি ফল দিয়ে খাওয়া দাওয়া হয়। ফল তরমুজ, বাঙ্গি অবশ্যই থাকবে। অঞ্চল ভেদে নিয়মের কিছুটা হেরফের হলেও মূল অংশ একই। দোকানপাটে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হিসাব চুকিয়ে ঘরদুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলে। ফলে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। এভাবেই চৈত্র সংক্রান্তি শেষ হয়।
পহেলা বৈশাখ। নতুন স্বপ্ন নিয়ে ভূস্বামীরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, নিজ নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়ন করেন। সেই মিষ্টি হতো স্পেশাল। বাড়িতে চলে মাছ, মাংসের উৎসব। এ উপলক্ষে কেউ কেউ উৎসবের আয়োজন করতেন। বাড়িতে বাড়িতে বানর, হনুমান এনে খেলা দেখানো হতো। গ্রামে হাতি ঘোড়া আসতো। সার্কাস চলতো মাস জুড়ে।
তখনকার সময় এই দিনের প্রধান ঘটনা ছিল একটি হালখাতা তৈরি করা। হালখাতা হলো বছরের প্রথম দিনে দোকানপাটের হিসাব-আনুষ্ঠানিকভাবে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া। ব্যবসায়ীরা তাদের দেনাপাওনার হিসাব সমন্বয় করে নতুন খাতা খোলেন। হিসাবের খাতা হালনাগাদ করা থেকেই হালখাতার উদ্ভব। খদ্দেররা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পুরানো দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। হালখাতা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রেতাণ্ডবিক্রেতার মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরি হয়।
এ কারণেই বাংলা বর্ষপঞ্জিতে ধর্মীয় অনুষঙ্গ নেই। তাই বাঙালির এ পঞ্জিকাটি হয়ে উঠতে পেরেছে ধর্মণ্ডসম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলায় বসবাসরত প্রতিটি মানুষের কাছে অসাম্প্রদায়িক।
পহেলা বৈশাখ বাঙালির সার্বজনীন লোক উৎসব। বছরের শেষদিন বিদায় আর নতুনকে বরণ। হালখাতার দিনে দোকানদাররা তাদের ক্রেতাদের বন্ধুবান্ধবদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকে। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে নতুন করে ডাক দেয়। বুকে তুলে আলিঙ্গন করে সবাইকে। হিসাবনিকাশ চুকিয়ে নতুন সূর্য উদিত হয়।
দিন যায় মাস যায় বছর যায়। জমিদারি প্রথা একদিন শেষ হয়। কিন্তু উৎসবপ্রিয় বাঙালি তার অতীত ঐতিহ্যকে ভুলে না। আঁকড়ে ধরে। বাঙালির একটি সুন্দর অতীত আছে। হাজারো বাধা পেরিয়েই সে অটুট থাকে তার সংস্কৃতিতে। বার বার আঘাত আসে। সে রুখে দাঁড়ায়।
সারা বছরের শেষদিন ৩০ চৈত্রকে চৈত্র সংক্রান্তির নামকরণে পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেমন বেঁধেছে, তেমনি পহেলা বৈশাখের আনন্দকে সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে।
বাংলাদেশে চৈত্র সংক্রান্তি এবং পহেলা বৈশাখ উদযাপন হয়।
নতুন বছরের উৎসবের সঙ্গে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নিবিড় যোগাযোগ। গ্রামে মানুষ ভোরে ঘুম থেকে ওঠে, কাঁচাহলুদ, নিমপাতা বাটা দিয়ে স্নান করে। দৈ, মুড়ি, খৈ, চিড়া, নারকেল, কলা, মিষ্টি খেয়ে দিনের সূচনা করে। অনেকের বাড়িতে খৈয়ের ছাতু দিয়ে নাড়ু তৈরি হয়। অতঃপর নতুন জামাকাপড় পরে এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে মিলিত হয়। 'শুভ নববর্ষ' বলে শুভেচ্ছা বিনিময় করে, কোলাকুলি করে।
চৈত্র মাসে বাড়িঘর পরিষ্কার করা হয়। পহেলা বৈশাখে বাড়িঘর সুন্দর করে সাজানো হয়। বিশেষ খাবারের ব্যবস্থাও থাকে। বিভিন্ন ধরনের মেলা বসে গ্রামের মিলিত এলাকায়, এই মেলা ৭দিন থেকে ১মাস পর্যন্ত চলে। মাটির জিনিসের প্রাধান্য থাকে। কোনো খোলা মাঠে আয়োজন করা হয় এই বৈশাখী মেলার।
এই দিনের একটি পুরানো সংস্কৃতি হলো গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন। এর মধ্যে থাকে নৌকাবাইচ, লাঠি খেলা, বলি খেলা কিংবা কুস্তির। বাংলাদেশে এরকম কুস্তির সবচেয়ে বড় আসরটি হয় ১২ বৈশাখ, চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে। এটি জব্বারের বলি খেলা নামে পরিচিত।
স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে এই উৎসব নাগরিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। কালক্রমে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আর কেবল আনন্দণ্ডউল্লাসের উৎসব নয়, বরং বাঙালি সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী ধারক-বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।
ডক্টর সন্জীদা খাতুন আর ওয়াহিদুল হকের পরিচালনায় ১৯৬৭ আর বাংলা ১৩৭৪ সালে পরাধীন বাঙালি চেতনার ধ্বজা উড়াতে রমনার বটমূলে গ্রামীণ লোক সংস্কৃতিকে একেবারে শহর বাংলায় শ্রুতিধর মানুষের প্রাণের কাছে নিয়ে এসেছে গানের মাধ্যমে। যা-ই হোক, সূর্যোদয়ের প্রথম প্রহরে রমনার বটমূলে ছায়ানটের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সন্জীদা খাতুনের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাংলা সনকে বরণ করে নেওয়া হয়। ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু হওয়া ছায়ানটের এই বর্ষবরণ উৎসব ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে ১৯৭২-এ ছায়ানটের বর্ষবরণ নিয়ে সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বেশ উৎসাহ দেখা যায়। যা এখন পর্যন্ত চলছে। এখন দেশের বেশির ভাগ জেলা শহরে জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে মঙ্গল শোভাযাত্রা, গান তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।।
২০১৬ সালে ইউনেস্কো ঢাকার চারুকলা অনুষদ থেকে আয়োজিত যে মঙ্গল-শোভাযাত্রা বের হয়, সেটিকে ‘মানবতার অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য’ হিসেবে ঘোষণা করে।
পহেলা বৈশাখে বাঙালি মেয়েদের মধ্যে লাল পাড়ের সাদা শাড়ি পরার প্রচলন আছে। এখন অবশ্য সবাই লাল-সাদা পোশাক পরে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে।
১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু ১ বৈশাখকে জাতীয় উৎসব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সরকারি ছুটির ঘোষণা দিয়েছিলেন। । আর জাতির পিতার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে প্রথম নববর্ষ ভাতা প্রদান শুরু করেন।
যে কোনো নববর্ষ মানেই নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন। জীবনকে রঙিন করে তোলার আকাঙ্ক্ষা। সবার জন্য একটি শান্তিময় দেশ হিসেবে আমাদের দেশকে পরিচিত করে তোলার একটা প্রচ্ছন্ন বার্তাও থাকে নববর্ষে।
শেষ করি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে-
আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও ॥
যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার-কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
শুভ নববর্ষ, শুভ বাংলাদেশ।